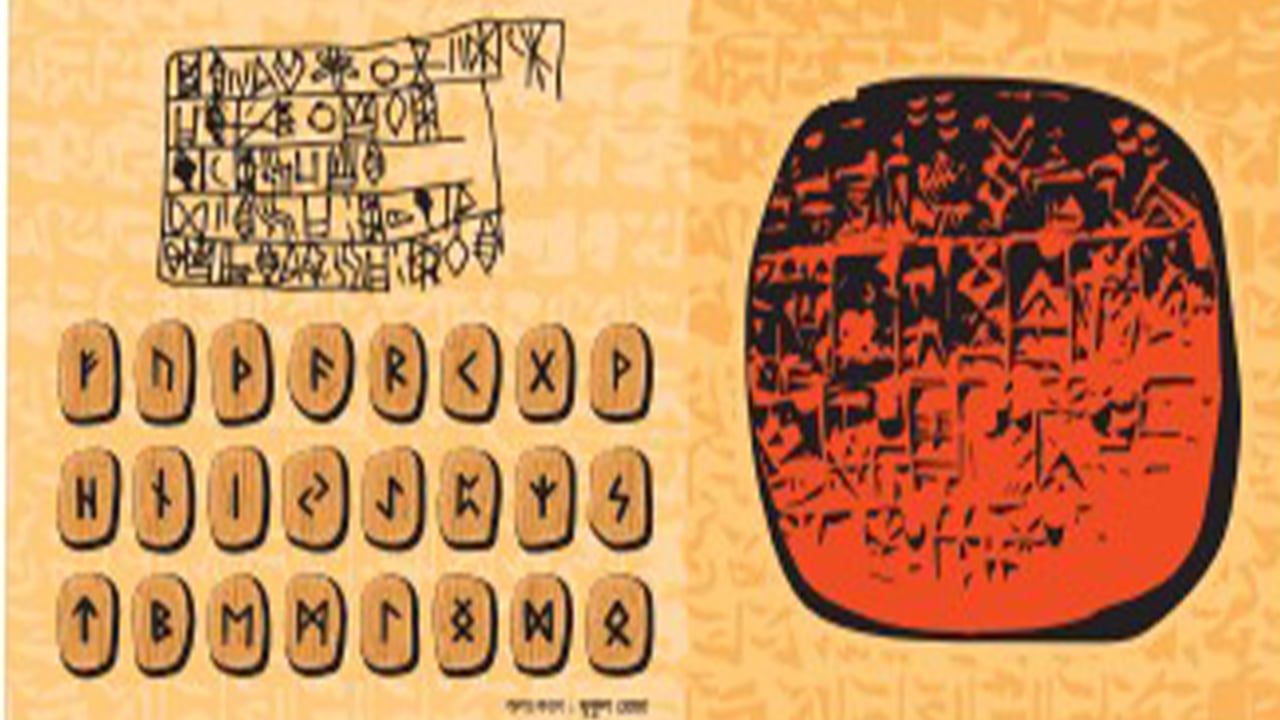তিন. ‘জনমানুষের বাংলা’য় লেখালেখি
১৯৪৭ সালের পরে বাংলাদেশের মানুষের রোখ ঘুইরা যায় ঢাকার দিকে। নগরমুখী স্থানান্তর ও যাওয়া-আসা খুব বাড়ে। শহরের সুবিধা ও ভাষিক-সাংস্কৃতিক স্বভাব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মোটামুটি শিক্ষিত অংশে প্রভাব ফেলতে থাকে। আবার শহরের কথ্যরীতিরে প্রভাবিত করে আঞ্চলিক ভাষাগুলাও। এইভাবে জনমানুষের ভাষা, অর্থাৎ হরপ্রসাদশাস্ত্রীর কথিত বিষয়ী লোকের ভাষাই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রধানে মৌখিক রীতি হিসাবে বাড়তে থাকে। এই পর্যন্ত আইসা আমরা পাই ভাষার তিন ধরনের রীতিভেদ—
এক. শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্রভিত্তিক সকল সাধারণ মানুষ এবং ধর্ম-বর্ণ-স্থান নির্বিশেষে সকল সচেতন সামাজিক সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, অর্থাৎ বাংলাদেশের ‘জনমানুষের বাংলা’ ।
দুই. (কলিকাতা-নদীয়ার কথ্য উপভাষার অনুকরণে প্রচলিত) লেখ্য ‘প্রমিত রীতি’, যেখানে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার মুষ্টিমেয় শিক্ষক-লেখক-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মী এই লেখ্য ‘প্রমিত রীতি’র সামান্য পরিবর্তিত রূপ আনুষ্ঠানিক পোশাকি ভাষা হিসাবে মুখে বলে থাকেন ।
তিন. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রীতি।
এইখানে একট বিষয় পড়ুয়াদের নজরে আনতে চাই। অনেকে সর্বাঞ্চলীয় জনসমাজের মুখের ভাষাকে অর্থাৎ বাংলাদেশের ‘জনমানুষের বাংলা’ ভাষাকে আঞ্চলিক কথ্যরীতি বলে ধরে নেন। কিন্তু এটি গুরুতর ভুল। আঞ্চলিক বাংলা সেই অঞ্চলের রীতিবৈচিত্র্য। যেমন নোয়াখালী, রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহের বিশিষ্ট আঞ্চলিক রীতি। অন্যদিকে ‘জনমানুষের বাংলা’ হইল বাংলাদেশের সব অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাধারণ মৌখিক রীতি। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যখন একসাথে হয় তখন তারা আর আঞ্চলিক রীতিতে কথা বলে না, কথা বলে জনসমাজের সাধারণ মৌখিক রীততে।
ভাষা প্রায় সবসময়ই বড় কথক গোষ্ঠীর একমতের মধ্য দিয়া বিকশিত হয়। কেউ একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করতে চাইলে অন্যরা যদি সেইটা নিজেদের কথাবার্তায় কাজে না লাগায়, তাইলে সেই শব্দটা এই ভাষায় আর জায়গা পায় না। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মিশ্রণ খুব বাড়ছে। আঞ্চলিক ভাষারীতি এবং জনমানুষের বাংলার মধ্যে ব্যাপক দেয়া-নেয়া হইছে, এখনো হইতেছে। যেমন আঞ্চলিক রীতির ‘বেইল নাই’ কথাটার প্রকাশক্ষমতা অনেক। এইটা সহজেই জনসমাজের বাংলায় জায়গা পাওয়া গেছে। আঞ্চলিক ভাষারীতি এবং জনসমাজের বাংলা এই দুইয়ের মধ্যে এই যে দেয়া-নেয়া, তা এই ভাষার প্রকাশক্ষমতা অনেক বাড়ায়া দিছে। এই দেয়া-নেয়া কিন্তু সবসময় জারি থাকে। এইটা এই ভাষার শক্তির বড় জায়গা। এইভাবে, গত সত্তর বছরে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে ‘জনমানুষের বাংলা’ খুবই শক্তিশালী একটা ভাষা হয়া উঠছে। এই ভাষার ব্যবহারিক পরিচয় কিছুটা তুইলা ধরা দরকার।
বাংলাদেশে লেখালেখির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পরিসর বিশেষত ফেসবুক ও ওয়েবসাইট একটা বিপ্লব নিয়া আসছে। নয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দাপটে অধিকাংশ মিডিয়া যখন সুবিধাবাদী গ্রুপগুলার পকেটে তখন ফেসবুক-ওয়েবসাইট পরিণত হইছে ভিন্নমতের লোকদের কথা বলার বড় জায়গায়। নয়া সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোখার জন্য আমি বিকল্প মাধ্যম তৈয়ার ও ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করছি বিভিন্ন প্রবন্ধে।১২ এইগুলা হইল সেই ধরনের বিকল্প জায়গা। ফেসবুক এবং ওয়েবসাইটে ‘জনমানুষের বাংলা’ শক্তিশালী লেখনরীতি হিসাবে দাঁড়ায়া গেছে। এইসব লেখায় পুরাই অস্বীকার করা হইছে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী লেখনরীতিরে। উদাহরণ হিসাবে আমি নিজের বই থাইকা এইখানে একটা নমুনা যোগ করতে চাই—‘বেভারলির কথামতো নিচু জাতের হিন্দুরা হিন্দু সমাজে নির্যাতিত হওয়ার কারণে মুসলমান হয়া থাকলে সারা ভারতেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি হওয়ার কথা। বিশেষ কইরা পাঞ্জাব, দিল্লি, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ—এইসব এলাকায় অবশ্যই মুসলমান বেশি থাকত। পাঞ্জাবে এই একুশ শতকেও ৩২ শতাংশ শিডিউলড কাস্ট, সাথে যোগ অইব উপজাতিগুলা, সব মিলায়া ৪০ শতাংশ ছাড়ায়া যাওয়ার কথা। অথচ পাঞ্জাবে মুসলমানের হার ১.৯৩ শতাংশ। মধ্য প্রদেশে শিডিউলড কাস্ট শিডিউলড ট্রাইব মিলায়া ৩৬ শতাংশ, অথচ মুসলমান সাত শতাংশেরও কম। দিল্লিতে মুসলমান ১৩ শতাংশ প্রায়। বিহারে শিডিউলড কাস্ট ও ট্রাইব মিলায়া ৬৩ শতাংশ, অথচ মুসলমান মাত্র ১৭ শতাংশ। দেখা যাইতেছে, যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষ বেশি আছিল, সেইখানে মুসলমান বেশি হইছে, এই কথাটা ঠিক নয়। উপ্রের পরিসংখ্যান থাইকা বুঝা যায় বেভারলির এই ব্যাখ্যা কতটা যুক্তিহীন, কী রকম দুনিয়াছাড়া। আসলে বাংলাদেশ একটা হিন্দুদেশ বা হিন্দুপ্রধান দেশ আছিল—এইটাই একটা ভুল বা বানোয়াট অনুমান, যেটা উনিশ শতকে সৃষ্টি হইছে। এই ভুল অনুমানের উপর খাড়ায়া যত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সিদ্ধান্ত হবে, তার সবই ভুল হইতে বাধ্য।’১৩
এইটা জনমানুষের বাংলা ভাষায় লেখা। আলোচনার বিষয় তথাকথিত ‘গুরুগম্ভীর, উন্নত ভাব’-এর শামিল। তাইলে এই ভাষায় গুরুগম্ভীর ও উন্নত ভাব প্রকাশ করা যায় না বইলা যে-অভিযোগ তোলা হয়, সেইটা সত্যি না।
নদীয়া-কলিকাতার আঞ্চলিক ভাষা প্রমথ চৌধুরীর চেষ্টায় চলিত ভাষা হিসাবে লেখার ভাষা হয়া ওঠে, যাতে যুক্ত হয় অজস্র সংস্কৃত শব্দ। সেই ভাষাই আমাদের বর্তমানকালের প্রমিত বাংলা। এই ভাষা বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা ও মনের আবেগ থাইকা অনেক দূরের জিনিস। বাংলাদেশের মানুষের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র সেই ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে, লেখতে পারে আরো কম সংখ্যক মানুষ। তার বিপরীতে জনমানুষের বাংলা সকলেই বুঝতে পারে। তা লেখার জন্য আলাদা চর্চা ও অভিধানের দরকার পড়ে না, কেবল মুখে বা মনে মনে উচ্চারিত শব্দগুলা লেখলেই হইল।
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাধারণ মুখের বুলি বা জনমানুষের ভাষার কিছু বিশেষত্ব সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক—
ক. বাংলাদেশের ‘জনমানুষের বাংলা ভাষার’ আলাপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল, এই রীতিই বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের মুখের ভাষা। শুধু ঢাকা বা চট্টগ্রাম বা রংপুর শহরের মতো বড় শহরের মানুষ এই ভাষায় কথা কয়, এমন না। বরং প্রত্যেকটা ছোট-বড় শহর অঞ্চল, উপজেলা প্রশাসনিক কেন্দ্রসহ অন্য ছোট মেলগুলাতেও সামাজিকভাবে সচেতন মানুষ এই ভাষায় কথা কয়।
খ. অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন, যারা আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলেন। কিন্তু ‘জনমানুষের বাংলা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয় না, কোনো ভাবগত দূরত্বও তৈয়ার হয় না।
গ. মুখের ভাষা হওয়ায় লেখার ক্ষেত্রেও এর প্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রকাশক্ষমতা বেশি হওয়ার কারণ হইল লেখক/কথক মুখে মুখে যে শব্দ/শব্দবন্ধে সারা দিন তার মনের কথা কইতেছেন বা ভাবতেছেন, লেখার সময় তিনি সেগুলাই লেখতেছেন। তার বোধ, অনুভূতি, বুদ্ধি—এইসব শব্দরে চিনে নিজের হাতের তালুর মতো। কোন ভাবটার জন্য কোন শব্দ/শব্দবন্ধ দরকার, সেইটা তার চিন্তা করতে হয় না, দোনামোনা করতে হয় না, অভিধানের আশ্রয় নিতে হয় না। মন থাইকা আপনাআপনি আইসা পড়ে। এইটা এই ভাষার বড় সুবিধা।
ঘ. নিজেরে এবং চাইরদিকের সবকিছুরে প্রকাশের দরকার থাইকা ভাষার জন্ম হইছে। তাই কোনো একটা সমাজে যে-ভাষা সৃষ্টি হইছে, সেই ভাষাই সেই সমাজের মনের কথা প্রকাশের সবচেয়ে ভালো বাহন। এর বাইরের যেকোনো ভাষা ব্যবহার করলে সেইখানে খুঁত থাকতে বাধ্য। বাংলাদেশের ‘জনসমাজের বাংলা’ হাজার বছর ধইরা এই দেশের মানুষের লেখার ও মুখের ভাষা হিসাবে চইলা আসছে। এইখানে বানোয়াট কিছু নাই। এই মাটি, পানি, বাতাস, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভূগোল, সমাজ, ভাব, ধর্ম, আচার—এইসব নিয়াই এই ভাষা দিনে দিনে ধনী হইছে। চাইরদিক নিয়া বাংলাদেশের মানুষের যে জীবন, সেই জীবনের কথা বলতে গিয়া এই ভাষার সৃষ্টি ও বাইড়া ওঠা। কাজেই এই জীবনের কথা বুঝানোর জন্য আর কোনো ভাষা এর চেয়ে বেশি ভালো হইতে পারে না।
ঙ. জনমানুষের বাংলা ভাষার কথনভঙ্গি অনেক গতিশীল, হালকা চালের, তীরের মতো ছোটে। এর কারণ হইল এই ভাষার প্রত্যেকটা শব্দের ব্যাপারে ব্যবহারকারী চেতন-অবচেতনে ওয়াকিবহাল। শব্দটা কানে যাওয়া মাত্রই তার মাথায় অর্থটা বাইজা উঠে। (প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত অনেক শব্দই ধার কইরা আনা। সেইজন্য ধারের শব্দের অর্থ সাথে সাথে মনে বাজে না, বুদ্ধি দিয়া বুঝতে হয়। কথনঢঙ অনেক ক্ষেত্রেই সরলসোজা না, নানা বাঁক ঘুইরা মূল অর্থের দিকে যায়।)
ছ. ভাষা লেখায় আসার পরে তার প্রতিটা শব্দই একটা স্থায়ী রূপ পায়া যায়। এই কারণে লিখিত রূপ ভাষার দরকারি বিকাশে বাধা হয়া দাঁড়ায়। লেখার ভাষা যদি চলমান মুখের বুলি থাইকা আসে এবং তার যদি মুখের ভাষার সাথে তাল মিলায়া চলার দায় থাকে, তাইলে মুখের ভাষা বদলাইলে তার লেখার রূপও বদলাবে।
আমাদের বর্তমান লেখনরীতি, অর্থাৎ প্রমিত রীতি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা না। ফলে কালে কালে মুখের ভাষা বিকশিত হইলেও সেইমত প্রমিত বাংলা বদলায় নাই। কারণ দুই ভাষার সরাসরি যোগাযোগ নাই। এইজন্য প্রমিত বাংলা ভাব প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রেই আড়ষ্ট। অন্যদিকে, জনমানুষের বাংলা লেখনরীতি হিসাবে চালু হইলে মুখের ভাষার প্রত্যেকটা রদবদলের সাথে সাথে লেখার ভাষায় আইসা পড়বে। দুইয়ের মিল যেমন থাকবে, তেমনি সময়ের দরকারে লেখার প্রকাশক্ষমতাও বাড়বে।
গত প্রায় এক দশক থাইকা ফেইসবুক ইত্যাদি ইলেকট্রনিক সামাজিক পরিসরে, নাটকে এবং তরুণ কবিদের কবিতা লেখা হইতেছে জনমানুষের বাংলা ভাষায়। এতে এই ভাষার লিখিত রূপের প্রকাশ ক্ষমতা সফলভাবে জাহির হইছে। এইখানে জনমানুষের বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকটা কবিতার একটু একটু কইরা দিলাম—
‘এমন গাভীন রাত্তির ভাঙ্গা পাটাতনও নাই, কীভাবে
ঢেউয়ের উপর ঘর সাজাই। মনকড়ালি পাখি ডাইকা যায়
প্রাচীন গুহায়। শুইনাছি, পাহাড়পুরী এক মেয়ে প্রত্নজন্ম
থেইকা আছে এখানে, গাভীন রাত্তিরে তেজস্বী এক
ঘোড়ার পিঠে জাইগা উঠে সে, আর তখন মেরুন-রঙের
একটা পাখি কীরকম শব্দ করে—নাচে। সেই পাখিটা
তোমার মতো বাংলা চক্ষু তার, বুকের ভিতর গভীর নদী
ভাঙে দূর-পাহাড়।’১৪
‘এইসব ভাবতে ভাবতে আইসা সামনে দাঁড়ায়
এক নিরাকের কাল
বুকের ভিতরে নিরাক
ফরফর শব্দ তুইলা উইড়া চলে এক
নিরাকপঙ্খী...
এইখানে মনে কয় একখান দাঁড়ি দেওন যায়।’১৫
‘কথা আমার দূরে যাইতে যাইতে
ভাটির আওয়াজ তুলবে
আমি গাইলে গান কলকল করবে পানি
নইলে অপেক্ষা করি, আইসা যাক ফসলের মাস
মুরালি ধানের পিঠার গন্ধে জাইনা যাবে
আমাদের বাড়িত একই রীত।’১৬
‘বিপ্লব পোষা কইতর না
খুঁদকুঁড়া দিয়া যত লোভ লালসা ছড়াই
বিপ্লব কখনো ধরা দেয় না কারো হাতের মুঠায়।
কয়েকটা কাতর শব্দের মধ্যে জাইগা রইছে
রক্তাক্ত জুলাই!
আমি তারে
দুইচোখ ভইরা কানতে দেখি।’১৭
‘আমি ঝুপড়ির চালে বইসা একলা ঝিমাই। গায়ে রোইদ লাগাই। কান পাইত্যা শহরের দুঃখী বাতাসের গুনগুন গান শুনি। বেচারা বাতাস শহরের দালানে ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গা মন নিয়া আবার বনাঞ্চলে ফিরা যায়। আমারো মনটা ফিইরা যাইতে চায়, ইচ্ছা করে ছোটবেলার মতো মায়ের বুকের দুধে কামড় দিয়া ঝুইল্যা থাকি, এক গাছ থেইক্যা আরেক গাছের ডালে লাফায়া বেড়াই। আমার দলের অন্যদের সাথে ঘুরিফিরি ছোটাছুটি করি আর আপনমনে দাঁত বাইর কইরা কিচিরমিচির করি। নাইলে মণ্ডলের মতো উদাস কণ্ঠে কই—বিচিত্র এই ঢাকা নগর, কে খেলাড়ি কে বাজিকর?’১৮
তিনটা কবিতা আর একটা গল্প থাইকা যে-চাইরটা নমুনা দেয়া হইছে, সেইগুলা জনমানুষের বাংলায় লেখা। নমুনাগুলায় দেখা যাইতেছে কাব্যিক সংবেদনা প্রকাশে এই ভাষা খুব সক্ষম, সহজেই পাঠকের মনের গহিনে হানা দেয়ার মতো। শেষ নমুনাটা মানুষের মনের আবেগের চমৎকার এক বয়ান। কাজেই, অন্তত এই কথা বলা যায় না যে, এই ভাষা আমাদের মনের গভীর ভাব প্রকাশ করতে পারে না।
মুখের ভাষারে নকল করার জন্যই লেখার সৃষ্টি। আইজ নতুন কইরা এই বিতর্ক তোলার দরকার পড়ে না যে, মুখের ভাষায় সাহিত্য লেখা সম্ভব কি না। কুড়ি শতকের গোড়ায় প্রমথ চৌধুরী যখন নদীয়া অঞ্চলের কথ্যরীতিতে লেখা শুরু করলেন, তখনো অনেক বিরোধিতা হইছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট বটগাছের ছায়া পায়া প্রমথ চৌধুরী নদীয়ার কথ্যভাষারে শেষ পর্যন্ত লেখার রীতি হিসাবে চালু করতে পারছেন। এখন প্রমিত নামধারী নদীয়ার সেই কথ্যভাষার বদলে বাংলাদেশের জনসমাজের সাধারণ মুখের ভাষা, অর্থাৎ ‘জনমানুষের বাংলা’ ভাষায় লেখার কথা উঠলে তাতে বাধা দেয়া হবে কোন যুক্তিতে? সংস্কৃতায়িত বাংলা চাপায়া দেয়ার আগে হাজার বছর ধইরা এই ভাষাতেই মানুষ কথা বলছে, আবার লেখালেখি করছে। এখন এই ভাষায় লেখার কথা তুললে যদি বিরোধিতা করা হয়, তাইলে কি দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ সন্দেহের মুখে পড়ে না? শেষে জনমানুষের বাংলা ভাষায় লেখার পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর একটা কথা উল্লেখ করি—‘মুখের ভাষা যে জীবন্ত ভাষা, এ বিষয়ে দুমত নেই। একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব করে তুলতে পারি।’১৯
সময়ের সাথে ভাষাও বদলায়। স্বাভাবিক এই রদবদলরেই ভাষার বিকাশ কয়। তবে তার গতি ধীর। একটা সমাজে রদবদল চোখে পড়ার মতো না হইলে ভাষার বদলও চোখে পড়ে না। ‘মান কথ্যবাংলা’রে আমাদের লেখার ভাষা করার কাজেও সময় লাগবে। তার শুরুটা হয়াও গেছে কবিতায়, নাটকে, গানে ও ইলেকট্রনিক সামাজিক পরিসরে। এখন দরকার দ্রুত প্রসার। প্রায় দুইশ বছর ধইরা আমাদের লেখার ভাষা আলাদা হয়া থাকছে বাংলাদেশের মানুষের ভাষা থাইকা। ফলে আমাদের সাহিত্য গেছে একদিকে, জনমানুষের মন-আবেগ আরেকদিকে। এখন সময় হইছে এই দূরত্ব ঘোচানোর। মান কথ্যবাংলায় সাহিত্যচর্চা করলে আমাদের প্রকাশক্ষমতা বাড়বে, প্রকাশিত চিন্তা-ভাব-আবেগের বানোয়াট ভাবটা থাকবে না, পড়ুয়ারা সহজেই নিতে পারবে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় ‘সাহিত্য সজীব’ হবে। যেই ভাষায় জমা হয়া আছে আমাদের শত শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাব, সংস্কৃতির বেবাক চিহ্ন, সেই ভাষায় ফিরার অর্থ তো নিজের শিকড়ে ফিরাই।
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন