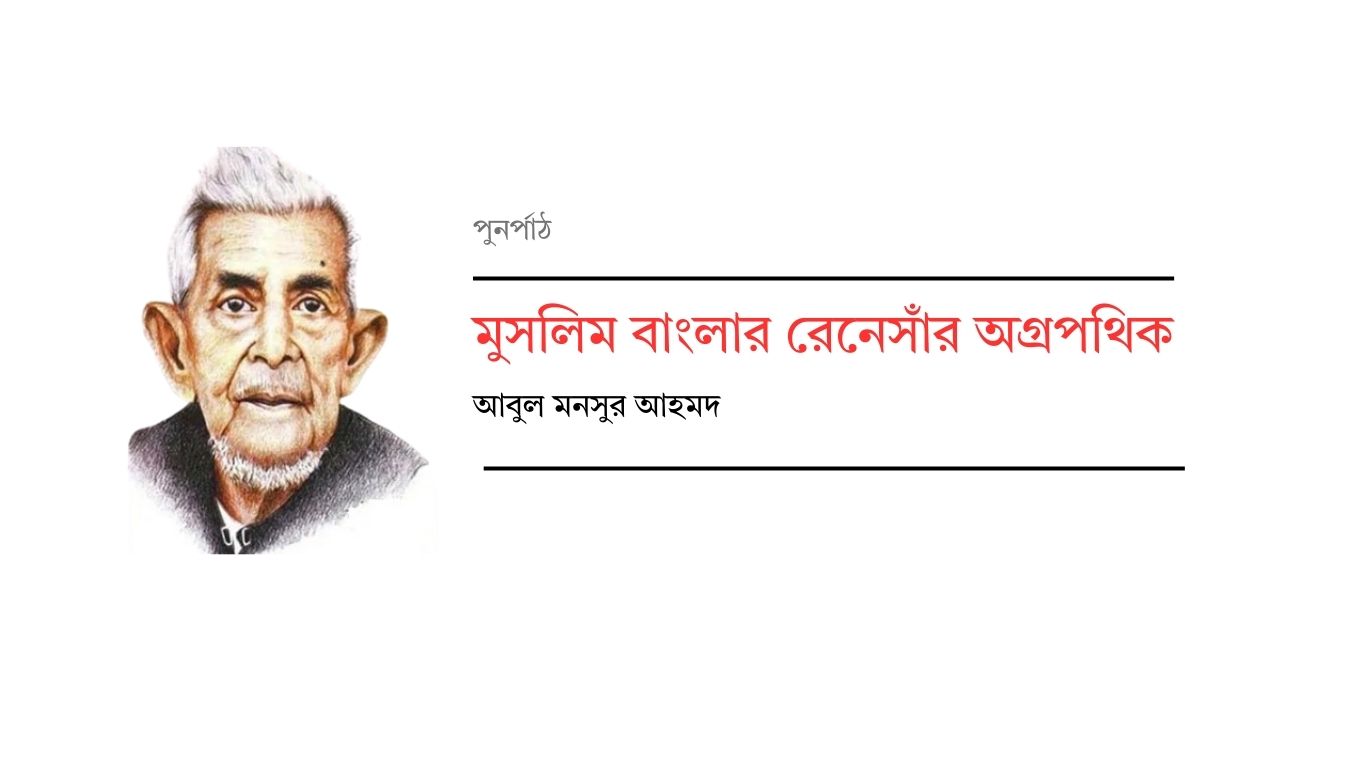১৯৬৮ সালের ৭ই জুন তারিখে সারাদেশ মওলানা সাহেবের নিরানব্বইয়া জন্মবার্ষিকী ধুমধামের সহিত পালন করে। ঐদিন গোটা দেশবাসী হাত তুলিয়া মোনাজাত করে, মওলানা সাহেবকে আল্লাহ শতায়ু করুন। আমিও দেশবাসীর সে মোনাজাতের শরীক হইয়াছিলাম। আমার মোনাজাতে বলিয়াছিলাম: মওলানা সাহের পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। মুসলিম-বাংলা তথা সারা মুসলিম ভারতের সার্বিক জাতীয় পুনর্জাগরণের মূলে যে কয়জন মনীষীর অবদান ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকিবে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রধান। মওলানা সাহেবের সহযোগী ও সহকর্মী সেই সব মনীষীর কেউ আজ আর বাঁচিয়া নাই। আল্লাহ তালার অশেষ মেহেরবানীতেই একমাত্র মওলানা সাহেবই গত ষাট বছরের পাঁচ পাঁচটি যুগের সংগ্রাম, সাহস, ত্যাগ, অধ্যবসায় ও সাফল্যের সাক্ষী স্বরূপ আজও দেশবাসীর সামনে ও অন্তরে কুতুবমিনারের ম্যাজেস্টি লইয়াই উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন। সংগ্রামের দিনে শত বিপদের মাঝখানেও যেমন তিনি দুশমনের কাছে মাথা হেঁট করেন নাই, সাফল্যের বিজয়ানন্দের উল্লাসেও তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কোন দোস্তের কাছেও মাথা নত করেন নাই। সর্ব অবস্থায় তিনি ছিলেন চির উন্নত শির।
কিন্তু হায়াত মওতের মালিক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বিরাট ধুমধাম ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে মওলানা সাহেবের ঐ জন্মবার্ষিকী পালনের পর দুই মাস যাইতে না যাইতেই তিনি দেশবাসীকে কাঁদাইয়া ১৮ই আগষ্ট তারিখে এন্তেকাল করিলেন। শতাব্দী-কালের একটা মহীরুহ, বিস্তীর্ণ ছায়াদার একটা বিশাল বটগাছ ভূমিসাৎ হইল। দেশ হারাইল একটা আলোকস্তম্ভ। দেশবাসী হারাইল বাড়ীর মুরুব্বি। সাংবাদিক-সাহিত্যিকরা হারাইলেন উপদেষ্টা, রাজনীতিবিদরা হারাইলেন একজন পথের দিশারী, আলেম সম্প্রদায় হারাইলেন একজন অনুপ্রেরণাদাতা। সারা পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) ধসিয়া পড়িল একটি সুউচ্চ মিনার। শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল সারাদেশ। দুইমাস আগে যাঁরা আনন্দ কলরবে সরব হইয়াছিলেন, দুইমাস পরে তাঁহারাই আবার জানাযার শোক মিছিলে নীরব হইলেন।
মওলানা সাহেবের সংগ্রামী জীবনের সাধনা যেমন নিষ্ঠাবান তাপসের অন্তহীন বিঘ্ন-বিপত্তি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার স্বাক্ষর, তাঁর পরিণাম সাফল্যও তেমনি গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমামণ্ডিত। উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথম দশকের কৃষ্ণ সাধনা হইতে বিশ শতকের পঞ্চম দশকের পাকিস্তান সংগ্রামের সাফল্য এই সুদীর্ঘ মুদ্দতে ‘আল-এছলাম’ ‘মোহাম্মদী’ ও ‘আজাদ’-এর মাধ্যমে মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক পুনর্জাগরণের গৌরবময় ইতিহাস একটিমাত্র ব্যক্তি জীবনের জন্য অনন্যসাধারণ। তবু মওলানার জীবনের এটাই সামগ্রিক রূপ নয়, তাঁর আসল রূপও নয়। বীর মোজাহিদদের সাফল্যের রঙ্গীন ছবিটাই আমাদের নজরে পড়ে আগে। সে সাফল্যের অন্তরালে কত যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, কত যে ব্যর্থতা-নৈরাশ্য, কত যে অশ্রু বারি, কত যে উত্থান-পতন, কত যে আশা-নৈরাশ্য, কত যে আলো-অন্ধকার লুক্কায়িত থাকে, সাধারণ দর্শকের নজরে তা পড়ে না। সাফল্যের ঝলমলা আলোকে সে সবই ঢাকা পড়িয়া যায়। সাধারণ মানুষের জন্য ঐ সাফল্যটুকুই যথেষ্ট। ওর বেশী জানার তাদের দরকার নাই। সাফল্যের ফল ভোগেরই তারা অংশীদার। সাফল্যের অন্তরালে যে দুঃখ-বেদনার কাহিনী প্রচ্ছন্ন থাকে, সে অপ্রিয় সত্য উদঘাটনে জনগণের প্রয়োজন নাই।
কিন্তু যাঁরা সে সাফল্যকে জাতির জীবনে প্রয়োগ করিবেন, নিত্য নব নব ফুলফলে সে সাফল্যের বৃক্ষকে মঞ্জুরিত করিবেন, যুগে যুগে সে সাফল্যকে অধিকতর সাফল্যের সোপান ও প্রগতির দিক-দর্শনরূপে ব্যবহার করিবেন, তাঁরা ঐ সাফল্যের বাহিরের রূপটুকু দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। মওলানা সাহেবকে তাঁরা শুধু একটা ব্যক্তিমাত্র হিসাবে, তা সে ব্যক্তিত্ব যত মহিমান্বিতই হউক, বিচার করিতে পারেন না।
তা করিলে মওলানা সাহেবকে আংশিক বিচার করা হইবে মাত্র। পূর্ণ বিচার তার করা হইবে না। ফলে সে বিচারে ভুল থাকিয়া যাইবে।
কারণ মওলানা আকরম খাঁ একটি ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না, অন্যান্য অনেক নেতার মত তিনি শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটা যুগের প্রতিনিধি-যুগের প্রতীক। স্বয়ং একটা যুগ। বাহির হইতে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব, তাঁর সাফল্যের বিপুলতা, তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের বিস্তৃতি দেখিলে বলিতেই হইবে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। মওলানা সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্বরূপী সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারকের শ্রেষ্ঠ মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল অপূর্ব সামঞ্জস্যে। তিনি একাধারে ছিলেন সবই। সকল অমৃত ফলের ছিলেন তিনি কল্পতরু।
কিন্তু ওটা তার গোটা রূপ নয়। গোটা রূপ তার বিবৃত সেই যুগে, যে যুগের চরম সন্ধিক্ষণে তার জন্ম। সে যুগের তিনি প্রতীক। সে যুগ ছিল মুসলিম বাংলার, তথা মুসলিম ভারতের এমনকি গোটা মুসলিম বিশ্বের ক্রান্তিকাল। অন্ধকার হইতে আলোর যুগ। বন্দীজীবন হইতে আজাদীর যুগ। কুসংস্কার হইতে মুক্তবাদের যুগ। গভীর অমানিশার অন্ধকার হইতে সুবেহ সাদেকের এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রভাতের যুগ। সব ক্রান্তিকালের মতই আমাদের জীবনেও ওটা ছিল ডায়লেমার যুগ, বিভ্রান্তির যুগ। আলোছায়ার যুগ। অনিশ্চয়তার যুগ। ‘কি করিব, কোনটা করিব’র যুগ। করি কি না করি’র যুগ। কাজেই কঠিনতম কর্তব্যের যুগ ছিল ওটা। মওলানা সাহেব যে চিন্তাপথের পথিক ছিলেন, সে পথের সহযাত্রীদের কর্তব্য নির্ধারণ মোটেই সহজ ছিল না। যে পথ সহজ ছিল, সে পথে মওলানা সাহেব যান নাই। তার বদলে কঠিন পথ, অনিশ্চয়তার পথ, বিপদের পথই তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন।
মওলানা সাহেব ছিলেন আলেমের বেটা আলেম। আলেমের কর্তব্যও ছিল ঐ যুগে অসামান্য। বাদশাহির পতন যুগের অবশ্যম্ভাবী বিলাসিতার কদাচারের পংকিলতায় তখন মুসলিম ভারতের অভিজাত শ্রেণী আকণ্ঠ নিমজজিত, ইংরাজ সরকার পৃষ্ঠপোষিত খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার প্রপ্যাগান্ডায় ইংরাজী শিক্ষিত সরকারী চাকুরিয়া মুসলমানরা এবং তাদের দেখাদেখি মুসলিম জনসাধারণ বিপথগামী। এদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও মূল্যবোধ প্রচারে যদি মওলানা আকরম খাঁ অবতরণ করিতেন, তবে তিনি কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, কেউ বলিতে পারিত না। সে কাজেও তিনি যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিতেন, তাতেও আমাদের সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে তার সামনে আর যে পথ খোলা ছিল, অপরের জন্য যতই কঠিন হউক মওলানার জন্য ছিল তা সহজ স্বাভাবিক ওয়ারিসী। মোজাহিদ বংশের আদর্শবাদী তরুণ ছিলেন তিনি। বাপ-দাদার জেহাদী লহু তার রগ-শেরায় করিত টগবগ। ভাবপ্রবণতার সামনে একটু শিথিল হলেই তিনি সে পথে নামিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু তা তিনি যান নাই, যে পথে তিনি গেলেন সেটাও ছিল জেহাদের পথ। কিন্তু সে জেহাদ তলোয়ারের ছিল না-ছিল কলম ও যবানের। কাজেই সে পথ ছিল আরও ব্যাপক আরও গভীর, আরও জটিল, আরও দুরূহ। কাজেই ওটা ছিল ত্যাগের পথ, বিপদের পথ, অবিশ্রামের পথ। সে পথ মুসলিম জাতির শুধু ধর্ম-কৃষ্টির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল না। ওটা ছিল তাদের বাঁচার প্রশ্ন। গোলামি ও আযাদীর সন্ধিক্ষণ। সুবেহ কাযেব ও সুবেহ সাদেকের ছিল ওটা ক্রান্তিকাল। আলোছায়ার বিভ্রান্তকর পরিবেশ। পথ চলা ছিল বিপজ্জনক। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপে অগ্রগতি চিরতরে স্তম্ভিত হইতে পারিত। একটি ভুল দাড়ক্ষেপে একটি শিথিল হস্তে হাইল চালনায় গোটা জাতির নৌকাডুবি হইতে পারিত। একটিমাত্র ভ্রমাত্মক নীতির ফল যুগ যুগ ধরিয়া গোটা জাতিকে বহন করিতে হইত। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুটা ছিল মুসলিম জাতির জন্য এমনি একটি যুগ।
ঊনিশ শতকের পুরাটাই ছিল মুসলিম বাংলায় জাতীয় জীবনে সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগ। শুধু মুসলিম-বাংলা নয়, সারা মুসলিম ভারতেরও এটা অন্ধকার যুগ। ১৭৫৭সালে পলাশীর পরে ১৭৬৪ সালে উদয়নালা, সিরাজের পরে মীর কাশিম, মুসলিম-বাংলার বাস্ত্রীয় অধিকার পুনরুদ্ধারের আশা চিরতরে নির্মূল। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বের ভিত পাকা হইল। এই ভাবে মুসলিম বাংলার দিকে নিশ্চিন্ত হইয়া মুসলিম-বাংলা বিজয়ের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া ইংরাজ ১৭৭৫ সালে বেগমদের অযোধ্যা, ১৭৮২ সালে হায়দার আলীর মহীশুরে, ১৭৯২ সালে টিপু সুলতানের মহীশুরে ও ১৭৯৪ সালে সিন্ধু-হায়দারাবাদে প্রভুত্ব কায়েম করিয়া তার পর-পরই পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ ও কাশ্মীরের মহারাজার সহিত চুক্তি করিয়া ইরান ও আফগানিস্তানের দিকে হস্ত প্রসারণের খাঁটি স্থাপন করিল।
ইরান ও আফগানিস্তানের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে ইংরাজের মতলব ছিল দুইটি। এক. অসন্তুষ্ট ভারতীয় মুসলমান তাদের প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র ইরান ও আফগানিস্তান হইতে কোনও সাহায্য লাভের চেষ্টা না করিতে পারে, তার ব্যবস্থা হিসাবে কাবুলেও ইংরাজের খাঁটি হওয়া দরকার। বিশেষত এই সময় মুসলিম বিশ্বের পুরুষ সিংহ সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য অনলবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইহার সহিত ভারতীয় মুসলমানদের কোনও যোগাযোগ না ঘটিতে পারে, সেদিকেও ইংরাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ইংরাজদের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল এই যে, আফগানিস্তান ও ইরানের সহযোগিতায় রুশিয় ভারত আক্রমণ করিতে পারে। সে সম্ভাবনা দূর করা ভারতের নিরাপত্তার জন্য ইংরাজের কর্তব্য। অথচ সত্য কথা এই যে, এই রুশ ভীতি ছিল ইংরাজের তৈয়ারী একটা ভাওতা মাত্র। বস্তুতঃপক্ষে ইংরাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে রুশিয়া ভারত আক্রমণ করিবে, এই আশংকা ইংরাজের কোনও দিন ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে মুসলিম দুনিয়া বিশেষত তুরষ্ক, ইরান ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও রুশিয়ার মধ্যে বরাব একটা গোপন চুক্তি ছিল। এই তিনটি মুসলিম দেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নিবার একটা ষড়যন্ত্রে তারা অংশীদার ছিল। ১৯০৭ সালে ইরান ও ১৯১৪ সালে তুরষ্ক বাটোয়ারা করা এই ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। ইংরাজ ও রুশিয়ার এই গোপন বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে দুই বিশ্বযুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত হয়। উভয় যুদ্ধেই ইংরাজ রুশিয়া উক্ত তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া ছিল। উভয় যুদ্ধেই ইংরাজ ও রুশিয়া মিত্রশক্তি। এতদসত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষ দিক হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইংরাজ ভারতে হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর মনে এই রুশ-ভীতি এবং কারল-ভীতি বরাবর জাগরুক রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইভাবে আঠার শতকের শেষদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কবজা করিবার পর ১৭৬৫ সালে প্রাপ্ত দেওয়ানীর ক্ষমতাবলে ১৭৯৩ সালে ইংবাজ বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। এই বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান ভূস্বামী-আয়মাদাররা নিঃস্ব হইয়া পড়ে। তাদের স্থলে হিন্দু তহসিলদাররা নয় জমিদার শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয়। এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আগের দিন পর্যন্ত মুসলমানরা বাংলার শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন নয়, বাংলার শিল্প-সাহিত্য আর্ট-কালচারেরও তারা ধারক ও বাহক ছিল। সাড়ে ছয় শ' বছর ধরিয়া মুসলমানরা বাংলার শাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিয়াছে বিদেশী আগন্তুক হিসাবে নয়, দেশের মাটিরই সন্তান হিসাবে। ছয় শ’ বছর ধরিয়া এরাই বাংলার অভিজাত ও ইন্টেলিজেনশিয়া। হঠাৎ একদিন ১৭৫৭ সালে পলাশীর ময়দানে মুসলমানদের বিশ্বজয়ী ক্ষুরধার শাণিত তলোয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ও জালজুয়াচুরির মুখে ভোঁতা হইয়া গেল। বিশ্বাসঘাতকতায় সেই যে রাজ্য গেল, তারপর এক শ বছরের মধ্যে দ্রুত ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে মালিকানা গেল, বাজেয়াফতির নামে লাখেরাজ আয়মাদারী গেল, রাজভাষ্য পরিবর্তনে চাকুরী গেল, পোশাক পরিবর্তনে শরাফতির নিশানাটুকুরও অবসান হইল। এক কালের বাদশা এক রাত্রে পথের ফকির হইল। এক কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক রাত্রে মূঢ়ের জাত হইয়া গেল। এক কালের খানদানী অভিজাত ভদ্রলোকেরা এক রাত্রে ‘ছোটলোক চাষা’ হইয়া গেল।
কিন্তু এতবড় বিপদও মুসলিম বাংলার একার বিপদ ছিল না। বিপদ সারা মুসলিম ভারতের। এমনকি সারা মুসলিম দুনিয়ার। কিন্তু তথাপি আমি এখানে মুসলিম বাংলার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি দুইটি কারণে।
এক: এই সময়কার ইংরাজের সর্বাত্মক জুলুম কার্যের ও বর্বর অত্যাচারের স্টীমরোলার চলিয়াছিল মুসলিম বাংলার উপরই সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লব গণ-আন্দোলনের ও সর্বাত্মক বিপ্লবের আকারে দেখা দিয়াছিল এই বাংলাতেই। হাজী শরিয়তুল্লার ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের মোজাহেদী বিপ্লব, ময়মনসিংহের ফকির আন্দোলন ইত্যাদি গণবিপ্লব ও খণ্ডযুদ্ধ দাবাগ্নির মত জুলিয়া উঠিয়াছিল এই বাংলাতেই। এইসব আন্দোলন দমনের নামে সিপাহী বিপ্লবের দণ্ড বিধানের নামে ফাঁসি, জেল-জুলুম রূপে যে তাণ্ডব দানবীয় নৃশংসতা চলে বিচার আদালতের দোহাই দিয়া, এক আম্বালা ও পাটনার বিচার ছাড়া আর সবগুলি হয় এই বাংলায় কলিকাতা, বর্ধমান, বারাসাত, রাজশাহী, দিনাজপুর ও অন্যান্যা অনেক স্থানে। এই সব বিচারের নামে হাজার হাজার কৃষককে ও শত শত আলেমকে ‘নিকটতম বৃক্ষে ঝুলাইয়া’ ফাঁসি দেওয়া হয় এই বাংলাতেই। এই দানবীয় জুলুম চলে ঊনিশ শতকের শেষার্ধের মধ্যভাগ পর্যন্ত।
দুই: আমরা আজ যে মহামনীষীটির জীবনী আলোচনা করিতেছি, তাঁর জন্ম হইয়াছিল ঠিক এই সময়ে উনিশ শতকের শেষার্ধের এই জেল-জুলুমের শয়তানী তাণ্ডবলীলার মাঝখানে এই বাংলাতেই।
যে সময় মওলানা আকরম খাঁ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন, সেদিনকার মুসলিম বাংলার বর্ণনা দিয়াছিল স্বয়ং ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব স্ট্যাটাস্টিক্স মিঃ ডব্লিউ হান্টার। তিনি তাঁর ‘ইণ্ডিয়ান মুসলমান’ নামক পুস্তকে (১৮৭২ খ্রিঃ) লিখিয়াছেন, ‘‘পলাশীর সময় হইতে আজ পর্যন্ত কিঞ্চিতাধিক একশ বছরে আমরা মুসলমানদের উপর সীমাহীন অবিচার করিয়াছি। যারা এককালে এই দেশের শাসক ছিল, তারা আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। পঞ্চাশ বছর আগেও যাদের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, আজ তাদের পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব হইয়াছে। এর জন্য দায়ী সম্পূর্ণ আমাদের অবিবেচনাপ্রসূত অবিচারমূলক শাসন। বাংলার অভিজাত মুসলিম ধ্বংস হইয়াছে। তাদের আয়ের পথ ছিল প্রধানত তিনটি, সামরিক বিভাগের উচ্চপদ, বিচার বিভাগের উচ্চপদ, রাজ সরকারের উচ্চপদ। এই তিনটি বিভাগের সর্বোচ্চ পদগুলিতে ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার। আজ সৈন্য বিভাগে মুসলমান নেওয়া আমরা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। দেওয়ানী বিভাগের বড় বড় পদগুলি আমরা ইংরাজরা দখল করিয়াছি। নিচের পদগুলি হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু তহশিলদার, যারা রায়তদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিত, তারাই আজ জমিদার হইয়াছে। মুসলিম জমিদাররা সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে ছিল মুসলমানদের একাধিপত্য। ফার্সী উঠাইয়া দেওয়ায় মুসলমানদের জন্য সে দরজাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানরা ইংরাজী শিখে না। যে ফার্সী ভাষায় তারা এতদিন দেশ শাসন করিয়াছে, এত জ্ঞানীগুণী এবং মনীষীর জন্ম দিয়াছে, আমাদের ইংরাজী ভাষা যতই ভাল হোক, মুসলমানরা অত সহজে সে ফার্সী ভাষা ছাড়িয়া ইংরাজী ভাষা ধরিবে না। মুসলমানদিগকে ইংরাজী পড়ায় উদ্বুদ্ধ করিতে সময় লাগিল। হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বে যেমন করিয়া ফার্সী শিখিয়াছে, আজ তেমনি করিয়াই ইংরাজী শিখিতেছে এবং নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করিতেছে।”
হান্টার সাহেবের এই বইখানা দরদ দিয়া লেখা, সহানুভূতিতে ভরা। এই সময়ে মুসলমানদের মনে হতাশা-নৈরাশ্য ও আত্মবিশ্বাসহীনতা চরম সীমায় উপস্থিত এক'শ বছরব্যাপী প্রতিরোধ ও সংগ্রামে ব্যর্থতায় মন তাদের ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চারদিকেই তারা নিরুৎসাহের অন্ধকার দেখিতেছে। ১৮৩১ সালে বারাসাতে ও বালাকোটে পরাজয়ে ও নেতৃবৃন্দের নিধনে আন্দোলনের মেরুদণ্ড তখনই, ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবু তার পরে আরও চল্লিশ বছর বিচ্ছিন্নভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম চলিতেছিল। ইংরাজ সরকারের ক্রমবর্ধমান শক্তির দুর্বার অগ্রগতির সামনে মোজাহিদদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময় সৈয়দ আহমদ, শহীদ বেলভীর চার খলিফার অন্যতম খলিফা জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলী সাহেব আরও কতিপয় আলেমের সহযোগিতায় এক ফতোয়া জারি করিয়া ভারতবর্ষকে পূর্ব ঘোষিত ‘দারুল হরব’ বাতিল করিয়া ‘দারুল ইসলাম’ ঘোষণা করিলেন এবং জেহাদ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম হওয়ার যুক্তিতে মুসলমানদিগকে ইংরাজের সহযোগিতা করিবার উপদেশ দিলেন। হান্টার সাহেবের বই-এ এই ফতোয়ার উল্লেখ করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার বন্ধ করিবার এবং তাদের উপর সুবিচার করিবার আন্তরিক অনুরোধ ও সুপারিশ করা হইয়াছে বৃটিশ সরকারের কাছে।
মুসলিম-ভারতের আলেমদের মধ্যে স্বয়ং সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীদের মধ্যে এই সময় মতভেদ দেখা দেয়। একদল মওলানা কেরামত আলীর পক্ষে যান। অপর দল শাহ ইমদাদুল্লাহ ও মওলানা মোঃ কাসেমের নেতৃত্বে জেহাদ চালাইয়া যান। সবদিকে পরাভূত হইয়া তারা মক্কা চলিয়া যান। কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেওবন্দে দারুল উলুম স্থাপন করিয়া ধর্ম-শিক্ষার অন্তরালে জেহাদী মনোভাব যিন্দা রাখিতে লাগিলেন। মওলানা শিবলী নোমানী লাখনৌতে নদওয়াতুল ওলামা স্থাপন করিয়া মুসলমানদিগকে ইসলামী শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট রাখিতে লাগিলেন।
পক্ষান্তরে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের প্রদর্শিত পথে যারা যারা গেলেন, তাদের মধ্যে আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ও বাংলার নবাব আবদুল লতিফের নাম করা যাইতে পারে। তারা ইংরাজ সরকারের সহযোগিতা করিতে এবং ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদিগকে উপদেশ দিলেন। এঁরা ঐ সময়ে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, সবই সময়োপযোগী ও দূরদর্শী মূল্যবান হিতোপদেশ। পরিবর্তিত অবস্থায় মুসলমানদের জন্য সত্যই উহাই ছিল একমাত্র মুক্তির পথ। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ও নবাব আবদুল লতিফ উভয়ে ছিলেন ইংরাজ সরকারের কর্মচারী। সিপাহী বিপ্লবে ও তার পরবর্তীকালে বাংলা ও ভারতের মুসলমানরা যখন ইংরাজের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রাম করিতেছে, ঠিক সেই সময় স্যার সৈয়দ ও নবাব আবদুল লতিফ বিদেশী সরকারের চাকুরীতে বহাল থাকিয়া স্বভাবতঃই তাদের মুসলিম নির্যাতনের সমস্ত কিছুই নীরবে সমর্থন করিতেছিলেন। তারাই সরকারী চাকুরী ব্যাপদেশে দেশভ্রমণ করিতে গিয়া ইংরাজের সহযোগিতার পরামর্শ দিতেন এবং সরকারী উদ্যোগে আহূত সভা-সমিতিতে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা বর্ণনা করিতেন। তখন তাদের উপদেশ গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হইয়াছিল সত্য কিন্তু তাদের আত্মমর্যাদাবোধ তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। ইংরাজের ভারত বিজয়ের প্রথম একশ বছর নয়া শাসকদের প্রভুত্ব মানিয়া না লওয়া এবং ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ না করা ভুল হইয়াছিল, এতে মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। একথা আজ অনেকেই বলিয়া থাকেন। ক্ষতি যে বিপুল হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লাভ-ক্ষতিটাই কি বড় কথা? নয়া শাসক যারা ছল-প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের রাজ্য কাড়িয়া নিয়া আমাদের গদীতে বসিল, চট করিয়া পরের মুহূর্তে তারই সামনে সালাম হুজুর বলিয়া কুর্নিশ করা গতকালের শাসক মুসলমানদের পক্ষে কি সম্ভব, স্বাভাবিক ও আত্মমর্যাসঙ্গত হইত? সাংসারিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াই আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হয়, এটাই নিয়ম। মুসলমানরা এটা করিয়া আত্ম-সম্মানী জাতির উপযুক্ত কাজ করিয়াছে। হিন্দুরা যে মনোভার লইয়া ফারসীর বদলে ইংরাজী ধরিয়াছিল মুসলমানদের পক্ষে সে মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না। উচিতও হইত না। হিন্দুরা ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজদের চাকুরী লইয়া বড়লোক হইয়া গেল, অতএব মুসলমানদেরও উচিত ছিল সে ভিড়ে ঢুকিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চাকুরী নেওয়া। তাতে তাদের আর্থিক লাভ হইত, এ বুদ্ধি যারা মুসলমানদের দেন, তারা পরবর্তীকালের বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন খান সাহেব, খান বাহাদুর লোক। এরাই আরও পরবর্তীকালে কায়েদে আজমের নির্দেশে প্রকাশ্য খেতাব বর্জন করিয়াও গোপনে খেতাবের দ্বারা পরিচিত হইতে গৌরব বোধ করিতেন। এরাই স্যার সৈয়দ ও নবাব আব্দুল লতিফের ঐতিহ্যের ভ্রান্ত উত্তরাধিকারী। কায়েদে আজমের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এদের রাজনীতি ছিল আঞ্জুমনী রাজনীতি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই শ্রেণীর রাজনীতিবিদে মুসলিম সমাজ ভরিয়া গিয়াছিল।
স্যার সৈয়দ ও নবাব লতিফের মতবাদ ও প্রচার-পদ্ধতি স্বীকার না করিয়াও মুসলিম সমাজে এক মতবাদ গড়িয়া ওঠে, যারা একদিকে স্যার নবাবদের ইংরাজ-ঘেঁষানীতি ও অপরদিকে নিশ্চিত পরিচয়ের সম্মুখীন জেহাদী নীতি, এই দুই চরম রাস্তার মাঝখানে এক মধ্যপন্থা বাছিয়া লইয়াছিলেন। বাংলায় এই মধ্যপন্থা অবলম্বী দলের মধ্যে ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি শুধু এই মতবাদের পাইওনিয়ার ছিলেন না, সকল দিক দিয়া তিনি ছিলেন এই দলের প্রাণস্বরূপ ও অগ্রনায়ক। পরবর্তীকালের ইতিহাস ও ঘটনাবলী প্রমাণ করিয়াছে যে, এই মধ্যপন্থীদের নীতিই পরিণামে ফলপ্রসূ হইয়াছে এবং আরও পরে মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক মুক্তি হাসিল করিয়াছে। এটা সুস্পষ্ট কারণেই ঘটিয়াছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ ও নবাব লতিফের প্রদর্শিত নীতি ছিল পজিটিভ ও গঠনমূলক। কিন্তু মুসলিম গণমনের উহা অনুকূল ছিল না। পক্ষান্তরে মুসলিম জনতার অন্তরের কাছাকাছি ছিল জেহাদী আলেমদের ঐ চরমপন্থা। কিন্তু উহা ছিল সম্পূর্ণ নেগেটিভ। তবে কোন গঠনমূলক পন্থা ছিল না। কাজেই প্রথমটা ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয়টা বিলম্বিত হইল।
ফলে জেহাদী নীতির অবসানে মুসলিম ভারতে থাকিয়া যায় শুধু দুইটি মতবাদ। একটি ইংরাজ শাসকের অন্ধ সহযোগিতার মতবাদ, অন্যটি ইংরাজ সরকারের বাজনীতিতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ধরা না দিয়া আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ এবং সে কাজে সরকারের সহযোগিতা নেওয়া-দেওয়া। প্রথম দলের চেয়ে দ্বিতীয় দল সঙ্গত কারণে মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হইল; তাদের নীতি ফলপ্রসূ হইল। সরকারী কর্মচারী ও খান বাহাদুরদের উপর এঁদের সুস্পষ্ট সুবিধা ছিল। এঁরা সরকারী ভাল কাজের প্রশংসা যেমন করিতেন, খারাপ কাজের প্রতিবাদও তেমন করিতেন। কিন্তু সরকারী কর্মচারী খান বাহাদুর ও নাইট-নবাবরা সরকারের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সব কাজেরই সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মুসলিম দুনিয়ার খলিফা তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার প্রথম মহাযুদ্ধে যখন ভারতীয় মুসলিম সৈন্যদের দিয়া যুদ্ধ করাইলেন, তখন প্রথম দল ইংরাজদের কাজ সমর্থন করেন, দ্বিতীয় দল প্রতিবাদ করেন। তারপর যখন ইংরাজ সরকারের নেতৃত্বে ইউরোপীয় খ্রিস্টান রাজার। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বেশীরভাগ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইলেন, তখনও প্রথম দল চুপ থাকিয়া তার সমর্থন করিল। দ্বিতীয় দল প্রতিবাদ করিল, আন্দোলন করিল, জেল খাটিল। এমনি করিযা দ্বিতীয় দল জনগণের হৃদয়ের কাছাকাছি থাকিয়া শিক্ষা প্রচারে ও সমাজ সংস্কারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া চলিল। পক্ষান্তরে প্রথম দল তাদের সুস্পষ্ট দূরদর্শী নীতি লইয়াও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না। কারণ ইহাদের প্রচারে নিঃস্বার্থপরতা ছিল না। তাদের কাজ ছিল সহজ আরামের ভোগের পথ। নিজেও সরকারী চাকুরী করিব, জনগণেরও ভাল করিব, ইহা ছিল প্রথম দলের নীতি। কলাও বেচিব রথও দেখিব এই আর কি। দ্বিতীয় দলের মাঝে রথ দেখাটাই ছিল, কলা বেচাটা ছিল না। তাই জনগণের অকুণ্ঠ আস্থা পাইয়াছিলেন এঁরা।
তাছাড়া এই দলের দৃষ্টি শুধু শিক্ষা ও চাকুরীতে হিন্দু সমাজের সহিত প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নীতি ছিল আরও দূরদর্শী, কর্মপন্থা ছিল আরও ব্যাপক। এঁদের মহান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতির সার্বিক পুনর্জাগরণ। একশো বছর ওলামা সম্প্রদায় মুসলিম জাতিকে ইংরাজী শিক্ষায় ও সরকারী চাকুরীতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। এর স্বাভাবিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া নব্য সুশিক্ষিত তরুণ মুসলিমকে শুধু ওলামা বিরোধীই করে নাই, পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধীও করিয়া তুলিয়াছিল। এই সঙ্গে খ্রিস্টান পাদ্রীরা সরকারের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের দোষত্রুটি ও খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া মুসলিম তরুণদের বিপথগামী করিতেছিলেন। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চেতনা, স্বকীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান লোপ পাইতেছিল। তার উপর একদিকে নতুন যুগের স্বাভাবিক ভোগ-বিলাস, ব্যভিচারে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও হিন্দু প্রভাবে মুসলিম জনতা পৌত্তলিকতাসহ হিন্দুদের বহু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুসারী হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে তমুদ্দুন- অধঃপতন হইতে রক্ষা করাও নেতাদের দায়িত্ব ছিল।
বাংলার এই দায়িত্ব পালনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন যে মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী আত্মত্যাগী আলেম সম্প্রদায়, মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন তাঁদের অগ্রনায়ক। মুসলমানদের শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক উন্নতির সাথে সাথে তাঁরা মুসলিম বাংলা, মুসলিম ভারত ও মুসলিম জগতের রাজনৈতিক অধিকারের কথাও চিন্তা করিতেন। জাতির এমন সন্ধিক্ষণে নেতাকে শুধু রাষ্ট্রীয় নেতা হইলেই চলে না। তাঁকে ধর্ম-কৃষ্টির প্যারিসম্যাটিক নেতাও হইতে হয়। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এই শ্রেণীর নেতা। তাঁর মধ্যে হইয়াছিল রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় উভয় নেতৃত্বের সংমিশ্রণ। তাঁর মিশন ছিল যুগপৎভাবে দুইটি: এক, বর্তমান গোলামি হইতে জাতির উদ্ধার। দুই, সুস্পষ্ট ভবিষ্যতে জাতির পদার্পণ। প্রথমটা সহজ। বর্তমানকে ঝাড়িয়া ফেলা। কিন্তু দ্বিতীয়টা কঠিন। আযাদী লাভের পরে কোন পথে যাইব? বন্দী মুক্তি পাইয়া বাড়ী যাইবে নিশ্চয়। কিন্তু বাড়ীটা চিনা থাকা দরকার। এটাই জানা ছিল মওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীদের। এই উদ্দেশ্যে মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা ইসলামাবাদী, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ দূরদর্শী আলেম আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা স্থাপন করেন এবং তার মুখপত্ররূপে 'আল ইসলাম' নামক উন্নত শ্রেণীর মাসিক কাগজ বাহির করেন ১৯১৩ সালে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বয়ং এই কাগজের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। মুসলিম বাংলা তথা সারা মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করার সাধু উদ্দেশ্যে তিনি এর আগেই সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' বাহির করিয়াছিলেন ১৯১১ সালে। পরের বৎসর ১৯১২ সালে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলিকাতা হইতে 'কমরেড' নামক সুবিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির করেন। এই সময় ইতালীর ত্রিপলি অধিকার, বলকান যুদ্ধে তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ খ্রিস্টানদের মধ্যে ভাগ করিয়া নেওয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধা প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার তোপের মুখে পড়িয়াও এই দেশ সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে নির্ভুল নেতৃত্ব দান করেন। ত্যাগের পথে, সংগ্রামের পথে জাতিকে ট্রেনিং দেন। এটা সত্যই কঠিন ছিল দুই কারণে। প্রথমতঃ এই সময়ে মুসলিম বাংলা বা মুসলিম ভারতে আসলে কোন রাজনৈতিক আদর্শ স্পষ্ট হইয়া দানা বাঁধে নাই। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সময় নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল। লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হইলেও এটা সত্য কথা যে, স্যার সৈয়দ আহমদ ও নবাব আবদুল লতিফের বাস্তববাসী দূরদর্শী নীতি পরবর্তীকালে স্বার্থপর সুবিধাবাদী রাজনীতিতে পরিণত হয়। নবাব মোহসেনুল মুল্ক ও নবাব ভিকারুল মুলক প্রমুখের নেতৃত্বে স্যার সৈয়দের নীতির অপভ্রংশের ধারা ও মিলামিল মুসলিম সমাজে চালু হয়, সেটাই রূপ পায় পরবর্তীকালে নাইট নবাব খান বাহাদুরদের আঞ্জুমনী রাজনীতিতে। বস্তুত উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে আঞ্জুমনী রাজনীতিই ছিল মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র রাজনীতি। মওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর সহকর্মীদের আঞ্জুমানে ওলামার মুবাল্লিগরা যখন বাংলার মফস্বলে মুসলিম স্বকীয়তার প্রচার করেন, তখন প্রতি জেলা হেড কোয়ার্টারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পৃষ্ঠপোষিত ও খান বাহাদুরদের পরিচালিত একটি করিয়া আঞ্জুমানে ইসলামিয়া বিদ্যমান ছিল। লোট-বেলাটকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া, সকল কাজে সরকারের সমর্থন দেওয়া এবং কংগ্রেসী, খেলাফতি বা অন্য যে কোনও প্রকারের আন্দোলনের নিন্দা করাই ছিল এই আঞ্জুমানগুলির কাজ। ইহাদের কবল হইতে মুসলিম জনসাধারণকে উদ্ধার করাই ছিল মওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর সহকর্মীদের কাজ। এটাই ছিল এঁদের এই যুগের ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব। এই সময়ে মুসলিম বাংলা তথা সারা মুসলিম ভারতে রাজনীতির দুইটি ধারা বিদ্যমান ছিল। একটি, নাইট-নবাব-খানবাহাদুরী রাজনীতি; অপরটি প্রগতিবাদী স্বাধীন রাজনীতি। একটির সিলসিলা নবাব মোহসিনুল মুলক প্রমুখের কথা আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়টির সিলসিলা শেখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, কায়েদে আযম জিন্নাহ, মওলানা আজাদ ও মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মৌঃ আবুল কাসেম, মৌঃ মুজিবুর রহমান, মৌঃ আবদুর রসুল প্রমুখ কিছু লোক প্রগতিমূলক স্বাধীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিলেও অধিকাংশই ছিলেন ঐ আঞ্জুমনী রাজনীতিতে বিশ্বাসী।
ইহাদেরই মোকাবেলায় মওলানা আকরম খাঁ ও তাঁর সহকর্মীরা কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের এবং পরে প্রজা আন্দোলনের মধ্য দিয়া মুসলিম জনতা ও ছাত্র তরুণদের মধ্যে একদল ত্যাগী, সাহসী ও সংগ্রামী কর্মী তৈয়ার করেন, যারা পরবর্তীকালে কায়েদে আযমের নেতৃত্বে পাকিস্তান সংগ্রামের সৈন্য বাহিনীতে পরিণত হয়। মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব এখান হইতেই সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। মওলানা সাহেব তাঁর 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে যেভাবে আমাদের রাজনৈতিক ও তামুদ্দুনিক আযাদী হাসিল করিয়াছিলেন, সেই সাম্প্রতিক ঘটনাই তাঁর দূরদর্শী রাজনীতির স্বাভাবিক পূর্ণতা লাভ। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার এত ডামাডোলের এবং জেল-জুলুমের মধ্যেও মওলানা সাহেব ‘কুরআন শরীফের তর্জমা’, ‘মোস্তফা চরিত’, ‘সমস্যা ও সমাধান’ ও ‘মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’-এর মত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় পুস্তক রচনা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তার কারণ সুস্পষ্ট। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে শুধু বৈষয়িক রাজনীতি মনে করিতেন না। এটাকে মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও পুনর্জাগরণের আন্দোলন মনে করিতেন। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তায় কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। শুধু রাজনৈতিক মুক্তিই যে আমাদের প্রকৃত আজাদী আনিবে না, সেই সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক আজাদীও অপরিহার্য-এ বিষয়ে ছিলেন তিনি সচেতন ও অতন্দ্র। সে জন্য তিনি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ উচ্ছেদের জন্য প্রজা আন্দোলনের জন্ম দেন। এ অন্যায় ও বেআইনী বন্দোবস্তের দ্বারা ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ শাসন বাংলার উপর যে আঘাত হানিয়াছিল, সোয়া শ বছর পরে মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাংলা তার জবাব দিয়াছিল ১৯২৯ সালে প্রজা সমিতি গঠন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ দাবি করিয়া। বস্তুত মুসলিম বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির এটাই ছিল প্রথম দাবি।
বস্তুত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর জীবনেতিহাস মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের সামগ্রিক পুনর্জাগরণের পরিপূর্ণ রেনেসাঁরই ইতিহাস। ‘আজাদ’ ও ‘মোহাম্মদী’র অসংখ্য প্রবন্ধে ও তাঁর রচিত বই-পুস্তকে তিনি মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ রূপায়ণে যে সুস্পষ্ট চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন তাতে দেখা যায়, মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কত সুন্দর রংগীন স্বপ্নই না দেখিয়াছিলেন।
তাঁর সে স্বপ্ন সফল হউক, তাঁর পরিকল্পনামত মুসলিম জাতির সর্বাঙ্গীণ সামগ্রিক পুনর্জাগরণ ঘটুক, তিনি বেহেশতে বসিয়া আমাদের উন্নতিতে গৌরবের হাসি হাসুন। এই মোনাজাত করিয়া আজ আমি তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আমিন।
সৌজন্য : মওলানা আকরম খাঁ (স্মারক), আবু জাফর সংকলিত ও সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন