
মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি
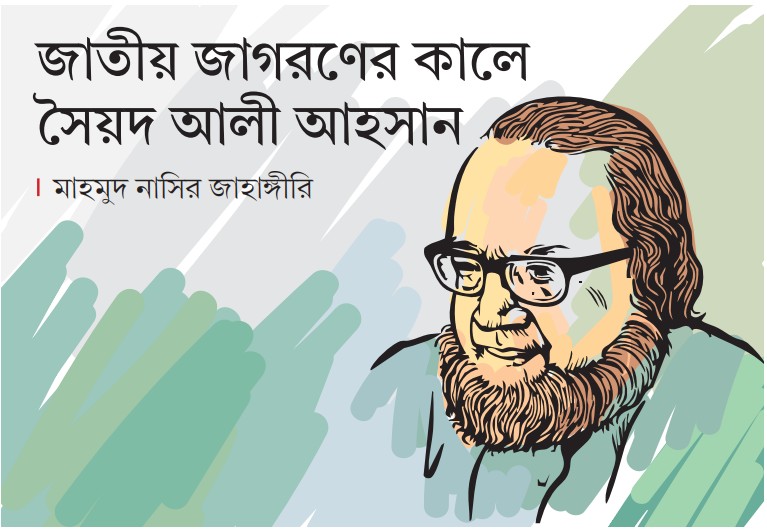
আরমানিটোলা স্কুলের ম্যাগাজিনে ১৯৩৭ সালে ‘দি রোজ’ নামে ইংরেজি কবিতা লিখে আত্মপ্রকাশ করেন সৈয়দ আলী আহসান (২৬ মার্চ ১৯২২-২৫ জুলাই ২০০২)। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার আগে ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম। সে সময় ইংরেজি কবিতা শিখতে হতো ছন্দ বুঝে। কাজেই সৈয়দ আলী আহসান গ্রের বিখ্যাত কবিতা এলিজির অনুকরণে লেখেন তার প্রথম কবিতা। চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ, গোলাম কুদ্দুস, মোফাখখারুল ইসলাম ও তালিম হোসেনের আদর্শ ছিলেন কবি ইকবাল। একই ধারায় আরবি-ফারসি শব্দাকীর্ণ প্রথম কাব্য চাহার দরবেশ রচিত হয় ১৯৪৫ সালে। তবে ভাষা আন্দোলনের পর দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসানই সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হন ভাষা আন্দোলনের চেতনা দিয়ে। ভাষা আন্দোলনের পরও স্বাতন্ত্র্যবাদী কবিতা লিখে গেছেন গোলাম মোস্তফা, সুফী জুলফিকার হায়দার, রওশন ইয়াজদানী প্রমুখ, কিন্তু ব্যতিক্রম সৈয়দ আলী আহসান। ব্যাপক বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অনেক আকাশ (১৯৫৯) কাব্যে প্রধান হয়ে ওঠে বাংলা শব্দের বহুবর্ণিল তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার। একক সন্ধ্যায় বসন্ত কাব্যে (১৯৬২) মূল বিষয় হয়ে ওঠে দেশপ্রেম। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব বাংলার নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু তার কবিতায় বাংলাদেশ তখনো পূর্ব বাংলা:
‘আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল।
অনেক পাতায় ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।’
স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২-৭৫ সালে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫-৭৭ সালে উপাচার্য ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবং পদাধিকারবলে বাংলা একাডেমির সভাপতি। ১৯৭৮ সালের ২৪ জুলাই থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রফেসর হিসেবে তিনি আবার যোগ দেন। তবে তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলাদেশের জনজাগরণকালের সঙ্গেই যুক্ত। জাতীয় জাগরণের কালে তিনি ছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৫৩-১৯৬০), বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক (১৯৬০-১৯৬৭) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৬৭-৭১)।
ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ—এ সময়টা তার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। দুটি আন্দোলনেই তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুনীর চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে, যার অন্তর্ভুক্ত এআর মল্লিক। বাংলাদেশের বাইরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সম্প্রসারণশীল ভাষাচেতনার পরিচয়ের শুরু।
সৈয়দ আলী আহসানের উদ্যোগে করাচির দুটি কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। করাচিপ্রবাসী বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজ দুটিতে ইন্টারমিডিয়েট ও বিএ শ্রেণিতে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ সময় করাচির সিন্ধু মুসলিম কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান মুহম্মদ ফারুক। মুহম্মদ ফারুক (১৯৩১-১৯৯৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, যে বছর সৈয়দ আলী আহসান করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। সৈয়দ আলী আহসান প্রকাশ করেন অর্ধবার্ষিক ‘Bengali Literary Review’। মুহম্মদ ফারুক সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে এ পত্রিকা সম্পাদনায় সহায়তা করেন। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র Bengali Literary Review (April 1960, vol.5, no.1) পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শহীদুল্লাহ্কৃত ‘আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়’ নামে ৫০টি চর্যাগীতির পাঠ ও পাঠান্তর, সঙ্গে বাংলায় ও ইংরেজিতে অনুবাদ তাতে স্থান পায়।
স্বায়ত্তশাসনের কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা যখন পৃথক বিভাগের মর্যাদা পায়, তখন চর্যাপদ প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিসে। ভাষা আন্দোলনের পর তার পুনরাবৃত্তি হয় করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন একই সঙ্গে পাঠ্য ছিল ঢাকা, রাজশাহী ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা একাডেমি এটা প্রকাশ করে ১৯৬৬ সালে, যখন সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন পরিচালক।
বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে সৈয়দ আলী আহসানের কাল (১৫ ডিসেম্বর ১৯৬০-১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭) অসংখ্য সাহিত্যসভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্মৃতিসভার জন্য স্মরণীয়। বর্ধমান হাউসের দোতলার ওপর তিনতলা নির্মাণ করা হয় তার সময়। এখানেই ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী। কর্মমুখর ও আধুনিক হয়ে ওঠে বাংলা একাডেমি। ৫ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা থেকে পরিচালক নিজে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। বইয়ের মাপ আগে ছিল রয়াল; সৈয়দ আলী আহসান বইয়ের মাপ কমিয়ে করেন ডবল ডিমাই। আগে সরকারি কাজে ব্যবহার করা হতো সাধু ভাষা; তার সময় থেকে প্রচলিত হয় চলিত ভাষা। সবুজপত্রের যুগে প্রবেশ করে বাংলা একাডেমি। আগে বের হতো বছরে তিনটি সংখ্যা, এখন থেকে হলো ত্রৈমাসিক।
ড. এনামুল হকের সময় গবেষণা, অনুবাদ, প্রকাশন, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক বিভাগ শুধুই ছিল প্রাথমিক স্তরের পরিকল্পনা, সৈয়দ আলী আহসানের সময় হয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। ১৯৬১ সাল তার কর্মোদ্দীপনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বছর। ১৯৬১ সালে ভাষাশহিদদের স্মরণে স্মারক একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান হয়। এর আগে একুশে ফেব্রুয়ারির কোনো অনুষ্ঠান হয়নি একাডেমিতে। প্রথম আলোচনা সভায় ড. শহীদুল্লাহ্, আবুল কাসেম, মুনীর চৌধুরী ও আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করেন এবং তার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯৬১ সালে শুরু হয় বাংলা পাঠ্যক্রম।
অবাঙালিদের সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে কাজ চালানোর উপযোগী বাংলা শেখানোর জন্য একাডেমি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে, অনেকটা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মতো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বাংলা একাডেমি। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোট দেড়শর মতো শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামান, আবদুল হাই প্রমুখ। ছাত্রদের মধ্যে কেউ এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ১৯৬১ সাল বিশেষভাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে নাট্যোৎসবের জন্য। বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় আসকার ইবনে শাইখের রক্তপদ্ম (১৯৫৭), ফররুখ আহমদের নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), সিকান্দার আবু জাফরের শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫২), মুনীর চৌধুরীর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে যুদ্ধবিরোধী নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬১), সৈয়দ আলী আহসানের ইডিপাস রেক্সের অনুবাদ এবং আমেরিকার বিখ্যাত পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার থর্নটন ওয়াইল্ডারের আওয়ার টাউন।
১৯৬১ সাল বাংলা একাডেমিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সম্পাদক হিসেবে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের জন্যও বিখ্যাত। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয় ড. এনামুল হকের সময় (১ ডিসেম্বর ১৯৫৬-১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০)। ড. শহীদুল্লাহ্র যোগদানের মাধ্যমে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে, তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-৬৮ কালে। ড. এনামুল হক, মুহম্মদ আব্দুল হাই, মুনীর চৌধুরী ও ড. দীন মুহম্মদকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।
সৈয়দ আলী আহসানের সময়েই ড. শহীদুল্লাহ্র পরিপূর্ণ অভিষেক হয় বাংলা একাডেমিতে। শুধু তার জন্মবার্ষিকী পালনই নয়, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা ও বিদায় সংবর্ধনা সবই হয় তার নেতৃত্বে। ১৯৬২ সালের ১৩ জুলাই শুক্রবার ড. শহীদুল্লাহ্র ৭৭তম জন্মবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে শুরু হয় জন্মতিথির উৎসব। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে একাডেমি প্রাঙ্গণে বিশেষ সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. শহীদুল্লাহ্। ১৯৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলা লিপি ও বানান সমস্যার বিষয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান। ড. শহীদুল্লাহ্ এ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পড়েন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে ড. শহীদুল্লাহ্, এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ডিপিআই ফেরদাউস খান ও মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ভাষা ও ব্যাকরণ সংস্কার করার সুপারিশ করে।
ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা একাডেমি ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহের কাজে বিশেষ তৎপর হয়। একাডেমির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩০০টি দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুথির মধ্যে আলাওলের বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল ৩৪। তার সময়েই পুথিসাহিত্য সংগ্রহ ও পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা কেটে যায়। ১৯৬০-৬৬ কালপর্বে আবদুস সাত্তার চৌধুরী (১৯১৯-৮২) সংগ্রহ করেন সাতশর বেশি পুথি। চট্টগ্রামের পুথিসংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরীকে বলা যায় সৈয়দ আলী আহসানেরই আবিষ্কার।
১৯৬৬ সালে ড. এআর মল্লিককে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবসৃষ্ট বাংলা বিভাগে সৈয়দ আলী আহসানের যোগদানের পর ১৯৬৭-৭১ কালে পুথিপাণ্ডুলিপি সংগ্রহের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সাহিত্য সমিতির মুখপত্র হিসেবে তিনি প্রকাশ করেন পাণ্ডুলিপি সাহিত্য সংকলন। এ পর্বে আবদুস সাত্তার চৌধুরী সংগ্রহ করেন প্রায় ৯০০ পুথিপাণ্ডুলিপি। ড. শহীদুল্লাহ্ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সৈয়দ আলী আহসান সংগ্রহ করেন আবদুস সাত্তার পুথিবিশারদের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই সম্ভবত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈয়দ আলী আহসানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পুথির সবচেয়ে উর্বরভূমি চট্টগ্রামের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তার নেতৃত্বে হয়ে ওঠে পুথিসাহিত্যের প্রধান তীর্থস্থান হিসেবে। এ সময়েই সৈয়দ আলী আহসান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মশতবার্ষিকীতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় ১৯৬৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর।
৮০ বছরের জীবনে প্রায় বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ছিল তার কর্মোদ্দীপনা। তবে শেষ মৃত্যুশয্যা বেছে নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতেই। আশির দশকের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক। আমাদের পড়াতেন আধুনিক বাংলা কবিতা। তার লেখা আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০) বইটি হাতে নিয়ে পায়চারি করতে করতে তিনি বক্তৃতা করতেন। কালের বিচারে ২০২২ সাল ছিল সৈয়দ আলী আহসানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী; যেমন ১৯৬১ সালে ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ, একই সঙ্গে ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক অনুষঙ্গ ও হাজার বছরের ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসাধককে শ্রদ্ধা।
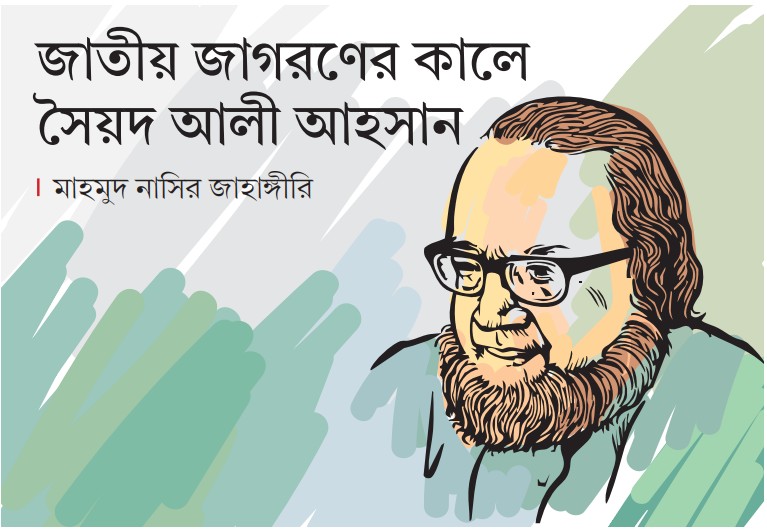
আরমানিটোলা স্কুলের ম্যাগাজিনে ১৯৩৭ সালে ‘দি রোজ’ নামে ইংরেজি কবিতা লিখে আত্মপ্রকাশ করেন সৈয়দ আলী আহসান (২৬ মার্চ ১৯২২-২৫ জুলাই ২০০২)। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার আগে ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম। সে সময় ইংরেজি কবিতা শিখতে হতো ছন্দ বুঝে। কাজেই সৈয়দ আলী আহসান গ্রের বিখ্যাত কবিতা এলিজির অনুকরণে লেখেন তার প্রথম কবিতা। চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ, গোলাম কুদ্দুস, মোফাখখারুল ইসলাম ও তালিম হোসেনের আদর্শ ছিলেন কবি ইকবাল। একই ধারায় আরবি-ফারসি শব্দাকীর্ণ প্রথম কাব্য চাহার দরবেশ রচিত হয় ১৯৪৫ সালে। তবে ভাষা আন্দোলনের পর দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসানই সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হন ভাষা আন্দোলনের চেতনা দিয়ে। ভাষা আন্দোলনের পরও স্বাতন্ত্র্যবাদী কবিতা লিখে গেছেন গোলাম মোস্তফা, সুফী জুলফিকার হায়দার, রওশন ইয়াজদানী প্রমুখ, কিন্তু ব্যতিক্রম সৈয়দ আলী আহসান। ব্যাপক বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অনেক আকাশ (১৯৫৯) কাব্যে প্রধান হয়ে ওঠে বাংলা শব্দের বহুবর্ণিল তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার। একক সন্ধ্যায় বসন্ত কাব্যে (১৯৬২) মূল বিষয় হয়ে ওঠে দেশপ্রেম। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব বাংলার নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু তার কবিতায় বাংলাদেশ তখনো পূর্ব বাংলা:
‘আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল।
অনেক পাতায় ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।’
স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২-৭৫ সালে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৫-৭৭ সালে উপাচার্য ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবং পদাধিকারবলে বাংলা একাডেমির সভাপতি। ১৯৭৮ সালের ২৪ জুলাই থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রফেসর হিসেবে তিনি আবার যোগ দেন। তবে তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলাদেশের জনজাগরণকালের সঙ্গেই যুক্ত। জাতীয় জাগরণের কালে তিনি ছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৫৩-১৯৬০), বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক (১৯৬০-১৯৬৭) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৬৭-৭১)।
ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ—এ সময়টা তার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। দুটি আন্দোলনেই তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুনীর চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে, যার অন্তর্ভুক্ত এআর মল্লিক। বাংলাদেশের বাইরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সম্প্রসারণশীল ভাষাচেতনার পরিচয়ের শুরু।
সৈয়দ আলী আহসানের উদ্যোগে করাচির দুটি কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। করাচিপ্রবাসী বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজ দুটিতে ইন্টারমিডিয়েট ও বিএ শ্রেণিতে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ সময় করাচির সিন্ধু মুসলিম কলেজে বাংলার অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান মুহম্মদ ফারুক। মুহম্মদ ফারুক (১৯৩১-১৯৯৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, যে বছর সৈয়দ আলী আহসান করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। সৈয়দ আলী আহসান প্রকাশ করেন অর্ধবার্ষিক ‘Bengali Literary Review’। মুহম্মদ ফারুক সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে এ পত্রিকা সম্পাদনায় সহায়তা করেন। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র Bengali Literary Review (April 1960, vol.5, no.1) পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শহীদুল্লাহ্কৃত ‘আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়’ নামে ৫০টি চর্যাগীতির পাঠ ও পাঠান্তর, সঙ্গে বাংলায় ও ইংরেজিতে অনুবাদ তাতে স্থান পায়।
স্বায়ত্তশাসনের কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা যখন পৃথক বিভাগের মর্যাদা পায়, তখন চর্যাপদ প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিসে। ভাষা আন্দোলনের পর তার পুনরাবৃত্তি হয় করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন একই সঙ্গে পাঠ্য ছিল ঢাকা, রাজশাহী ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা একাডেমি এটা প্রকাশ করে ১৯৬৬ সালে, যখন সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন পরিচালক।
বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে সৈয়দ আলী আহসানের কাল (১৫ ডিসেম্বর ১৯৬০-১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭) অসংখ্য সাহিত্যসভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্মৃতিসভার জন্য স্মরণীয়। বর্ধমান হাউসের দোতলার ওপর তিনতলা নির্মাণ করা হয় তার সময়। এখানেই ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী। কর্মমুখর ও আধুনিক হয়ে ওঠে বাংলা একাডেমি। ৫ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা থেকে পরিচালক নিজে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। বইয়ের মাপ আগে ছিল রয়াল; সৈয়দ আলী আহসান বইয়ের মাপ কমিয়ে করেন ডবল ডিমাই। আগে সরকারি কাজে ব্যবহার করা হতো সাধু ভাষা; তার সময় থেকে প্রচলিত হয় চলিত ভাষা। সবুজপত্রের যুগে প্রবেশ করে বাংলা একাডেমি। আগে বের হতো বছরে তিনটি সংখ্যা, এখন থেকে হলো ত্রৈমাসিক।
ড. এনামুল হকের সময় গবেষণা, অনুবাদ, প্রকাশন, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক বিভাগ শুধুই ছিল প্রাথমিক স্তরের পরিকল্পনা, সৈয়দ আলী আহসানের সময় হয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। ১৯৬১ সাল তার কর্মোদ্দীপনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বছর। ১৯৬১ সালে ভাষাশহিদদের স্মরণে স্মারক একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান হয়। এর আগে একুশে ফেব্রুয়ারির কোনো অনুষ্ঠান হয়নি একাডেমিতে। প্রথম আলোচনা সভায় ড. শহীদুল্লাহ্, আবুল কাসেম, মুনীর চৌধুরী ও আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করেন এবং তার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯৬১ সালে শুরু হয় বাংলা পাঠ্যক্রম।
অবাঙালিদের সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে কাজ চালানোর উপযোগী বাংলা শেখানোর জন্য একাডেমি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করে, অনেকটা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মতো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বাংলা একাডেমি। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোট দেড়শর মতো শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামান, আবদুল হাই প্রমুখ। ছাত্রদের মধ্যে কেউ এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ১৯৬১ সাল বিশেষভাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে নাট্যোৎসবের জন্য। বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় আসকার ইবনে শাইখের রক্তপদ্ম (১৯৫৭), ফররুখ আহমদের নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), সিকান্দার আবু জাফরের শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫২), মুনীর চৌধুরীর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে যুদ্ধবিরোধী নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬১), সৈয়দ আলী আহসানের ইডিপাস রেক্সের অনুবাদ এবং আমেরিকার বিখ্যাত পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার থর্নটন ওয়াইল্ডারের আওয়ার টাউন।
১৯৬১ সাল বাংলা একাডেমিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সম্পাদক হিসেবে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের জন্যও বিখ্যাত। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয় ড. এনামুল হকের সময় (১ ডিসেম্বর ১৯৫৬-১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০)। ড. শহীদুল্লাহ্র যোগদানের মাধ্যমে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে, তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-৬৮ কালে। ড. এনামুল হক, মুহম্মদ আব্দুল হাই, মুনীর চৌধুরী ও ড. দীন মুহম্মদকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।
সৈয়দ আলী আহসানের সময়েই ড. শহীদুল্লাহ্র পরিপূর্ণ অভিষেক হয় বাংলা একাডেমিতে। শুধু তার জন্মবার্ষিকী পালনই নয়, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা ও বিদায় সংবর্ধনা সবই হয় তার নেতৃত্বে। ১৯৬২ সালের ১৩ জুলাই শুক্রবার ড. শহীদুল্লাহ্র ৭৭তম জন্মবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে শুরু হয় জন্মতিথির উৎসব। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে একাডেমি প্রাঙ্গণে বিশেষ সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. শহীদুল্লাহ্। ১৯৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলা লিপি ও বানান সমস্যার বিষয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান। ড. শহীদুল্লাহ্ এ বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পড়েন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে ড. শহীদুল্লাহ্, এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ডিপিআই ফেরদাউস খান ও মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ভাষা ও ব্যাকরণ সংস্কার করার সুপারিশ করে।
ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা একাডেমি ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহের কাজে বিশেষ তৎপর হয়। একাডেমির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩০০টি দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুথির মধ্যে আলাওলের বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল ৩৪। তার সময়েই পুথিসাহিত্য সংগ্রহ ও পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা কেটে যায়। ১৯৬০-৬৬ কালপর্বে আবদুস সাত্তার চৌধুরী (১৯১৯-৮২) সংগ্রহ করেন সাতশর বেশি পুথি। চট্টগ্রামের পুথিসংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরীকে বলা যায় সৈয়দ আলী আহসানেরই আবিষ্কার।
১৯৬৬ সালে ড. এআর মল্লিককে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবসৃষ্ট বাংলা বিভাগে সৈয়দ আলী আহসানের যোগদানের পর ১৯৬৭-৭১ কালে পুথিপাণ্ডুলিপি সংগ্রহের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সাহিত্য সমিতির মুখপত্র হিসেবে তিনি প্রকাশ করেন পাণ্ডুলিপি সাহিত্য সংকলন। এ পর্বে আবদুস সাত্তার চৌধুরী সংগ্রহ করেন প্রায় ৯০০ পুথিপাণ্ডুলিপি। ড. শহীদুল্লাহ্ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সৈয়দ আলী আহসান সংগ্রহ করেন আবদুস সাত্তার পুথিবিশারদের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই সম্ভবত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈয়দ আলী আহসানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পুথির সবচেয়ে উর্বরভূমি চট্টগ্রামের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তার নেতৃত্বে হয়ে ওঠে পুথিসাহিত্যের প্রধান তীর্থস্থান হিসেবে। এ সময়েই সৈয়দ আলী আহসান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মশতবার্ষিকীতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয় ১৯৬৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর।
৮০ বছরের জীবনে প্রায় বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ছিল তার কর্মোদ্দীপনা। তবে শেষ মৃত্যুশয্যা বেছে নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতেই। আশির দশকের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক। আমাদের পড়াতেন আধুনিক বাংলা কবিতা। তার লেখা আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০) বইটি হাতে নিয়ে পায়চারি করতে করতে তিনি বক্তৃতা করতেন। কালের বিচারে ২০২২ সাল ছিল সৈয়দ আলী আহসানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী; যেমন ১৯৬১ সালে ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ, একই সঙ্গে ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক অনুষঙ্গ ও হাজার বছরের ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসাধককে শ্রদ্ধা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন বলেছেন, ছাত্রদল নেতা ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়েদ হোসাইন হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে—কেউ যেন আইনের ফাঁক দিয়ে কেউ বেরিয়ে না যায়।
২৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী রিয়াদ হাসানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বোরকা ও পর্দাশীল নারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। এই মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।
১ ঘণ্টা আগে
সমাবেশে জোবায়েদের সহপাঠী সজল খান বলেন, “পুলিশ এখনো বর্ষার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। শুধু বর্ষা ও মাহির নয়, এই ঘটনায় বর্ষার পরিবারও জড়িত। গতকাল আদালতে আমাদের সঙ্গে পুলিশের আচরণ ছিল অমানবিক। আমাদের এক বান্ধবী ভিডিও করতে গেলে তার ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। আমরা পুলিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই।”
১ ঘণ্টা আগে
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ আইনের মামলায় বুয়েটের ২১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত রায়কে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে জামিনের বিষয়ে অধিকতর শুনানির জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন বিচার
২ ঘণ্টা আগে