বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অনালোচিত অধ্যায়

শামসুদ্দিন ইলিয়াস
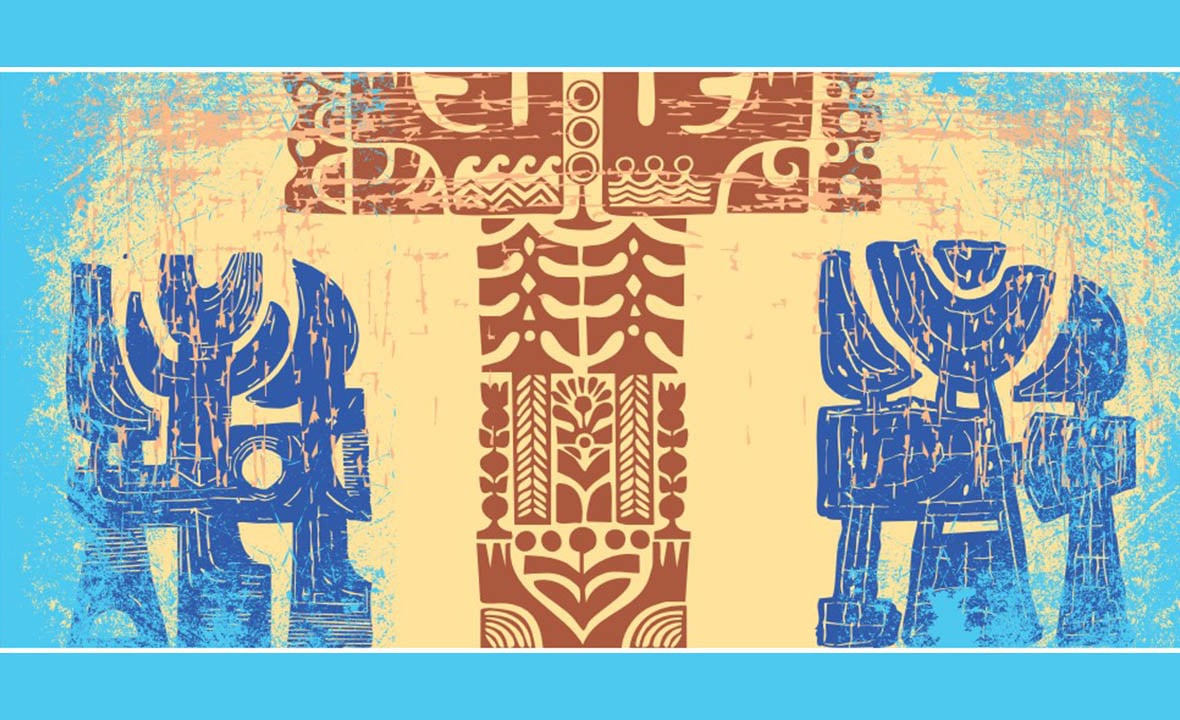
‘বাংলা ভাষার সৌভাগ্য যে, উদ্ভব-মুহূর্তে এক উদার রাজশক্তির সাহচর্য লাভ করেছে। যার ফলে তার পূর্ণ বিকাশ কেবল ত্বরান্বিত হয়নি, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্যে সঞ্জীবিত ও নবশক্তির সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পেরেছে।’—ড. ওয়াকিল আহমদের এ মতের যথার্থ নজির বাংলা সাহিত্যের অনোন্মোচিত যুগের পাতায় পাতায়, ভাষা-ইতিহাসের পরতে পরতে। সে উদার রাজশক্তির ঔদার্যচিহ্ন অনুসন্ধানের আগে অনুধাবন প্রয়োজন শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের সিদ্ধান্ত—‘বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।’ এ দাবির আরো সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন ড. এসএম লুৎফর রহমান—‘কেবল বাংলায় নয়, গোটা উপমহাদেশে ৫৪৪টি (মতান্তরে আরো বেশি) ভাষা উপভাষার মধ্যে প্রায় সৃষ্টি ভাষা মুছলিম শাসন কায়েমের পরে মুছলমানরাই সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষা তার একটি মাত্র।’
বাংলা ভাষার উদ্ভবকালে বাংলার শাসনক্ষমতায় ছিল পাল রাজবংশ—ধর্মে বৌদ্ধ, নীতিতে উদারপন্থি। বাংলা ভাষার জন্ম এবং বাংলা সাহিত্যের আদি লিখিত নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয়েছিল এ সময়ে।
প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করা পাল রাজবংশকে পরাজিত করে বাংলার ক্ষমতা দখলে নেয় দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন রাজবংশ। ধর্মে তারা হিন্দু, সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ। বাংলার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যবাদের গজিয়ে ওঠা সেনদের মাধ্যমে, সে সময়ে। ক্ষমতা দখলের পর সেন রাজবংশ বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অতিকায় আগ্রাসী হয়ে ওঠে। জাতিগত নিধন চালায় বৌদ্ধদের ওপর। নিধনযজ্ঞ শুধু মানুষ হত্যায় সীমিত ছিল না, সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-ধর্ম সমূলে নির্মূলের নৃশংসতা ছিল সেনদের স্বাভাবিক তৎপরতা। ওয়াকিল আহমদ জানান, ‘বাঙ্গালী বৌদ্ধ নিধন-পর্ব কেবল সমাপ্ত হল না, তাদের কৃষ্টিকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলল। বৌদ্ধরা সেদিন নেপালে পালিয়ে গিয়ে এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ হতে চর্যাপদের অবলুপ্তি রোধ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যরোষে কত বাংলা-বৌদ্ধ গ্রন্থের সেদিন মৃত্যু-সমাধি রচিত হয়েছিল, আজ তার কে হিসাব দেবে?’
সেন রাজবংশের চতুর্থ রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন কবি। সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি-পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল তার রাজসভায়। জয়দেব, উমাপতি ধর, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন তাদের মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্মণ সেন এবং তার রাজসভার কবিকুল ছিলেন ‘বাংলাদেশি’, ‘বাংলাভাষী’। কিন্তু বাংলা ভাষার কবি ছিলেন না। সাহিত্যচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত। মূলত সংস্কৃত মুখের ভাষা হতে অসমর্থ এক ভাষার নাম।
বাংলা ভাষা সেন রাজাদের নির্মূলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার কারণ তাদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা। তারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। বাংলা মানুষের মুখের ভাষা হলেও তাদের চর্চার ভাষা ছিল না। দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন তার কারণ—“ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী ‘দূর দূর’ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন, বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল—তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।”
সেনদের বাংলা বিদ্বেষ বিষয়ে তিনি আশঙ্কা করেন—‘দেবভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতগণের বাংলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোনো কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না।”
ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জীবনের জন্য এক উদার রাজদৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষক সাহচর্য প্রত্যাশিত ছিল, যাতে উন্মুখ জনসাধারণ দুর্বোধ্য সংস্কৃতের দাসত্ব ছিন্ন করে প্রাণের ভাষার মুক্ত চর্চা করতে পারে। বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা না ঘটলে বাংলা ভাষা হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়নে নির্জীব এমনকি নির্ভুল হতে পারত। আরো অগ্রসর অভিমত ব্যক্ত করেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান—‘মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। এটা বাংলাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি উৎসাহিত হয়। যদি বাংলায় মুসলিম-বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ প্রদেশে আর কয়েক শতকের জন্যে হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকত, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।’ মুসলমান সুলতানদের ঔদার্যই প্রাণহীন বাংলা ভাষা প্রাণবন্ত করেছে। রাজানুকূল্য বাংলা সাহিত্যে করেছে ফুলে-ফলে-পত্রপল্লবে বিকশিত।
১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন। বাংলার ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রকৃত সমৃদ্ধির সূচনা হয়। তার পরের শতাব্দীকালজুড়ে মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার ও স্থিতি স্থাপনের সংগ্রাম চলে। সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে মুসলিম রাজশক্তি বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে তৎপর হন।
মুসলিম শাসকদের ভাষা ছিল তুর্কি, রাজভাষা ফারসি। তৎকালীন বিশ্বসভ্যতায় দুটো ভাষাই সাহিত্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। তবু মুসলমান সুলতান ও আমির-মালিকগণ জনসাধারণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এর কারণ ইসলামের উদারতা, উচ্চ মূল্যবোধ, বৈষম্যহীন আদর্শ এবং উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি সুলতানদের অত্যাগ্রহ।
ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব-ইরান-তুরান থেকে আগত সুফি-দরবেশ ও উলামাসমাজ উপলব্ধি করলেন, বাংলার জনসাধারণ আরবি, ফারসি ও তুর্কির সঙ্গে অপরিচিত। সুতরাং সাধারণের ভাষা বাংলায় ধর্ম-সমাজ বিষয়ক বইপুস্তক লেখা তারা কর্তব্য মনে করেন। বাংলার অধিবাসীদের স্থানীয় ভাষায় মানবীয় শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনবোধ করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলা ভাষা এক নবজীবন লাভ করে, জনসাধারণ ও রাজদরবারের মাঝে সৌভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধসেতু স্থাপন করে।
মুসলমান শাসকবর্গ বাংলাদেশেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। বাংলাদেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন, এ মাটির সন্তান হিসেবে নিজেদের পরিচয় ধারণ করেন। এ দেশের আদি অধিবাসীদের মতো বাংলা তাদেরও ভাষা হিসেবে আদরিত হয়।
মুসলিম শাসনামলে বিপুল উন্নতি সাধিত হয় হিন্দু সমাজের। হিন্দুদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরাও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, ধর্মীয় গ্রন্থপাঠের অধিকার পায়। অথচ মুসলিম-পূর্ব সেনযুগে শিক্ষাগ্রহণ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণ শ্রেণির দখলে ছিল। শিক্ষাদীক্ষা হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এমনকি, ধোপা-নাপিত শ্রেণির লোকেরাও সাহিত্যে ও জ্ঞানানুশীলনে খ্যাতিমান হয়। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনই এ কথা প্রথম উচ্চারণ করেন যে, মুসলমানেরা ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান থেকেই আসুন না কেন এদেশে এসে তারা সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে পড়েন। হিন্দুদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানার কৌতূহল দেখা যায়। তাই তারা সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে প্রেরণা দেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা কেবল প্রয়োজনবোধে প্রয়োগসিদ্ধ ছিল না, আস্বাদন-কাম্য অন্তরবাসনাও সক্রিয় ছিল। ড. সেন লেখেন, ‘পাঠান প্রাধান্যকালে (মুসলমান) বাদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্র অনেক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মৰ্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গালা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।’
অথচ ‘মুসলমান ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার কবিগণ কোন হিন্দু রাজার কাছ থেকে সহযোগিতা বা দাক্ষিণ্য পাননি।’—জানান ড. ওয়াকিল আহমদ। এমনকি সেনযুগের ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে এ অলীক ধর্মবাণী প্রচার করেছিলেন, ‘যারা অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে, তারা রৌরব নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।’
মুসলিম সুলতানগণ বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষারও মূল্যায়ন করেছেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করান। তার একটি দর্শন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সুলতানের নাম অনুসারে ‘দালাইল-ই-ফিরোজ শাহী’ কৃত হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের সংস্কৃতি অনুরাগ বিশ্ববিদিত। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ ছাড়াও তার পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। বহু সংস্কৃত পণ্ডিত গ্রন্থ প্রণয়ন ও কৃতিত্বের জন্য সম্রাট আকবর থেকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন লাভ করেন। সম্রাট শাহজাহান জাহাঙ্গীর এবং দারাশিকোও ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক।
মুসলমান শাসকদের জ্ঞানদীপ্ত পরিবেশ ও উদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হয়ে হিন্দু কবিগণ বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগের সুযোগ লাভ করেন। ফলে হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যসমূহ এর উজ্জ্বল প্রমাণ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর যে গ্রন্থটি রচনাকাল বিবেচনায় প্রাচীনতা দাবি করে তা ‘ইউসুফ-জুলেখা’। রচয়িতা মধ্যযুগের মুসলিম কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর। পবিত্র কোরআনের সুরা ইউসুফের কাহিনি অবলম্বনে এ কাহিনি কাবাব রচনায় কবি একজন ‘রাজেশ্বর’-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্য পেয়েছিলেন। কাব্যের বন্দনা অংশে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে মহান ‘রাজেশ্বর’ ছিলেন কবি ও কাব্যানুরাগী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ।
সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ ছিলেন ‘রামায়ণ’ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক। কৃত্তিবাস ছিলেন কবি যশপ্রার্থী। সুলতানের আদেশে তিনি সংস্কৃত থেকে ‘রামায়ণ’ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ ও ‘লক্ষ্মী চরিত্র’ রচনা করেন মালাধর বসু। তার কাব্যকৃতি সুলতানকে সন্তুষ্ট করে। তাই মালাধর বসুকে সুলতান ‘গুণরাজ খান’ উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘মনসা বিজয়’ কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন বিপ্রদাস। হোসেন শাহের সময়কালে আরেকজন শক্তিমান খুবই বিজয় গুপ্ত। তার কাব্য ‘পদ্মপুরাণ’ বা ‘মনসামঙ্গল’।
কবি যশোরাজ খান সুলতান হোসেন শাহের অধীনে রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শাহী আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রচনা করেন ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুলতানের আগ্রহ ও উন্নতিকল্পে পৃষ্ঠপোষকতায় কৃতজ্ঞ হয়ে সুলতানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীকর নন্দীর ‘মহাভারত’ কাব্য সুলতান নুসরত শাহের আমলে ছুটি খানের আদেশে রচিত হয়েছিল। কবি শ্রীধর যুবরাজ ফিরোজ শাহের আদেশে ‘বিদ্যাসুন্দর কাব্য’ রচনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মুসলমান শাসকদের অবদানের বিবরণ শেরশাহের একটি কামানে এবং বারো ভূঁইয়াদের প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁ উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিতভাবে প্রমাণিত।
বাংলা ভাষার বিকাশ ও পরিচর্যায় মুসলমান সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষণের ইতিহাস এখনো সামগ্রিকভাবে অনাবিষ্কৃত। আবিষ্কৃত অংশের আলোচনা-পর্যালোচনাও সমকালীন সাহিত্যে উপেক্ষিত। এ উপেক্ষার অন্ধকার থেকে উন্মুক্ত আলোর দিগন্ত-অভিমুখে দৃপ্ত পদক্ষেপ সময়ের প্রয়োজন।
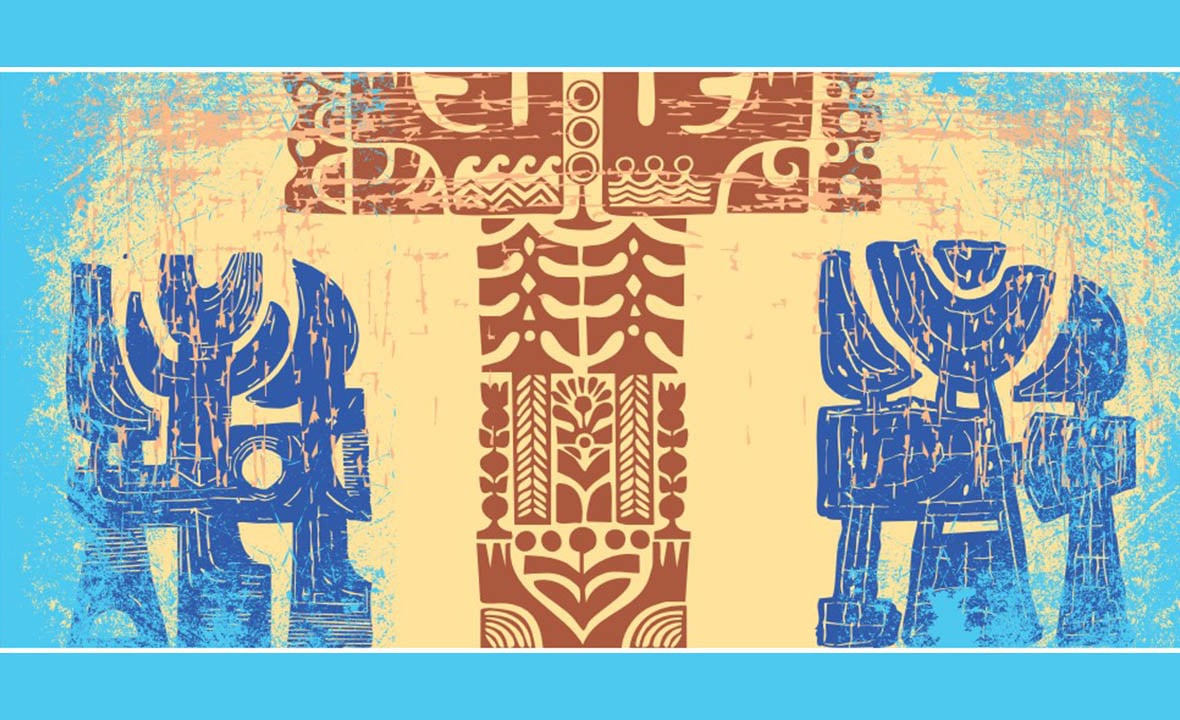
‘বাংলা ভাষার সৌভাগ্য যে, উদ্ভব-মুহূর্তে এক উদার রাজশক্তির সাহচর্য লাভ করেছে। যার ফলে তার পূর্ণ বিকাশ কেবল ত্বরান্বিত হয়নি, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্যে সঞ্জীবিত ও নবশক্তির সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পেরেছে।’—ড. ওয়াকিল আহমদের এ মতের যথার্থ নজির বাংলা সাহিত্যের অনোন্মোচিত যুগের পাতায় পাতায়, ভাষা-ইতিহাসের পরতে পরতে। সে উদার রাজশক্তির ঔদার্যচিহ্ন অনুসন্ধানের আগে অনুধাবন প্রয়োজন শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের সিদ্ধান্ত—‘বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।’ এ দাবির আরো সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন ড. এসএম লুৎফর রহমান—‘কেবল বাংলায় নয়, গোটা উপমহাদেশে ৫৪৪টি (মতান্তরে আরো বেশি) ভাষা উপভাষার মধ্যে প্রায় সৃষ্টি ভাষা মুছলিম শাসন কায়েমের পরে মুছলমানরাই সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষা তার একটি মাত্র।’
বাংলা ভাষার উদ্ভবকালে বাংলার শাসনক্ষমতায় ছিল পাল রাজবংশ—ধর্মে বৌদ্ধ, নীতিতে উদারপন্থি। বাংলা ভাষার জন্ম এবং বাংলা সাহিত্যের আদি লিখিত নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয়েছিল এ সময়ে।
প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করা পাল রাজবংশকে পরাজিত করে বাংলার ক্ষমতা দখলে নেয় দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন রাজবংশ। ধর্মে তারা হিন্দু, সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ। বাংলার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যবাদের গজিয়ে ওঠা সেনদের মাধ্যমে, সে সময়ে। ক্ষমতা দখলের পর সেন রাজবংশ বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অতিকায় আগ্রাসী হয়ে ওঠে। জাতিগত নিধন চালায় বৌদ্ধদের ওপর। নিধনযজ্ঞ শুধু মানুষ হত্যায় সীমিত ছিল না, সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-ধর্ম সমূলে নির্মূলের নৃশংসতা ছিল সেনদের স্বাভাবিক তৎপরতা। ওয়াকিল আহমদ জানান, ‘বাঙ্গালী বৌদ্ধ নিধন-পর্ব কেবল সমাপ্ত হল না, তাদের কৃষ্টিকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলল। বৌদ্ধরা সেদিন নেপালে পালিয়ে গিয়ে এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ হতে চর্যাপদের অবলুপ্তি রোধ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যরোষে কত বাংলা-বৌদ্ধ গ্রন্থের সেদিন মৃত্যু-সমাধি রচিত হয়েছিল, আজ তার কে হিসাব দেবে?’
সেন রাজবংশের চতুর্থ রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন কবি। সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি-পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল তার রাজসভায়। জয়দেব, উমাপতি ধর, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন তাদের মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্মণ সেন এবং তার রাজসভার কবিকুল ছিলেন ‘বাংলাদেশি’, ‘বাংলাভাষী’। কিন্তু বাংলা ভাষার কবি ছিলেন না। সাহিত্যচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত। মূলত সংস্কৃত মুখের ভাষা হতে অসমর্থ এক ভাষার নাম।
বাংলা ভাষা সেন রাজাদের নির্মূলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার কারণ তাদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা। তারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। বাংলা মানুষের মুখের ভাষা হলেও তাদের চর্চার ভাষা ছিল না। দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন তার কারণ—“ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী ‘দূর দূর’ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন, বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল—তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।”
সেনদের বাংলা বিদ্বেষ বিষয়ে তিনি আশঙ্কা করেন—‘দেবভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতগণের বাংলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোনো কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না।”
ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জীবনের জন্য এক উদার রাজদৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষক সাহচর্য প্রত্যাশিত ছিল, যাতে উন্মুখ জনসাধারণ দুর্বোধ্য সংস্কৃতের দাসত্ব ছিন্ন করে প্রাণের ভাষার মুক্ত চর্চা করতে পারে। বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা না ঘটলে বাংলা ভাষা হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়নে নির্জীব এমনকি নির্ভুল হতে পারত। আরো অগ্রসর অভিমত ব্যক্ত করেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান—‘মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। এটা বাংলাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি উৎসাহিত হয়। যদি বাংলায় মুসলিম-বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ প্রদেশে আর কয়েক শতকের জন্যে হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকত, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।’ মুসলমান সুলতানদের ঔদার্যই প্রাণহীন বাংলা ভাষা প্রাণবন্ত করেছে। রাজানুকূল্য বাংলা সাহিত্যে করেছে ফুলে-ফলে-পত্রপল্লবে বিকশিত।
১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন। বাংলার ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রকৃত সমৃদ্ধির সূচনা হয়। তার পরের শতাব্দীকালজুড়ে মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার ও স্থিতি স্থাপনের সংগ্রাম চলে। সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে মুসলিম রাজশক্তি বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে তৎপর হন।
মুসলিম শাসকদের ভাষা ছিল তুর্কি, রাজভাষা ফারসি। তৎকালীন বিশ্বসভ্যতায় দুটো ভাষাই সাহিত্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। তবু মুসলমান সুলতান ও আমির-মালিকগণ জনসাধারণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এর কারণ ইসলামের উদারতা, উচ্চ মূল্যবোধ, বৈষম্যহীন আদর্শ এবং উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি সুলতানদের অত্যাগ্রহ।
ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব-ইরান-তুরান থেকে আগত সুফি-দরবেশ ও উলামাসমাজ উপলব্ধি করলেন, বাংলার জনসাধারণ আরবি, ফারসি ও তুর্কির সঙ্গে অপরিচিত। সুতরাং সাধারণের ভাষা বাংলায় ধর্ম-সমাজ বিষয়ক বইপুস্তক লেখা তারা কর্তব্য মনে করেন। বাংলার অধিবাসীদের স্থানীয় ভাষায় মানবীয় শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনবোধ করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলা ভাষা এক নবজীবন লাভ করে, জনসাধারণ ও রাজদরবারের মাঝে সৌভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধসেতু স্থাপন করে।
মুসলমান শাসকবর্গ বাংলাদেশেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। বাংলাদেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন, এ মাটির সন্তান হিসেবে নিজেদের পরিচয় ধারণ করেন। এ দেশের আদি অধিবাসীদের মতো বাংলা তাদেরও ভাষা হিসেবে আদরিত হয়।
মুসলিম শাসনামলে বিপুল উন্নতি সাধিত হয় হিন্দু সমাজের। হিন্দুদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে নিম্নশ্রেণির হিন্দুরাও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, ধর্মীয় গ্রন্থপাঠের অধিকার পায়। অথচ মুসলিম-পূর্ব সেনযুগে শিক্ষাগ্রহণ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণ শ্রেণির দখলে ছিল। শিক্ষাদীক্ষা হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এমনকি, ধোপা-নাপিত শ্রেণির লোকেরাও সাহিত্যে ও জ্ঞানানুশীলনে খ্যাতিমান হয়। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনই এ কথা প্রথম উচ্চারণ করেন যে, মুসলমানেরা ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান থেকেই আসুন না কেন এদেশে এসে তারা সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে পড়েন। হিন্দুদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানার কৌতূহল দেখা যায়। তাই তারা সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে প্রেরণা দেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা কেবল প্রয়োজনবোধে প্রয়োগসিদ্ধ ছিল না, আস্বাদন-কাম্য অন্তরবাসনাও সক্রিয় ছিল। ড. সেন লেখেন, ‘পাঠান প্রাধান্যকালে (মুসলমান) বাদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্র অনেক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মৰ্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গালা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।’
অথচ ‘মুসলমান ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার কবিগণ কোন হিন্দু রাজার কাছ থেকে সহযোগিতা বা দাক্ষিণ্য পাননি।’—জানান ড. ওয়াকিল আহমদ। এমনকি সেনযুগের ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে এ অলীক ধর্মবাণী প্রচার করেছিলেন, ‘যারা অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে, তারা রৌরব নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।’
মুসলিম সুলতানগণ বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষারও মূল্যায়ন করেছেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করান। তার একটি দর্শন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সুলতানের নাম অনুসারে ‘দালাইল-ই-ফিরোজ শাহী’ কৃত হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের সংস্কৃতি অনুরাগ বিশ্ববিদিত। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ ছাড়াও তার পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। বহু সংস্কৃত পণ্ডিত গ্রন্থ প্রণয়ন ও কৃতিত্বের জন্য সম্রাট আকবর থেকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন লাভ করেন। সম্রাট শাহজাহান জাহাঙ্গীর এবং দারাশিকোও ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক।
মুসলমান শাসকদের জ্ঞানদীপ্ত পরিবেশ ও উদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হয়ে হিন্দু কবিগণ বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগের সুযোগ লাভ করেন। ফলে হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যসমূহ এর উজ্জ্বল প্রমাণ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর যে গ্রন্থটি রচনাকাল বিবেচনায় প্রাচীনতা দাবি করে তা ‘ইউসুফ-জুলেখা’। রচয়িতা মধ্যযুগের মুসলিম কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর। পবিত্র কোরআনের সুরা ইউসুফের কাহিনি অবলম্বনে এ কাহিনি কাবাব রচনায় কবি একজন ‘রাজেশ্বর’-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্য পেয়েছিলেন। কাব্যের বন্দনা অংশে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে মহান ‘রাজেশ্বর’ ছিলেন কবি ও কাব্যানুরাগী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ।
সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ ছিলেন ‘রামায়ণ’ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক। কৃত্তিবাস ছিলেন কবি যশপ্রার্থী। সুলতানের আদেশে তিনি সংস্কৃত থেকে ‘রামায়ণ’ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ ও ‘লক্ষ্মী চরিত্র’ রচনা করেন মালাধর বসু। তার কাব্যকৃতি সুলতানকে সন্তুষ্ট করে। তাই মালাধর বসুকে সুলতান ‘গুণরাজ খান’ উপাধিতে ভূষিত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘মনসা বিজয়’ কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন বিপ্রদাস। হোসেন শাহের সময়কালে আরেকজন শক্তিমান খুবই বিজয় গুপ্ত। তার কাব্য ‘পদ্মপুরাণ’ বা ‘মনসামঙ্গল’।
কবি যশোরাজ খান সুলতান হোসেন শাহের অধীনে রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শাহী আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রচনা করেন ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুলতানের আগ্রহ ও উন্নতিকল্পে পৃষ্ঠপোষকতায় কৃতজ্ঞ হয়ে সুলতানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীকর নন্দীর ‘মহাভারত’ কাব্য সুলতান নুসরত শাহের আমলে ছুটি খানের আদেশে রচিত হয়েছিল। কবি শ্রীধর যুবরাজ ফিরোজ শাহের আদেশে ‘বিদ্যাসুন্দর কাব্য’ রচনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মুসলমান শাসকদের অবদানের বিবরণ শেরশাহের একটি কামানে এবং বারো ভূঁইয়াদের প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁ উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিতভাবে প্রমাণিত।
বাংলা ভাষার বিকাশ ও পরিচর্যায় মুসলমান সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষণের ইতিহাস এখনো সামগ্রিকভাবে অনাবিষ্কৃত। আবিষ্কৃত অংশের আলোচনা-পর্যালোচনাও সমকালীন সাহিত্যে উপেক্ষিত। এ উপেক্ষার অন্ধকার থেকে উন্মুক্ত আলোর দিগন্ত-অভিমুখে দৃপ্ত পদক্ষেপ সময়ের প্রয়োজন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন বলেছেন, ছাত্রদল নেতা ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়েদ হোসাইন হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে—কেউ যেন আইনের ফাঁক দিয়ে কেউ বেরিয়ে না যায়।
২২ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী রিয়াদ হাসানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বোরকা ও পর্দাশীল নারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। এই মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।
১ ঘণ্টা আগে
সমাবেশে জোবায়েদের সহপাঠী সজল খান বলেন, “পুলিশ এখনো বর্ষার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। শুধু বর্ষা ও মাহির নয়, এই ঘটনায় বর্ষার পরিবারও জড়িত। গতকাল আদালতে আমাদের সঙ্গে পুলিশের আচরণ ছিল অমানবিক। আমাদের এক বান্ধবী ভিডিও করতে গেলে তার ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। আমরা পুলিশের এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই।”
১ ঘণ্টা আগে
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ আইনের মামলায় বুয়েটের ২১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত রায়কে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে জামিনের বিষয়ে অধিকতর শুনানির জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন বিচার
২ ঘণ্টা আগে