এই নিবন্ধটি আমার পূর্ববর্তী লেখা ‘এনবিআরে কঠিন সিদ্ধান্তের সময়’ (আমার দেশ, ১ জুন ২০২৫)-এর ধারাবাহিকতা। প্রায় দুই দশক আগে প্রেষণে সরকারি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, সেটিই এখানে তুলে ধরছি।
আমি পাকিস্তান ও ভারতের শুধু সিম ও মোবাইল-সংক্রান্ত করনীতি পর্যালোচনা করেছিলাম। তাদের অনেকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার ও করনীতির মধ্যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে তখনো আমরা আমদানিনির্ভর একটি কাঠামোর মধ্যে বন্দি ছিলাম। এই বাস্তবতা আমাকে ভাবতে বাধ্য করে ‘আমরা কেন পিছিয়ে?’
২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে মোবাইল ফোন ব্যবহার রীতিমতো সামাজিক বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল। মানুষ তখন প্রথমবারের মতো ‘সবার হাতে মোবাইল’ যুগে প্রবেশ করছিল। অথচ রাজস্ব আহরণের কাঠামো তখনো পুরোনো আমদানিনির্ভর পদ্ধতিতেই আটকে ছিল। সিম বিক্রির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, মোবাইল ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবু সরকারের রাজস্ব আয় তেমন বাড়ছে না। প্রশ্ন উঠল—সমস্যার মূল কোথায়?
ঢাকা বিমানবন্দরের ট্যাক্স ফাঁকির চিত্র
একজন অফিসারের প্রতিবেদনে পরিষ্কার হয়, ২০০৪ সালে একজন ব্যবসায়ী যদি বৈধপথে ব্যাংকক থেকে ১০০টি মোবাইল ফোন আনে, তাহলে শুধু ট্যাক্স বাবদ তাকে দিতে হতো ১০০×১৫০০ দেড় লাখ টাকা (ভ্রমণ খরচ বাদে) । তবে অসাধু ব্যবসায়ীরা ঢাকার বিমানবন্দরের পার্সোনাল লাগেজ হিসেবে প্রতি ট্রিপে অনায়াসে ব্রিফকেসে ১০০টি বাটন মোবাইল সেট রেখে নানা কৌশলে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে বিপুল পরিমাণ মোবাইল সেট দেশের বাজারে আনা হতো।
সে সময় ব্যবসায়ীদের যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ অন্তত ৫০ হাজার টাকা হলেও, ট্যাক্স ফাঁকির মাধ্যমে প্রতি ট্রিপে ন্যূনতম এক লাখ টাকার লাভ হতো। এর ফলে মোবাইল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিমানবন্দরে কর ফাঁকি দিয়ে মোবাইল আনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধরা পড়লেও বিদ্যমান বিধি অনুসারে শুধু আর্থিক জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হতো, যা ট্যাক্সের পুরো পরিমাণ ও প্রয়োজনে কাস্টমস কর্মকর্তার মর্জিমাফিক অতিরিক্ত টাকাসহ হতো।
পরিসংখ্যানই খুলে দিল চোখ
২০০৪-০৫ অর্থবছরে দেশে ২৪ লাখ নতুন সিম বিক্রি হয়েছে। অথচ সেই বছরে মাত্র ৬ লাখ ২৬ হাজার মোবাইল সেট বৈধভাবে আমদানি হয়েছে। সরকারের প্রাপ্ত রাজস্ব ছিল মাত্র ৯৪ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, প্রায় ১৮ লাখ মোবাইল সেট চোরাই পথে এসেছে বলে অনুমান করা হয়, যার ফলে আনুমানিক ২৬০ কোটি টাকার রাজস্ব হাতছাড়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—পুরোনো ট্যাক্স কাঠামো অকেজো, অব্যবহারযোগ্য। যদি সরকার আমদানিপর্যায়ে উচ্চ শুল্ক আরোপের পরিবর্তে ব্যবহারভিত্তিক কর ব্যবস্থায় যায়, তবে তা রাজস্ব বাড়াবে এবং চোরাচালান ঠেকাবে।
যে ব্যবহার করে, সে ট্যাক্স দেবে : নতুন নীতির ভিত্তিপ্রস্তর
প্রতিকারের নিমিত্তে প্রথমে একটি ছোট পদক্ষেপ নেওয়া হয়—ঢাকা বিমানবন্দরে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখগুলোর বদলে অপরিচিত ও নিরপেক্ষ ফিল্ড স্টাফদের পোস্টিং দিয়ে তদবির ও প্রভাব খাটানোর প্রবণতা বন্ধের চেষ্টা করা হয়। এতে কিছুদিনের জন্য ফাঁকি কিছুটা কমে এলেও, পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি। চতুর ব্যবসায়ীরা দ্রুতই নতুন পথ বেছে নেয়—ঢাকা বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর ব্যবহার শুরু করে। বিষয়টি তখন আরো পরিষ্কার হয়ে যায়—কৌশলগত পরিবর্তন বা লোক বদল করে এই সংঘবদ্ধ চোরাচালান চক্রকে থামানো যাবে না; প্রয়োজন একটি মৌলিক নীতিগত সংস্কার।
এ পর্যায়ে মোবাইল সেটের ওপর আরোপিত শুল্ক ১৫০০ থেকে কমিয়ে ৫০০ টাকা করার একটি প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় আসে, যাতে বৈধ আমদানিকারকদের জন্য বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক হয় এবং চোরাচালান নিরুৎসাহিত হয়। কিন্তু তখনকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান খায়রুজ্জামান চৌধুরী এই প্রস্তাবে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন এবং উল্টো পরামর্শ দেন—যেহেতু রাজস্ব কমবে, তাই বাজেট লক্ষ্যমাত্রাও ৩২ হাজার কোটি থেকে কমিয়ে ২৮ হাজার কোটি করা হোক। প্রেক্ষাপট ছিল ২০০৪-০৫ অর্থবছর, যখন জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫৭২৪৮ কোটি টাকা।
তবে আমি তখন থেমে যাওয়ার পাত্র ছিলাম না। বারবার ফাঁকি রোধে ব্যর্থ হয়ে এবার ভাবতে শুরু করলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একপর্যায়ে এনবিআরকে একটি বিকল্প ও বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাব দিই : মোবাইল হ্যান্ডসেটের আমদানি শুল্ক ১৫০০ টাকা থেকে কমিয়ে মাত্র ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হোক। পাশাপাশি, সেই ট্যাক্সটি প্রতিস্থাপন করা হোক নতুন সিম সংযোগের ওপর ১২০০ টাকা করে ব্যবহারভিত্তিক কর আরোপের মাধ্যমে। (উল্লেখ্য, আগের বছর মোবাইল সেটের জন্য কর ছিল ৪৫০০ টাকা)। কারণ, যত মোবাইল ফোনই বৈধ বা অবৈধভাবে দেশে আসুক, ব্যবহার করার জন্য সিম তো লাগবেই। ফলে, মোবাইল সেট চোরাচালানের আর কোনো সুবিধা থাকছে না, বরং কর ফাঁকি রোধ হবে এবং সরকার রাজস্ব হারানোর বদলে আরো বেশি রাজস্ব পাবে।
ওপরে বর্ণিত পরিসংখ্যানটি উপস্থাপনের পর এনবিআর চেয়ারম্যান প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝে প্রাথমিকভাবে সম্মতি দেন এবং বিষয়টি গোপনে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়। এভাবেই জন্ম নেয় একটি ব্যবহারভিত্তিক রাজস্বনীতির—‘যে ব্যবহার করে, সে ট্যাক্স দেবে’, যার মাধ্যমে সরকার পরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হয় এবং চোরাচালানির মাধ্যমে মোবাইল হ্যান্ডসেট অলাভজনক হয়ে যায়।
সমালোচনার মুখে যুক্তির দৃঢ়তা
২০০৫-২০০৬ সালের বাজেটে যখন নতুন সিমে ১২০০ টাকা করে কর আরোপ করা হয়, তখন মোবাইল অপারেটররা এবং কয়েকটি সংবাদমাধ্যম সরকারের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়। গ্রামীণফোনসহ অন্য অপারেটররা নারী ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বলে প্রচার শুরু করে। সমালোচনার কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও শীর্ষপর্যায়ে সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন। যুক্তি দিয়ে বোঝানো হলোÑ‘হ্যান্ডসেটের ওপর ট্যাক্স ৩০০ টাকা করা হয়েছে, বাকি ১২০০ টাকা শুধু সিমে স্থানান্তর হয়েছে।’ রাজস্ব হারানো বন্ধ করাই মূল লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত এনবিআরের সমর্থন এবং অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে সিম কর ১২০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৯০০ টাকা নির্ধারণ করে অর্থ বিল পাস হয়। এই সিদ্ধান্ত মোবাইল অপারেটরদের অনেক গোপন তথ্যও সামনে আনতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে তারা যে আমদানি করা হ্যান্ডসেটের ওপর সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছিল না, সে সত্য এই সুযোগে প্রকাশ্যে আসে।
৭ বছরে রাজস্বে ৮ হাজার কোটি টাকার সাফল্য ও একটি ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা
২০০৪ সালে দেশে মোবাইল সিম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ লাখ। ২০০৫ সালে এটি বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটিতে, ২০০৬ সালে ১ কোটি ৯১ লাখে এবং ২০১২ সালের মধ্যে তা লাফিয়ে পৌঁছে যায় ১০ কোটি ৬০ লাখে। এ সময় নেওয়া একটি সুনির্দিষ্ট নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিটি সিম থেকে গড়ে ৮০০ টাকা করে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়। ফলে, ২০১২ সাল পর্যন্ত মাত্র সাত বছরে সরকার অর্জন করে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা, যা শুধু হ্যান্ডসেট আমদানির ওপর ট্যাক্স রেখে কখনোই সম্ভব হতো না। এই ছোট কিন্তু দূরদর্শী সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন মোবাইল আমদানিকে সহজ করেছে, তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি টেকসই ভিত্তিও তৈরি করেছে।
২০২৪ সালের ২৪ জুন জাতীয় সংসদে জানানো হয়, দেশে নিবন্ধিত সিমের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩ কোটি ২৭ লাখ ৫৬ হাজার ৯৭০টি, যদিও এর মধ্যে অনেক নিষ্ক্রিয় সিমও রয়েছে। তবু এ পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে সময়োপযোগী ওই নীতির প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল—সরকারি রাজস্ব আহরণের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় তার মধ্য দিয়ে—এটি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।
নীতিহীনতার খেসারত : মোবাইল লাইসেন্স থেকে হারানো ৭৬০০ কোটি টাকা
১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৯ কোটি টাকা করে চারটি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্স দেয় (সিটি সেল ছাড়া)। অথচ সেই একই সময় পাকিস্তান সরকার প্রতি থেকে ১৯০০ কোটি করে চারটি মোবাইল কোম্পানি থেকে আদায় করে প্রায় ৭৬০০ কোটি টাকা। যথাযথ উদ্যোগ, আন্তরিকতা ও তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ থাকলে বাংলাদেশও পাকিস্তানের মতো ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে পারত, যা ১৯৯৬-৯৭ সালের জাতীয় বাজেটের (২৪ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা) একটি বিশাল অংশ ছিল। পরে আমার একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং (২০০৪-০৫ সালে) জাতীয় সংসদে স্বীকার করেন, ‘শুধু অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও স্বার্থান্বেষীদের কারণে আমরা মোবাইল লাইসেন্স ফি থেকে বিপুল রাজস্ব হারিয়েছি।’ (২০০৫ সালের ৩০ জুন ‘প্রথম আলো’, ‘নয়া দিগন্ত’, ‘দ্য ডেইলি স্টার’সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়।) এটি শুধুই একটি উদাহরণ নয়, এটি প্রমাণ যে সঠিক পলিসি ও দেশাত্মবোধক জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্র কীভাবে আত্মঘাতী হতে পারে।
বর্তমান এনবিআর চেয়ারম্যান ও সাহসী সংস্কার
বর্তমানে এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান একটি সাহসী ও ফলপ্রসূ সংস্কার-প্রয়াসে লিপ্ত। তিনি অটোমেশন, মানবসম্পদ পুনর্বিন্যাস ও দ্বৈত কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে এনবিআরকে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চাচ্ছেন, যা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) পরামর্শ ও সরকারের নীতিগত অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালে ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ’ জারি করা হয়, যার মাধ্যমে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পৃথক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও পরামর্শক কমিটি, দুই ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে অধ্যাদেশটি তৈরি হয়েছে, কিছু স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তা তা বাতিলের দাবিতে ‘পেন ডাউন’ কর্মসূচি চালিয়ে পুরো রাজস্ব ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করছে। অথচ সরকার ইতোমধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার ঘোষণা দিয়েছে এবং এনবিআরকে স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী বিভাগে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজস্ব নীতি ও প্রশাসন পৃথককরণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের ব্যবস্থাগত জটিলতা দূর করে রাজস্ব আহরণকে আরো কার্যকর ও দক্ষ করে তোলাই এর উদ্দেশ্য।
প্রতিরোধ নয়, সদর্থক সংলাপ প্রয়োজন
কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এনবিআরের ভেতরের একটি সংগঠিত গোষ্ঠী ততপর।
এনবিআর কর্মকর্তাদের উচিত হবে দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের জায়গা থেকে রাজস্ব সংস্কার বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপে অংশ নেওয়া। তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও যৌক্তিক আপত্তিকে মূল্য দেওয়া হবে—তবে সেটি হতে হবে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায়।
২০০৫ সালে সিমভিত্তিক করনীতির সাহসী সিদ্ধান্তের মতোই আজকের সংস্কার চেষ্টাও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে, যদি রাষ্ট্র তার সংস্কারপন্থি নেতৃত্বকে সহায়তা করে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ না করে। ৮ হাজার কোটি টাকার সাফল্যের সেই দূরদর্শী চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক—‘যে ব্যবহার করে, সে ট্যাক্স দেবে’ এই ধারণার সঙ্গে বর্তমান আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে যদি যোগ হয় স্বচ্ছতা, মানবসম্পদ পুনর্বিন্যাস ও দ্বৈত কাঠামো সংস্কার এবং অটোমেশন, তবে রাজস্ব আহরণে বাংলাদেশ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে। এখনই সিদ্ধান্তের সময়—রাষ্ট্র কি সেই দূরদর্শিতাকে স্বীকৃতি দেবে, নাকি অদূরদর্শিতা দাপটে আবার একটি যুগান্তকারী সংস্কার মুখ থুবড়ে পড়বে?
লেখক : সাবেক সহকারী নৌবাহিনী প্রধান ও উপ-উপাচার্য বিইউপি
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


 গবেষণায় বাংলাদেশ পিছিয়ে কেন?
গবেষণায় বাংলাদেশ পিছিয়ে কেন?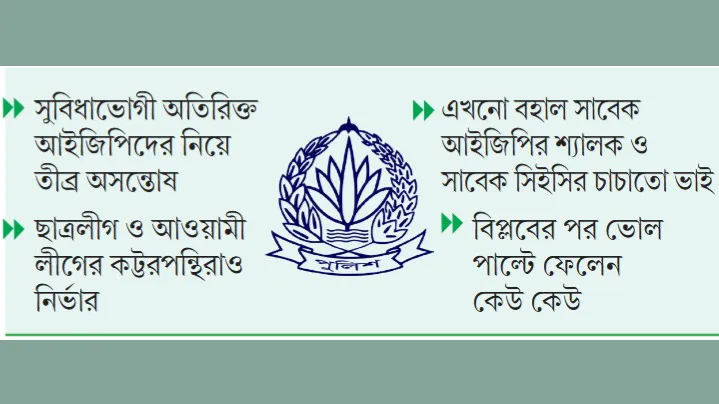 পুলিশ প্রশাসনে এখনো দাপট মাফিয়া মনিরুলের
পুলিশ প্রশাসনে এখনো দাপট মাফিয়া মনিরুলের