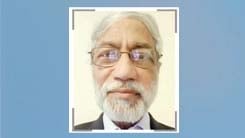বেশ কবছর আগের কথা। আমেরিকার টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তিউনিসিয়ার ‘ইউনিভার্সিটি অব টিউনিসÑএল মানারের’ এক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই সুযোগে দুই সপ্তাহের জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে।
সুদূর উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের পাড়ে, লিবিয়া আর আলজেরিয়ার মাঝখানে এক কোটি লোকের ছোট্ট দেশ তিউনিসিয়া। সে দেশের একটি বড় অংশ সাহারা মরুভূমি এমনিতেই গ্রাস করে ফেলেছে। তার ওপর মরুভূমির বালুর চাদর আগ্রাসী আক্রোশে ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে তিউনিসিয়ার অবশিষ্ট সবুজ জমিনের দিকে।
এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও তিউনিসিয়ার সংগ্রামী মানুষ টিকে আছে যুগ যুগ ধরে। তবু সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জেসমিন বিপ্লবের আগে, বাংলাদেশের অনেক লোক এ দেশটির নামও জানত না। সুন্দর এই দেশটির কথা আমি প্রথম শুনেছি মাত্র ১৯৭০ সালে, যখন তৎকালীন জর্ডানের বাদশাহ হোসেন বিন তালাল পিএলও এবং ইয়াসির আরাফাতকে তার দলবলসহ জর্ডান থেকে বের করে দেন তখন। ওই সময় তিউনিসিয়া সরকার ইয়াসির আরাফাত ও তার অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ সরকারকে আশ্রয় দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সুনাম অর্জন করেছিল।
ন্যাসভিল থেকে শিকাগো এবং প্যারিস হয়ে আমি যখন তিউনিস গিয়ে পৌঁছালাম, তখন দুপুর গড়িয়ে সূর্য পশ্চিম আকাশে মাত্র একটুখানি হেলেছে। কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনের কাজ সেরে আধা ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে এলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম অ্যারাইভাল এরিয়ায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন পেশাগত বন্ধু ও তিউনিসে আমার হোস্ট শিহেব বোডউইন। টার্মিনাল থেকে নেমেই অনুভব করলাম ভরদুপুরে মরুভূমি দেশের লু হাওয়ার উত্তাপ।
গাড়িতে ওঠার পরই শিহেব বললেন, ‘সন্ধ্যা নামতে এখনো অনেক দেরি, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে চলো হোটেলে যাওয়ার আগে তোমাকে এক চক্কর তিউনিস শহর ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে যাই।’ আমি তার প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়ে গেলাম। দেখলাম এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে শহরে যাওয়ার পথটা খুবই সুন্দর। সাজানো-গোছানো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঝকঝকে-তকতকে। দুদিকে রাস্তা। মাঝখানে সবুজ আইল্যান্ড। হরেক রকমের রঙিন ফুল আর নানা জাতের বাহারি গাছগাছালি দিয়ে খুব রুচিসম্মতভাবে সাজানো।
শিহেব গাড়ি চালাচ্ছেন, শহর ঘুরেফিরে দেখাচ্ছেন আর কমেন্টারি দিচ্ছেন। এর মধ্যে একসময় সাগরতীরেও নিয়ে গেলেন। ভূমধ্যসাগরের দিকে চোখ তুলে বললেন, ‘তিউনিসিয়ার সমুদ্রসৈকতের সঙ্গে ইতালির সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের ন্যূনতম দূরত্ব মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল। দুঃসাহসী তিউনিসিয়ানরা সাধারণ নৌকায় চড়ে ওই পথে ইতালি চলে যান।’
তার আগে এক জায়গায় নিয়ে তিনি আমাকে একটি তিন-চারতলা বড় বিল্ডিং দেখিয়ে বললেন, ‘উনিশ শ সত্তর সালে যখন পিএলওর লটবহর নিয়ে চেয়ারম্যান আরাফাত এ দেশে এসে আশ্রয় নেন, এটাই ছিল তার হেডকোয়ার্টার। কথা প্রসঙ্গে একসময় তিনি গৌরবের সঙ্গে বললেন, তারা মহান মনীষী ইবনে খালদুনের উত্তরসূরি। এর আগে আমি জানতাম না, ইবনে খালদুনের মতো মহান পুরুষের জন্ম হয়েছিল তিউনিসিয়ায়। ওইবার তিউনিস থেকে ফিরে এসে ইবনে খালদুনের ওপর আমার বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিছু লেখাপড়া করি তার ওপর। এখনো পড়ছি। ইবনে খালদুন বোঝার চেষ্টা করছি। যতই পড়ছি, ততই বুঝতে পারছি ইবনে খালদুন কত বড়মাপের ইতিহাসবিদ এবং কত বড় সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন।
শিহেবের সঙ্গে গাড়িতে করে তিউনিস ঘুরতে ঘুরতে দেশটি সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা দারুণ ইতিবাচক ধারণা জন্মাল। যদিও আমি অর্থনীতির ছাত্র, তবু আমার জানা ছিল না আফ্রিকার কোনো দেশ এত সুন্দর, এত উন্নত হতে পারে। বন্ধু শিহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমরা এত অল্প সময়ে এত এগিয়ে গেলে কেমন করে?’ শিহেব জানালেন, সম্ভবত দুই কারণে।
প্রথমত, দুই যুগ ধরে তাদের সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা এবং মানবসম্পদের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। দ্বিতীয়ত, তাদের ‘জিওগ্রাফিক প্রোক্সিমিটি টু ইউরোপও একটি ফ্যাক্টর’। অর্থাৎ, ইউরোপের সঙ্গে তিউনিসিয়ার ভৌগোলিক নৈকট্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো বললেন, সকালবেলা প্ল্যান করে তারা দুপুরে প্যারিস পৌঁছে যান এবং কাজ সেরে রাতে ফিরেও আসতে পারেন। ইউরোপের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাদের জনগণের মধ্যে একটি আস্থা এবং প্রতীতির জন্ম দিয়েছে, ‘ইউরোপ যদি পারে তো এত কাছে থেকে আমরা পারব না কেন’?
বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না, শিহেব আমাকে যে পথে নিয়ে ঘুরছেন, সেটা ‘নিউ তিউনিস’ অর্থাৎ তিউনিসের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এবং নতুন অঞ্চল। নিশ্চয়ই তিউনিসেও ময়লা, দুর্গন্ধ, ঘিঞ্জিময় পুরোনো এরিয়াও আছে, আছে গরিবদের থাকার জায়গা, বস্তিতুল্য অঞ্চল। বোধগম্য কারণেই প্রথম দিন তিনি আমাকে সে পথে নিয়ে যাচ্ছেন না।
ঘোরাঘুরি করে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, তখন শিহেব এক দোকান থেকে আমাকে কিছু বোতলের পানি, মিষ্টি ফল আর শুকনো খাবার কিনে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন, ‘তুমি একটুক্ষণ রেস্ট নিয়ে, শাওয়ার সেরে ইচ্ছে করলে এখানেই এসব রেস্টুরেন্টে এসে ডিনার খেতে পারো।’ আমি শাওয়ার নিলাম ঠিকই, কিন্তু বেরোতে ইচ্ছে হলো না, সফর ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে আসছিল।
একটি কলা, কয়েক টুকরো বিস্কুট এবং তিন-চার ঢোক বোতলের পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাধারণত বিছানা বদলে আমার ঘুমের সমস্যা হয়, কিন্তু সে রাতে তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে এক ঘুমে ভোরবেলা উঠলাম। সকালে বেসমেন্টে নাশতা খেয়ে হোটেলের সামনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, উত্তর আফ্রিকায় প্রথম এসেছি দেশটি কেমন, তার মানুষজন কেমন একটু দেখি। হোটেলটি যে সড়কের ওপর, সেটা অনেকটা ঢাকার মিরপুর রোডের মতো। চওড়া রাস্তা। যান চলাচলেও বেশ ব্যস্ত।
রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম। কয়েকটি জিনিস আমার চোখে ধরা পড়ল। প্রথমত, ছোট-বড় বাড়ি, বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং সর্বত্র বিল্ডিংয়ের ছাদে, ঘরের দেয়ালে টিভির ডিশ অ্যান্টেনা। বুঝলাম, সবাই স্যাটেলাইট টিভি দেখে। উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ছাদে, বারান্দায় ও বেলকনিতে লোকজন রঙ-বেরঙের ভেজা কাপড় মেলে দিয়েছে। বুঝলাম, এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি মিল আছে। আরেকটা বিষয় আমার নজর কাড়ল।
সেটা হলো রাস্তায় রিকশা বা ওই জাতীয় কোনো স্লো মুভিং যানবাহন নেই। সবাই গাড়িতে চলছে। আরো ভালো করে খেয়াল করে যা দেখলাম তাতে অবাক এবং অভিভূত না হয়ে পারলাম না। গুনে দেখলাম প্রতি ১০টি গাড়ির মধ্যে ছয়টির স্টিয়ারিং হুইল ধরে যিনি বসে আছেন, তিনি একজন নারী। অর্থাৎ তিউনিসিয়ার মহিলা সমাজ খুব অগ্রসরমাণ।
তারা রান্নাঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ নন। ঘরের বাইরেও তাদের আরেকটি জগৎ আছে, যেখানে তারা কাজ করেন। তারা বেশ ফরওয়ার্ড লুকিং। আউট গোয়িং প্রকৃতির। চেহারা-সুরতে, চলনে-বলনে এবং বেশ-ভূষায় তিউনিসীয় রমণীরা একেবারে ইউরোপীয়দের মতো। আধুনিক ভাষায় যাকে বলে স্মার্ট।
কতক্ষণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার পর হোটেলের উল্টোদিকে কিছুদূর হাঁটলাম। ওদিকে দেখলাম একটি বিশাল আবাসিক এলাকা। সবই বড় ও মাঝারি সাইজের পাকা দালানবাড়ি। সবকটি বাড়িই দেয়ালঘেরা। ভেতরে বাড়ির সামনে আছে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান। দেখে মনে পড়ল ষাটের দশকের ধানমন্ডির কথা। ওই সময় ঢাকার ধানমন্ডি এ রকমই সুন্দর ছিল। একেবারে ছবির মতো। আবাসিক এলাকায় লোক চলাচল তেমন নেই।
নেই ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক ও ফকির-মিসকিনদের আহাজারি। মাঝে মাঝে দেখলাম বাড়ির সামনে বাগানে লোকজন ফুলগাছের পরিচর্যা করছে। দু-তিন রাস্তা পরপর ইন্টারসেকশনের কোনায় ছোট ছোট দোকান। এসব দোকানে চাল, ডাল, ডিম, রুটি, তেল, পানি, তরিতরকারি, ফলমূল, কুকি-বিস্কুট, চকলেট, ললিপপ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারলাম রোদের তেজ বাড়ছে আর বেশি সময় বাইরে থাকা যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলাম।
দুপুরের দিকে শিহেব এলেন। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে গেলেন। একটি ক্লাসে গেলাম। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাদের কথাবার্তার ধরন-ধারণ ও চিন্তাভাবনার কথা জেনে অবাক হলাম। তারা খুব চটপটে। আধুনিক। আমেরিকার প্রতি তাদের কৌতূহলের সীমা নেই। তবে তারা একেবারেই অন্ধ আমেরিকা অনুসারী নয়। কথাবার্তায় পরিশীলিত। কাপড়চোপড়ে ভদ্র ও শালীন।
তারা চারটি ভাষায় কথা বলতে জানে। আরবি, ফরাসি, ইংরেজি এবং এই তিন ভাষার মিশ্রণে চতুর্থ আরেকটি ভাষা যার কোনো নাম নেই। বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে চারটি নয়, তিনটি নয়, মাত্র দুটি ভাষা শেখানো হয়, তাও কিছু শহুরে স্কুল ছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি তো জানেই না, বাংলাটাও ঠিকমতো রপ্ত করতে পারে না। সব মিলে উত্তর আফ্রিকার একটি ছোট্ট দেশ তিউনিসিয়ার সঙ্গে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের তুলনা করে হতাশ হলাম, মনে বড় কষ্ট পেলাম। ভাবলাম, আমার সোনার বাংলাদেশ কখন এমন হবে?
লেখক : অধ্যাপক, টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি; ম্যানেজিং এডিটর জার্নাল অব ডেভেলপিং এরিয়াজ
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন