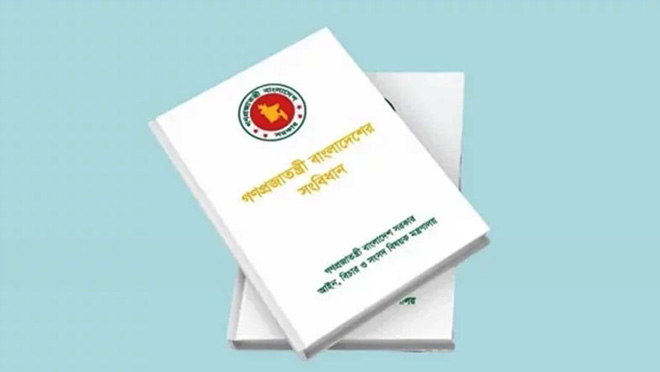সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, যা দেশের শাসনব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করে। এটি নাগরিকদের অধিকার, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এবং সরকারের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। সংবিধান রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূল দলিল, যা নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জঁ-জাক রুসোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (The Social Contract, 1762) অনুযায়ী, রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য গঠিত এবং তাদের সম্মতিতেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান কেবল শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশিকা নয়, এটি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। আমেরিকার দার্শনিক জন ডিওয়ি (John Dewey) বলেছেন, ‘Democracy begins in conversation.’ অর্থাৎ গণতন্ত্র তখনই সফল হয়, যখন জনগণের মত প্রকাশের সুযোগ থাকে। যেমন, মার্কিন সংবিধানের প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে, ‘We the People’ অর্থাৎ জনগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। এই ধারণা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। গণতন্ত্রের মূল চেতনা হলো জনগণের মতপ্রকাশ ও অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা।
বিখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিক আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন—‘Democracy is the government of the people, by the people, for the people.’ অর্থাৎ জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের জন্য কার্যকর এবং জনগণের ক্ষমতায়নই গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংবিধান হতে হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও সময়োপযোগী। যদি জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণ ছাড়া সংবিধানের সংশোধন বা সংস্কার করা হয়, তবে তা গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। জনগণের মতামত ছাড়া পরিবর্তিত সংবিধান সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গা হারিয়ে ফেলতে পারে। সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যদি জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিতে না পারে, তাহলে গণতন্ত্রের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। কিন্তু ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তা ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সংবিধানের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রচিত হয়েছিল। তবে বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫৪ বছরে এ সংবিধান ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সংশোধন সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়, যেখানে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধী মত ও নাগরিক সমাজের পরামর্শ উপেক্ষিত হয়েছে।
সংবিধান সংশোধন বা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করতে গেলে কিছু বিষয় সামনে চলে আসে। যথা বিশ্বে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসে, যা সংবিধানের সংশোধন ও সংস্কার জরুরি করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি রাষ্ট্রের দিকে তাকাতে পারি। যেমন নব্বইয়ের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি (অ্যাপার্টহেইড) অবসানের পর, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের সংবিধান সংস্কার করে একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করে, যা সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে। আবার ১৯৫৮ সালে ফ্রান্স পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণ করে, যা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনে।
সংবিধানকে জনগণের প্রত্যাশা ও আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর আইসল্যান্ডের জনগণ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি তোলে।
জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে একটি নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা হয়, যা আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর চাহিদা প্রতিফলিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের কিছু ধারা অপ্রাসঙ্গিক বা বিতর্কিত হতে পারে, যা সংস্কারের মাধ্যমে সমাধান করা যায়।
সংবিধান সংশোধনের বর্তমান পদ্ধতি কতটা গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া মূলত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত আছে। সংক্ষেপে এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রথমে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে একটি বিল আনা হয়। এরপর সংবিধানের সাধারণ ধারাগুলোর সংশোধনের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগে। অতঃপর সংসদে বিলটি পাস হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে এটি কার্যকর হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে শুধু সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংশোধন করতে পারেন, যেখানে সাধারণ জনগণের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই।
এ ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদই একমাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা। কিন্তু যখন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে, তখন তাদের ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থাকে। ফলে বিরোধী দলের মতামত উপেক্ষিত হয়, ক্ষমতাসীন দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করতে পারে এবং একদলীয় নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি তৈরি হয়, যা গণতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট করে।
কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হওয়া উচিত। বর্তমান পদ্ধতিতে জনগণের কোনো গণভোট (Referendum) দেওয়ার সুযোগ নেই, কোনো জাতীয় সংলাপ বা মতামত নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই এবং সংবিধান সংশোধনের সময় সাধারণ নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের কোনো সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে জনগণ নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে না, যা গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী।
সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা যদি শুধু সংসদের হাতে থাকে, তাহলে তা হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের আশঙ্কা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ সংবিধানের বিগত সংশোধনীগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারব, যেমন দলীয় স্বার্থে নির্বাচনি পদ্ধতি পরিবর্তন করা। অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সালে সাধারণ নির্বাচন হয় এবং ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৭ বছর পর দেশে আবার সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
এরপর ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। কিন্তু ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। এ ধরনের পরিবর্তন গণতন্ত্রের বিকাশের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত করার শঙ্কা তৈরি করতে পারে।
এ ছাড়া বিদ্যমান সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ায় আইনি জটিলতা রয়েছে। অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ায় কোনো ভুল বা বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা আদালতে গড়ায়। বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধন নিয়ে একাধিক মামলা ও আইনি বিতর্ক দেখা গেছে, যেমন পঞ্চম সংশোধনীতে (১৯৭৯) সামরিক শাসনের মাধ্যমে আসা কিছু বিধান সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছিল, যা পরে আদালত অবৈধ ঘোষণা করে।
এরপর ত্রয়োদশ সংশোধনীতে (১৯৯৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। ষোড়শ সংশোধনীতে (২০১৪) বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা পরে আদালত বাতিল করে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে, শুধু সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করা হলে তা দীর্ঘ মেয়াদে সংকট তৈরি করে।
সংবিধান সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। এই প্রেক্ষাপটে গণপরিষদ নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে ওঠে, কারণ এটি সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ মতামত, বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে। গণপরিষদ নির্বাচন হলে জনগণের প্রতিনিধিরা সরাসরি সংবিধান সংশোধনের কাজে যুক্ত হতে পারেন।
এটি সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের মতামত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। আইসল্যান্ডে ২০০৮ সালে সংবিধান সংস্কারের জন্য ২৫ নাগরিকের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ (Constitutional Council) গঠন করে, যেখানে সাধারণ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার করা হয়। আবার ১৯৪৬ ও ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সে সংবিধান সংস্কারের জন্য দুটি পৃথক গণপরিষদ গঠন করা হয়েছিল। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মতামতের ভিত্তিতে নতুন সংবিধান রচিত হয়।
গণপরিষদ নির্বাচন হলে সংসদীয় রাজনীতির বাইরে থাকা বিভিন্ন অংশীজন (stakeholder) যেমন নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারবে। ফলে নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সম্ভব হয়।
উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণপরিষদ গঠন করা হয়, যেখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হয়। ২০১৫ সালে নেপালে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ফলে তাদের নতুন সংবিধান অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে।
গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কারের সিদ্ধান্তের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এতে একক দলের পরিবর্তে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন বা সংস্কার হয়। ফলে সংবিধান সংশোধনে রাজনৈতিক পক্ষপাত কমে এবং সংবিধান দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হয়। সংবিধান সংস্কারে গণপরিষদ নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়।
যেমন গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন থাকা অপরিহার্য। গণপরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা অপরিহার্য। গণপরিষদ নির্বাচনের পর জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য গণভোট বা গণশুনানি করা যেতে পারে। এটি সংবিধানের বৈধতা বাড়ায় এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
সর্বোপরি গণতন্ত্রের বিকাশ ও গণমানুষের অংশগ্রহণ, জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে গণতন্ত্রের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদে গণপরিষদ নির্বাচন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
লেখক : শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন