
ড. মো. মিজানুর রহমান
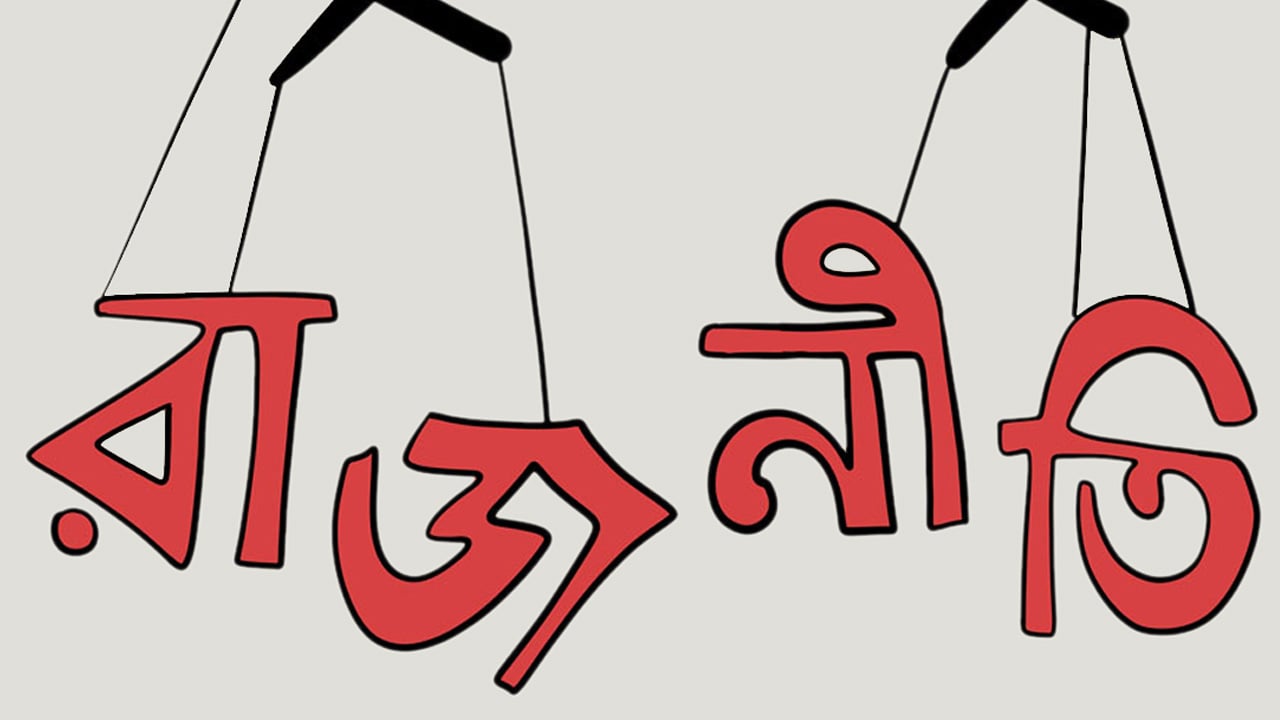
বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমন এক অববাহিকায় অবস্থিত, যার ওপর প্রভাব ফেলে প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে ভারতের নদী ব্যবস্থাপনা। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে হঠাৎ বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয়, বিশেষ করে ভারতের উজানে অপ্রত্যাশিতভাবে পানি ছেড়ে দেওয়ার কারণে। প্রশ্ন উঠেছে, ভারত কি বাংলাদেশকে না জানিয়ে পানি ছেড়ে দিয়েছে? আর যদি তা করে থাকে, তাহলে তা কি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয়? এবং এর মোকাবিলায় বাংলাদেশের করণীয়ই বা কী?
বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও, এখন সে পরিচিতি আর শুধু ঐতিহ্যের নয়, বরং আশঙ্কার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হঠাৎ করে যে প্রবল বন্যা দেখা দেয়, তা শুধু প্রাকৃতিক নয়—বরং এর পেছনে রয়েছে কূটনৈতিক গাফিলতি, আঞ্চলিক দায়িত্বহীনতা এবং দীর্ঘস্থায়ী পানি বণ্টন সমস্যার সুনিপুণ প্রতিচ্ছবি।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তা, ধরলা, করতোয়া এবং বরাক-কুশিয়ারা নদীর উজানে বিশেষ করে, ভারতের গজলডোবা ব্যারাজ (তিস্তা), ধলই বাঁধ (বরাক-কুশিয়ারা), কুশিয়ারা ব্যারাজসহ একাধিক স্থানে সঞ্চিত অতিরিক্ত পানি, আগাম কোনো বার্তা না দিয়ে একযোগে ছেড়ে দেওয়ায় পানির স্রোতে ভেসে যায় মানুষের বসতবাটি, জমির ফসল, মাছ, পশুসম্পদ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই ভয়াবহতার দায় কার? ভারতের উজানে বাঁধ, ব্যারাজ ও জলাধার রয়েছে অন্তত ৪০টির মতো, যার মধ্যে তিস্তার গজলডোবা ব্যারাজ এবং বরাক নদীর ধলই বাঁধ অন্যতম। ভারতের আবহাওয়া সংস্থা মে মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিলেও, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে (The Daily Star, ৩০ মে ২০২৫), ভারতের পক্ষ থেকে এবারের পানি ছাড়া সংক্রান্ত কোনো আগাম সতর্কতা পাঠানো হয়নি। অথচ ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম মূল দায়িত্বই ছিল এ ধরনের তথ্যবিনিময়। আবার ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের পানি ব্যবহারের আন্তর্জাতিক আইন, অনুযায়ী, উজান রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে পানি ছাড়ার আগে নিচের রাষ্ট্রকে আগাম অবহিত করা।
জাতিসংঘ পানি-সংক্রান্ত সনদের ধারা ৫ অনুযায়ী যৌথ নদীর পানির ন্যায্য ও সমতুল্য বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। ধারা ৭ অনুযায়ী, নিচু অববাহিকার রাষ্ট্রের ক্ষতি না হয়, এমন ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আছে। ধারা ১১ অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনায় অন্য রাষ্ট্রকে আগাম অবহিত করার বিধান আছে। ভারত এই কনভেনশন স্বাক্ষর করলেও এখনো অনুমোদন করেনি, তবে কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল হিসেবে এটিকে বাধ্যতামূলক ধরা হয়।
অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্র যদি জেনে-শুনে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রে মানবিক বিপর্যয় ঘটায়, তবে তা ট্রান্স বাউন্ডারি হার্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতের পানি ছাড়া এই তত্ত্বে পড়ে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। তবে ভারতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ডুম্বুর বাঁধের গেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেছে এবং এটি ইচ্ছাকৃত ছিল না। এই বক্তব্য বাংলাদেশের জন্য আশ্বস্তকর নয়, কারণ আগাম সতর্কতা ছাড়া পানি ছেড়ে দেওয়া দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে।
বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত উজানে বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ এবং অনিয়ন্ত্রিত পানি ছেড়ে দেওয়ার ফলে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা ও শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকটে ভুগছে। এই পরিস্থিতি দেশের কৃষি, অর্থনীতি ও জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, বন্যার কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৭০ শতাংশ নদীর পানি বর্ষা মৌসুমে ভারতের দিক থেকে আসে । ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তি বাস্তবায়নে নিয়মিত ৩০ শতাংশ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রতিবছর গড়ে তিন থেকে চারবার মাঝারি থেকে বড় ধরনের বন্যা দেখা দিয়েছে। ২০২২ সালে সিলেট অঞ্চলে জুন-জুলাইয়ে যে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, তাতে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।
এবার ২০২৫ সালে এখনো বর্ষা মৌসুম পুরোদমে শুরু হয়নি, তার আগেই পানি প্রবেশের যে প্রবণতা শুরু হয়েছে, তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে চলতি বছরে প্রায় এক কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বাংলাদেশের উচিত, বন্যা মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া। পাশাপাশি বাংলাদেশ যদি চায়, তবে আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের এই আচরণকে ‘পরিবেশগত অপরাধ’ হিসেবে তুলে ধরতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ‘বেসিনভিত্তিক সমন্বয়’ ছাড়া এ সমস্যার কোনো টেকসই সমাধান নেই। এই মুহূর্তে দরকার ভারতের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ‘রিভার ইনফরমেশন শেয়ারিং চুক্তি’, যেখানে প্রতিটি বাঁধ থেকে কখন, কত পানি ছাড়া হবে, তা জানিয়ে দিতে হবে ৭২ ঘণ্টা আগে।
বাংলাদেশের জন্য এখন সময় এসেছে আন্তর্জাতিক পাননীতি মেনে চলার জন্য ভারতের প্রতি জোরালো কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার এবং অভ্যন্তরীণভাবে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অর্থনীতিকে রক্ষা করার। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশেষ করে, জাতিসংঘ, SAARC, BIMSTEC-এর মতো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে ভারতের পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি উত্থাপন করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।
বাংলাদেশ চাইলে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিজ বা আইনিজের পরামর্শ গ্রহণ সম্ভব, তবে মামলার জন্য দুই রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন। জাতিসংঘ মানবাধিতার কমিশন পানি সংকটকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে, আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিযোগ দিলে রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়তে পারে, এটি কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। সে ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম ভারতীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা (real-time telemetry); রিভার ব্যারিয়ার সিস্টেম ও বাঁধ উন্নয়ন; পানি সংরক্ষণ হ্রদ স্থাপন এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট অবকাঠামো গড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে কূটনৈতিক চুক্তি ও নজরদারি বাড়াতে পারে, যেমন ভারতের সঙ্গে তিস্তা ও অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন চুক্তি দ্রুত সম্পাদন করা।
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতা, সরকারের সক্রিয়তা এবং জনগণের সচেতনতা, এই ত্রয়ীর সমন্বয় ছাড়া এই দুর্যোগের চক্র থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। প্রয়োজন এখন একটি ‘পানি কূটনীতি’, যেখানে শক্তি নয়, সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে দক্ষিণ এশিয়ার নদী রাজনীতি। বিশেষ করে এখন সময় এসেছে আন্তর্জাতিক পানিনীতি মেনে চলার জন্য ভারতের প্রতি জোরালো কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার এবং অভ্যন্তরীণভাবে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অর্থনীতিকে রক্ষা করার। দেশের জনগণের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় একটি সুসংহত এবং কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন জরুরি। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট পরিকল্পনায় বন্যা প্রতিরোধে কমপক্ষে ৫,০০০ কোটি টাকার আলাদা বরাদ্দ থাকা জরুরি।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক
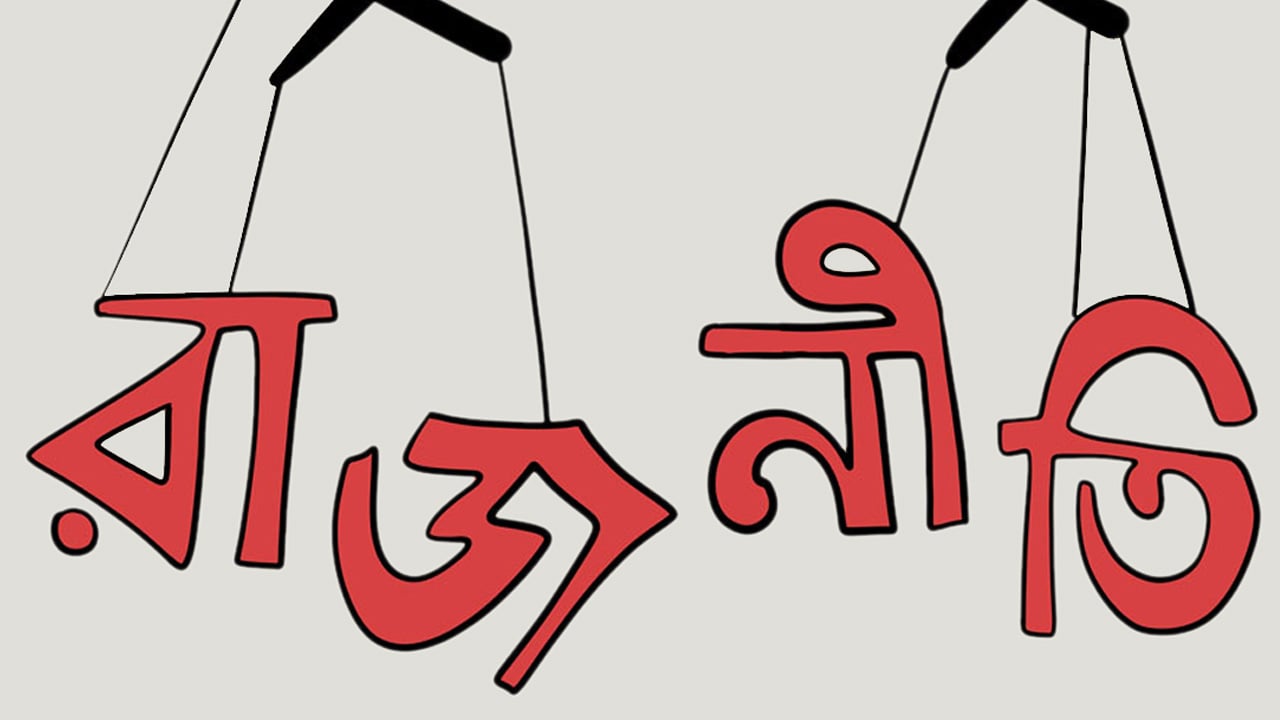
বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমন এক অববাহিকায় অবস্থিত, যার ওপর প্রভাব ফেলে প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে ভারতের নদী ব্যবস্থাপনা। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে হঠাৎ বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয়, বিশেষ করে ভারতের উজানে অপ্রত্যাশিতভাবে পানি ছেড়ে দেওয়ার কারণে। প্রশ্ন উঠেছে, ভারত কি বাংলাদেশকে না জানিয়ে পানি ছেড়ে দিয়েছে? আর যদি তা করে থাকে, তাহলে তা কি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয়? এবং এর মোকাবিলায় বাংলাদেশের করণীয়ই বা কী?
বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও, এখন সে পরিচিতি আর শুধু ঐতিহ্যের নয়, বরং আশঙ্কার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হঠাৎ করে যে প্রবল বন্যা দেখা দেয়, তা শুধু প্রাকৃতিক নয়—বরং এর পেছনে রয়েছে কূটনৈতিক গাফিলতি, আঞ্চলিক দায়িত্বহীনতা এবং দীর্ঘস্থায়ী পানি বণ্টন সমস্যার সুনিপুণ প্রতিচ্ছবি।
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তা, ধরলা, করতোয়া এবং বরাক-কুশিয়ারা নদীর উজানে বিশেষ করে, ভারতের গজলডোবা ব্যারাজ (তিস্তা), ধলই বাঁধ (বরাক-কুশিয়ারা), কুশিয়ারা ব্যারাজসহ একাধিক স্থানে সঞ্চিত অতিরিক্ত পানি, আগাম কোনো বার্তা না দিয়ে একযোগে ছেড়ে দেওয়ায় পানির স্রোতে ভেসে যায় মানুষের বসতবাটি, জমির ফসল, মাছ, পশুসম্পদ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই ভয়াবহতার দায় কার? ভারতের উজানে বাঁধ, ব্যারাজ ও জলাধার রয়েছে অন্তত ৪০টির মতো, যার মধ্যে তিস্তার গজলডোবা ব্যারাজ এবং বরাক নদীর ধলই বাঁধ অন্যতম। ভারতের আবহাওয়া সংস্থা মে মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিলেও, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে (The Daily Star, ৩০ মে ২০২৫), ভারতের পক্ষ থেকে এবারের পানি ছাড়া সংক্রান্ত কোনো আগাম সতর্কতা পাঠানো হয়নি। অথচ ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম মূল দায়িত্বই ছিল এ ধরনের তথ্যবিনিময়। আবার ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের পানি ব্যবহারের আন্তর্জাতিক আইন, অনুযায়ী, উজান রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে পানি ছাড়ার আগে নিচের রাষ্ট্রকে আগাম অবহিত করা।
জাতিসংঘ পানি-সংক্রান্ত সনদের ধারা ৫ অনুযায়ী যৌথ নদীর পানির ন্যায্য ও সমতুল্য বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। ধারা ৭ অনুযায়ী, নিচু অববাহিকার রাষ্ট্রের ক্ষতি না হয়, এমন ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আছে। ধারা ১১ অনুযায়ী পানি ব্যবস্থাপনায় অন্য রাষ্ট্রকে আগাম অবহিত করার বিধান আছে। ভারত এই কনভেনশন স্বাক্ষর করলেও এখনো অনুমোদন করেনি, তবে কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল হিসেবে এটিকে বাধ্যতামূলক ধরা হয়।
অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্র যদি জেনে-শুনে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রে মানবিক বিপর্যয় ঘটায়, তবে তা ট্রান্স বাউন্ডারি হার্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতের পানি ছাড়া এই তত্ত্বে পড়ে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। তবে ভারতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ডুম্বুর বাঁধের গেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেছে এবং এটি ইচ্ছাকৃত ছিল না। এই বক্তব্য বাংলাদেশের জন্য আশ্বস্তকর নয়, কারণ আগাম সতর্কতা ছাড়া পানি ছেড়ে দেওয়া দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে।
বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত উজানে বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ এবং অনিয়ন্ত্রিত পানি ছেড়ে দেওয়ার ফলে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা ও শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকটে ভুগছে। এই পরিস্থিতি দেশের কৃষি, অর্থনীতি ও জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, বন্যার কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৭০ শতাংশ নদীর পানি বর্ষা মৌসুমে ভারতের দিক থেকে আসে । ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তি বাস্তবায়নে নিয়মিত ৩০ শতাংশ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রতিবছর গড়ে তিন থেকে চারবার মাঝারি থেকে বড় ধরনের বন্যা দেখা দিয়েছে। ২০২২ সালে সিলেট অঞ্চলে জুন-জুলাইয়ে যে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, তাতে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।
এবার ২০২৫ সালে এখনো বর্ষা মৌসুম পুরোদমে শুরু হয়নি, তার আগেই পানি প্রবেশের যে প্রবণতা শুরু হয়েছে, তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে চলতি বছরে প্রায় এক কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বাংলাদেশের উচিত, বন্যা মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া। পাশাপাশি বাংলাদেশ যদি চায়, তবে আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের এই আচরণকে ‘পরিবেশগত অপরাধ’ হিসেবে তুলে ধরতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ‘বেসিনভিত্তিক সমন্বয়’ ছাড়া এ সমস্যার কোনো টেকসই সমাধান নেই। এই মুহূর্তে দরকার ভারতের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ‘রিভার ইনফরমেশন শেয়ারিং চুক্তি’, যেখানে প্রতিটি বাঁধ থেকে কখন, কত পানি ছাড়া হবে, তা জানিয়ে দিতে হবে ৭২ ঘণ্টা আগে।
বাংলাদেশের জন্য এখন সময় এসেছে আন্তর্জাতিক পাননীতি মেনে চলার জন্য ভারতের প্রতি জোরালো কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার এবং অভ্যন্তরীণভাবে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অর্থনীতিকে রক্ষা করার। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশেষ করে, জাতিসংঘ, SAARC, BIMSTEC-এর মতো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে ভারতের পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি উত্থাপন করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।
বাংলাদেশ চাইলে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিজ বা আইনিজের পরামর্শ গ্রহণ সম্ভব, তবে মামলার জন্য দুই রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন। জাতিসংঘ মানবাধিতার কমিশন পানি সংকটকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে, আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিযোগ দিলে রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়তে পারে, এটি কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। সে ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম ভারতীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা (real-time telemetry); রিভার ব্যারিয়ার সিস্টেম ও বাঁধ উন্নয়ন; পানি সংরক্ষণ হ্রদ স্থাপন এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট অবকাঠামো গড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে কূটনৈতিক চুক্তি ও নজরদারি বাড়াতে পারে, যেমন ভারতের সঙ্গে তিস্তা ও অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন চুক্তি দ্রুত সম্পাদন করা।
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতা, সরকারের সক্রিয়তা এবং জনগণের সচেতনতা, এই ত্রয়ীর সমন্বয় ছাড়া এই দুর্যোগের চক্র থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। প্রয়োজন এখন একটি ‘পানি কূটনীতি’, যেখানে শক্তি নয়, সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে দক্ষিণ এশিয়ার নদী রাজনীতি। বিশেষ করে এখন সময় এসেছে আন্তর্জাতিক পানিনীতি মেনে চলার জন্য ভারতের প্রতি জোরালো কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার এবং অভ্যন্তরীণভাবে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অর্থনীতিকে রক্ষা করার। দেশের জনগণের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় একটি সুসংহত এবং কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন জরুরি। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তবে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট পরিকল্পনায় বন্যা প্রতিরোধে কমপক্ষে ৫,০০০ কোটি টাকার আলাদা বরাদ্দ থাকা জরুরি।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে, তখন দুর্নীতি কেলেঙ্কারি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের কারণে দেশটিতে অসন্তোষের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই ভারতে একটি নতুন যুগের সূচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার এই প্রতিশ্রুতি ছিল—‘সবকা সাথ,
১ ঘণ্টা আগে
বিচার দীর্ঘ হবে, জটিলও বটে; কিন্তু ন্যায়ের প্রকৃত মাপকাঠি কেবল রায়ে নয়, স্মৃতির সততায়। গুমের স্মৃতির মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ প্রমাণ করছে—জাতি ক্ষত ভুলে নয়, তা স্বীকার করেই আরোগ্য লাভ করে। যেমন জার্মানি মুখোমুখি হয়েছিল হলোকস্টের, আর্জেন্টিনা তার ‘ডার্টি ওয়ারের’, আর দক্ষিণ আফ্রিকা তার বর্ণবৈষম্য
১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরে যাতায়াত মানে এক ধরনের যুদ্ধ। প্রতিদিন অফিসে যাওয়া-আসার পথে এ যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয় লাখ লাখ মানুষকে। অশেষ বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় অন্য যাতায়াতকারীদেরও। যানজটে মূল্যবান সময় অপচয় আর যানবাহনের তেলই শুধু পুড়ছে না; বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব বহুমাত্রিক। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী
১ দিন আগে
লৌহমানবীখ্যাত মার্গারেট থ্যাচার যখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, তখন তার ছেলে ট্রাফিক আইনলঙ্ঘন করার দায়ে জরিমানার শিকার হয়েছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সন্তান বলে রক্ষা পাননি। কারণ ইংল্যান্ডে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, প্রধানমন্ত্রী, লর্ড, ব্যারন কিংবা সাধারণ মানুষ যেই হন না কেন। এই তো অতিসম্প্রতি ব্রিটেনে
১ দিন আগে