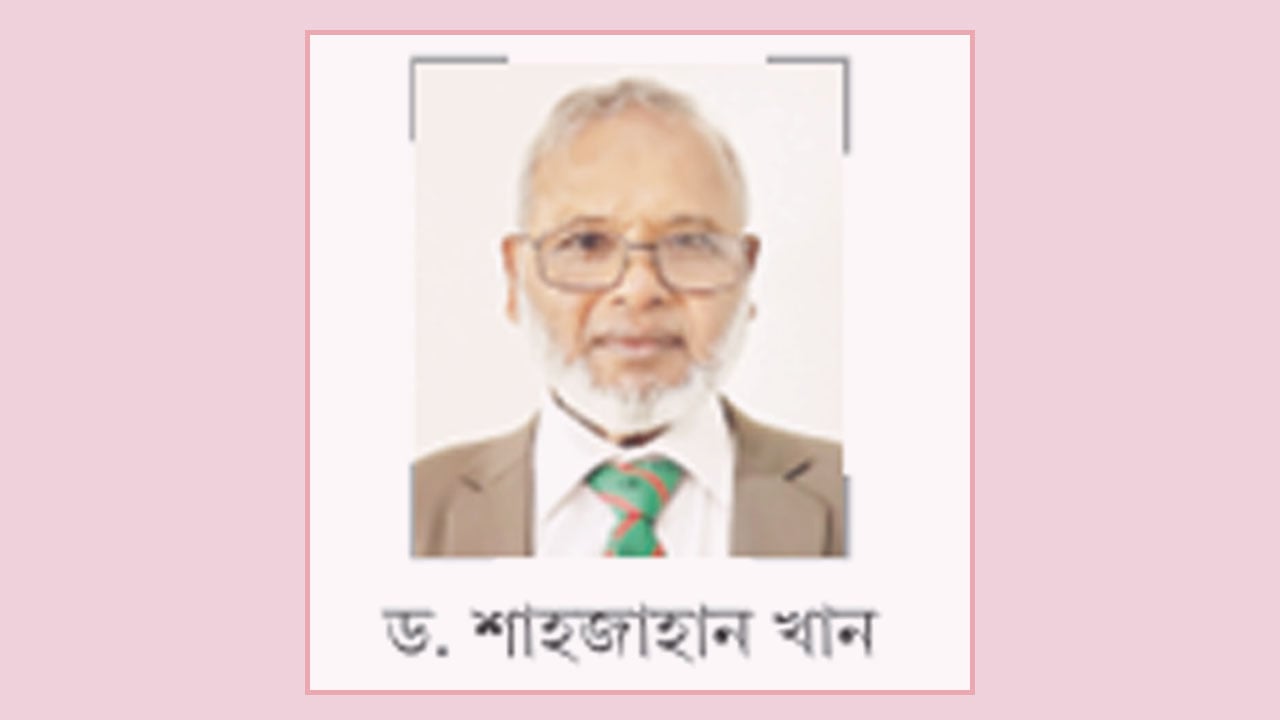আজকের বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলত শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ ঘিরে। যে বিশ্ববিদ্যালয় যত মানসম্মত শিক্ষা দিতে পারে, যত বেশি প্রভাবশালী গবেষণা প্রকাশ করতে পারে, সে-ই বিশ্ব র্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকে। তাই বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের শিক্ষা ও গবেষণার কৌশল পুনর্গঠন করছে, প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করছে, যাতে তারা আরো কার্যকর হতে পারে।
কিন্তু বাংলাদেশে এমন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ভালো করছে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা এখনো আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের উচ্চশিক্ষা খাত আজও রাজনৈতিক প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনার শিকার। এতে প্রকৃত মেধা ও গবেষণা-সাফল্যের পরিবর্তে আনুগত্য বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে তরুণরা নতুন জ্ঞান তৈরি করবে, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি গড়ে তুলবে এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে। এখান থেকেই জাতি ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানুষ তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান কাঠামোয় থেকে আমরা বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারব না। তাই কাঠামোগত পরিবর্তন এখন অপরিহার্য।
২. শাসন ও কার্যনির্বাহী শাখার বিভাজন
যেকোনো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি প্রধান অংশ থাকে। একদিকে শাসন (Governance), যেখানে উচ্চপর্যায়ের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ হয়। অন্যদিকে থাকে কার্যনির্বাহী (Executive), যারা দৈনন্দিন শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
২.১ বিশ্ববিদ্যালয় শাসন
শাসনব্যবস্থা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা। এখানে ঠিক হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য কী হবে, কোন কৌশলে সেটি অর্জিত হবে, বাজেট কীভাবে তৈরি হবে, এমনকি টিউশন ফি পর্যন্ত কীভাবে নির্ধারণ হবে। এই শাসন কাঠামো দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল থাকে এবং প্রতিবছর ধাপে ধাপে সদস্য পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।
২.১.১ সিনেট ও তার ভূমিকা
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সিনেটকে শাসনের প্রধান সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। তবে এ জন্য কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। সিনেটে থাকতে হবে—শিক্ষক, কর্মচারী, পেশাজীবী, আর্থিক ও আইন বিশেষজ্ঞ, সরকারি প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থী। সিনেটের প্রধান হবেন চ্যান্সেলর, যিনি চার বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।
এখনকার মতো রাষ্ট্রপতিকে শুধু নামমাত্র চ্যান্সেলর করে রাখার পরিবর্তে, উন্নত দেশের মতো যোগ্য ও সম্মানিত নাগরিককে এ পদে আনার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদটি শুধু রাজনৈতিক প্রতীক নয়, এটি এক ধরনের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের প্রতীক।
২.২ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যনির্বাহী
কার্যনির্বাহী শাখা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। তারা প্রতিদিনের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালায়। এর প্রধান হচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর (কোথাও একে রেক্টর বা প্রেসিডেন্টও বলা হয়)। তাকে নির্বাচিত করা হবে একটি সার্চ কমিটির মাধ্যমে, যারা যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, গবেষণার মান এবং প্রশাসনিক দক্ষতা যাচাই করে প্রার্থী বাছাই করবে। নির্বাচিত ভাইস চ্যান্সেলর চার বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।
২.২.১ সিন্ডিকেট ও তার ভূমিকা
ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে সিন্ডিকেট হবে কার্যনির্বাহী শাখার মূল নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এর কাজ হলো সিনেটের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনের কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে কি নাÑতা তদারকি করা। এতে ভাইস চ্যান্সেলর ছাড়াও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক প্রতিনিধি, কর্মচারী প্রতিনিধি এবং ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
৩. একাডেমিক নেতৃত্ব শিক্ষা ও গবেষণা
বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শক্তি দুটি—শিক্ষা ও গবেষণা। কিন্তু বৈশ্বিক র্যাংকিংয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় গবেষণা। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এর মানে আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে গবেষণা প্রকাশ, প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা অনুদান সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা করা।
এই পরিবর্তন আনতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রশাসনে নতুন কাঠামো প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর রাখলেই চলবে না; গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্যও আলাদা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর থাকা দরকার। তার অধীনে গবেষণা পরিচালক এবং একটি শক্তিশালী গবেষণা টিম কাজ করবে। পাশাপাশি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আধুনিক গবেষণা ডেটাবেস তৈরি করতে হবে, যাতে সব গবেষণা, প্রকাশনা, অনুদান ও ব্যয়ের তথ্য সহজে পাওয়া যায়।
৪. মেধাভিত্তিক নিয়োগ
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য নির্ভর করে সঠিক নেতৃত্ব ও যোগ্য শিক্ষক-গবেষকের ওপর। তাই সব নিয়োগ হতে হবে মেধাভিত্তিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, ডিন কিংবা প্রভোস্ট—সবার নিয়োগে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি ও প্রতিযোগিতা থাকতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাব, ব্যক্তিগত পরিচিতি বা পক্ষপাতিত্ব নয়, বরং একাডেমিক ও পেশাগত যোগ্যতাই হবে আসল মানদণ্ড।
৫. অর্জনভিত্তিক অর্থায়ন
সরকারি অর্থায়নও কর্মদক্ষতার সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যূনতম অর্থ পাবে মৌলিক খরচ চালানোর জন্য। কিন্তু যারা শিক্ষা ও গবেষণায় ভালো করবে, তারা অতিরিক্ত অর্থায়ন পাবে পুরস্কার হিসেবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এক ধরনের স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা তৈরি হবে এবং সবাই ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হবে।
বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে শাসন, প্রশাসন, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং অর্থায়নে কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। শাসন কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য সংসদে আইন সংশোধন প্রয়োজন। তবে একাডেমিক ও প্রশাসনিক সংস্কারগুলো চাইলে এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
এই প্রস্তাবনাগুলো নিছক ধারণা নয়, এগুলো একটি রূপরেখা, যা বিশেষজ্ঞদের আলোচনার মাধ্যমে আরো উন্নত করা যেতে পারে। সঠিক কাঠামো, স্বচ্ছ নিয়োগ এবং অর্জনভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একদিন বিশ্ব র্যাংকিংয়ের শীর্ষে পৌঁছাতে পারবে—এই আশা আমরা করতেই পারি।
লেখক : ইমেরিটাস প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া
ভাইস চ্যান্সেলর, এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় অব বাংলাদেশ, ঢাকা
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন