বাংলাদেশে ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটা শুনলেই সাধারণ মানুষ যখন তাচ্ছিল্যের হাসিতে মুখ বাঁকা করেন, ঠিক তখন স্রোতের বিপরীতে শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলা এক ভিন্নপথের যাত্রী তিনি। যার লেখনী সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীদের কাছে হেমলকের থেকে বিষাক্ত মনে হয়। যিনি কলম হাতে নিলে নড়বড়ে হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদী সিংহাসন—তিনি আর কেউ নন, তিনি জনবুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর। ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছাকাছি থেকে কলাটা-মুলাটা হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করা বুদ্ধিজীবীর দল আর তাদের দরবারি সমাজ হয়তো তাকে অবহেলা করেছে; কিন্তু তিনি ছিলেন সব দ্রোহ-বিপ্লবে আর প্রতিবাদে নিজের স্বভাবভঙ্গিমায় নির্লিপ্ত, মতপ্রকাশে অবিচল ও নির্ভীক।
প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশে যখন বুদ্ধিজীবীদের গর্বের অন্ত থাকে না। সেখানে অক্সফোর্ডফেরত একজন প্রজ্ঞাবান হয়েও সেটিকে নিয়ে তিনি বাহাদুরি করেননি। তিনি তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রতিবাদী জীবন বেছে নিয়ে। আইয়ুববিরোধী লড়াইয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গণমানুষের কাতারে থেকে। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে গণমানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নে বাংলাদেশপন্থি যে চিন্তাভাবনা, তার শেকড়ও তার চিন্তায় প্রোথিত ছিল। আর সেখান থেকে বিচ্যুত একদলীয় বাকশালের বিরুদ্ধে তার মতো দাঁতভাঙা সমালোচনা আর কাউকে করতে দেখা যায়নি।
পলাতক স্বৈরাচার শেখ হাসিনার দুর্দমনীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সৎসাহস না থাকায় বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী যখন কুঁজো হয়ে হাঁটার অভ্যাস করছেন। তখনো সদম্ভে বদরুদ্দীন উমর ছিলেন চির উন্নত মম শির। কারণ একটাই, তিনি কোনো পদক বা পুরস্কারের লোভ করেননি কোনো দিন। একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ফিলিপস, আদমজী—সবই তিনি পায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন তাচ্ছিল্যের হাসিতে। তাই তো স্বাধীনতার পর তারই হাতে গড়ে তোলা লেখক শিবির থেকে বের হওয়া অগণিত লেখক বেহায়ার মতো বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তার। ওদিকে তিনি লেখকদের এই দলান্ধতাকে থোড়ায় কেয়ার করে দাঁড়িয়েছেন গণমানুষের পাশে; নেতৃত্ব দিয়েছেন কৃষক আন্দোলনেরও।
আর এ জন্যই একজন বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে নিছক কোনো নাম না। তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান, কাজে-কর্মে, চলনে-বলবে চির উজ্জ্বল এক প্রজ্ঞার অগ্নিশিখা। তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এক যুগান্তকারী ধারার স্থপতি। তিনি সাধারণ কোনো গবেষক বা চিন্তাবিদ নন, বরং একক মহিমায় গড়া এক বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠান—যিনি জীবনের পরম প্রান্ত পর্যন্ত যুক্তি, বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধের নিরন্তর সাধনায় নিয়োজিত থেকেছেন। শ্রেণি-চেতনার দীপ্তি, নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা ছিল তার চিন্তার মূলে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তাল মঞ্চ হোক বা উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রচিন্তার জটিল ক্ষেত্র—তিনি সর্বত্র দাঁড়িয়েছেন শোষণের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, নির্ভীক এক প্রতিরোধী কণ্ঠ হয়ে।
ব্যক্তি হিসেবে অভিজাত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে জন্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে এসে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার কাজটা সহজ ছিল না। তারপরও বদরুদ্দীন উমর সেটা পেরেছেন। কারণ তিনি কখনো অনিয়মতান্ত্রিক সুবিধা আর প্রাপ্তির জৌলুশের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নানা প্রতিবন্ধকতা, রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণের অনিবার্য ফল হিসেবে ধেয়ে আসা আক্রমণগুলোকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন আত্মশুদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে। তার বৌদ্ধিক শৃঙ্খলার অবলম্বন এবং সমাজ রূপান্তরের শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল ফ্যাসিবাদী শক্তির বরাভয়। যখন আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের অনেকেই সময়ের চাহিদা বা ক্ষমতার প্রলোভনে মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, বদরুদ্দীন উমর তখন ছিলেন এক অনমনীয় পুরুষ—যিনি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন নির্ভীকভাবে, নিঃসংশয়ে। আর এর প্রতিফলন ছিল চব্বিশেও। হয়তো এ জন্যই বদরুদ্দীন উমরকে ‘কণ্ঠহীন সময়ের অনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মাহরুফ চৌধুরী।
২৯ জুলাই ২০২৪ উত্তাল গণবিপ্লবের মুহূর্তে একটি দৈনিক পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন—‘বর্তমানে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, এর ফলে চারদিকে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে, তাতে এ সরকারের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ এই গণঅভ্যুত্থান যত ব্যাপক হয়েছে, এর আগে কোনো অভ্যুত্থান এত ব্যাপক কখনো হয়নি। ঢাকা শহর এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলে তো বটেই, সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।
কোটা আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় না গিয়ে সরকার ছাত্রদের ওপর যেভাবে আক্রমণ করেছে, এতে এ আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ যে যার পক্ষ থেকে এ আন্দোলনে শরিক হয়েছে। এ কথা বলা দরকার, ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছে, তা আর কোটার আন্দোলন হিসেবে দেখলেই চলবে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রলীগ যে তাণ্ডব, নির্যাতন এবং নানাভাবে জুলুম চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ ছাত্রদের ক্ষোভ ছিল। এ ক্ষোভের একটি ভূমিকাও ছাত্রদের কোটা আন্দোলনে পড়েছে।
এটিকে শুধু কোটা আন্দোলন, শুধু চাকরির আন্দোলন হিসেবেই দেখলে হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া ছিল কোটা আন্দোলনে। সরকারি আক্রমণের কারণে এই কোটা আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে একটি অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং ব্যাপকভাবে সারা দেশে অভ্যুত্থান হয়েছে।’
বদরুদ্দীন উমরের বৃদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ বোঝার জন্য তার এই বক্তব্যটুকুই যথেষ্ট। আর এ জন্যই তিনি বিশ্বপরিসরে অ্যান্তোনিও গ্রামশি, ফ্রানৎজ ফানোঁ কিংবা এদুয়ার্দো গালিয়ানোর সারিতে আসীন। তিনি তাদের মতোই কলম, কণ্ঠ, চৈতন্য আর চিন্তার ঠিকানা খুঁজেছিলেন প্রতিরোধের ভাষায়। তিনি তার বুদ্ধিবৃত্তিকে মুক্তির অঙ্গীকারে পরিণত করেছিলেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ যেখানে ক্ষমতার পদলেহনে আত্মতুষ্টি খুঁজে ফেরে, তিনি সেখানে হয়ে উঠেছিলেন ব্যতিক্রমের একমাত্র উজ্জ্বল প্রতীক। মেধা ও মননে অনন্য আর চিন্তায় আপসহীন এই বুদ্ধিজীবী তার বিশ্লেষণে যেমন ছিলেন নির্মোহ তেমনি ন্যায়ের প্রশ্নে অবিচল বলেই জুলাই নিয়ে সব থেকে সঠিক বক্তব্যটি এসেছিল তার থেকেই। তিনি রাখঢাক না করে সরাসরি বলেছিলেন—‘১৯৫২ থেকে যত গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, এটিই সবচেয়ে ব্যাপক’। বয়সের ভারে চোখে কম দেখা আর কানে কম শুনেও তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেটি বুঝতে অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছিল অন্যদের।
নৈতিক দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদার দীপ্তি আর মনুষ্যত্বের মহিমার জন্য বদরুদ্দীন উমর আমাদেরসহ আগের কয়েকটি প্রজন্মকে আলোড়িত করেছেন। চিন্তার দিক থেকে স্বতন্ত্র, বাক্য নির্বাচনে অমলিন আর চিন্তার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে নৈতিক অনমনীয়তার প্রতীক হয়ে ওঠা এই মহিরুহ আজ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষ্যকার হিসেবে তিনি যে গর্জন তুলেছিলেন সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে, সাম্য আর মানবতার পক্ষে ক্ষমতার খেলায় সেটি হারিয়ে না যাক।
বদরুদ্দীন উমরের হাত ধরে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতের যে সংলাপ, ন্যায়ের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার তা বিস্তৃত হোক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। তার চিন্তার দীপ্তি নতুন বাংলাদেশ গড়ার পাথেয় হোক আমাদের জন্য। যেখানেই শোষণ, বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় অবিচার দানা বেঁধে উঠবে, সেখানে গর্জে উঠুক ‘সক্রিয় বুদ্ধিজীবী’ বদরুদ্দীন উমরের উত্তরসূরিরা। গ্রামসির শ্রেণিচেতনা অঙ্গীকার, ফ্রেইরির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কবি নজরুলের দ্রোহ আর র্যাবোর অনিবার্য উত্তরাধিকার ডানা মেলুক তার চিন্তাকে সামনে রেখে।
বদরুদ্দীন উমরের প্রস্থান শুধু স্মৃতির শূন্যতা নয়, এর থেকে যে বিবেকের শূন্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সততার শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা পূরণের জন্য আমাদের নিজ নিজ চিন্তা, আদর্শ আর নৈতিক দৃঢ়তাকে জীবিত রাখতে হবে প্রতিশ্রুতিশীল বৌদ্ধিক চর্চায়, দ্রোহ-প্রতিরোধে এবং আমাদের সাহসে।
লেখক : সহযোগী অধ্যাপক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


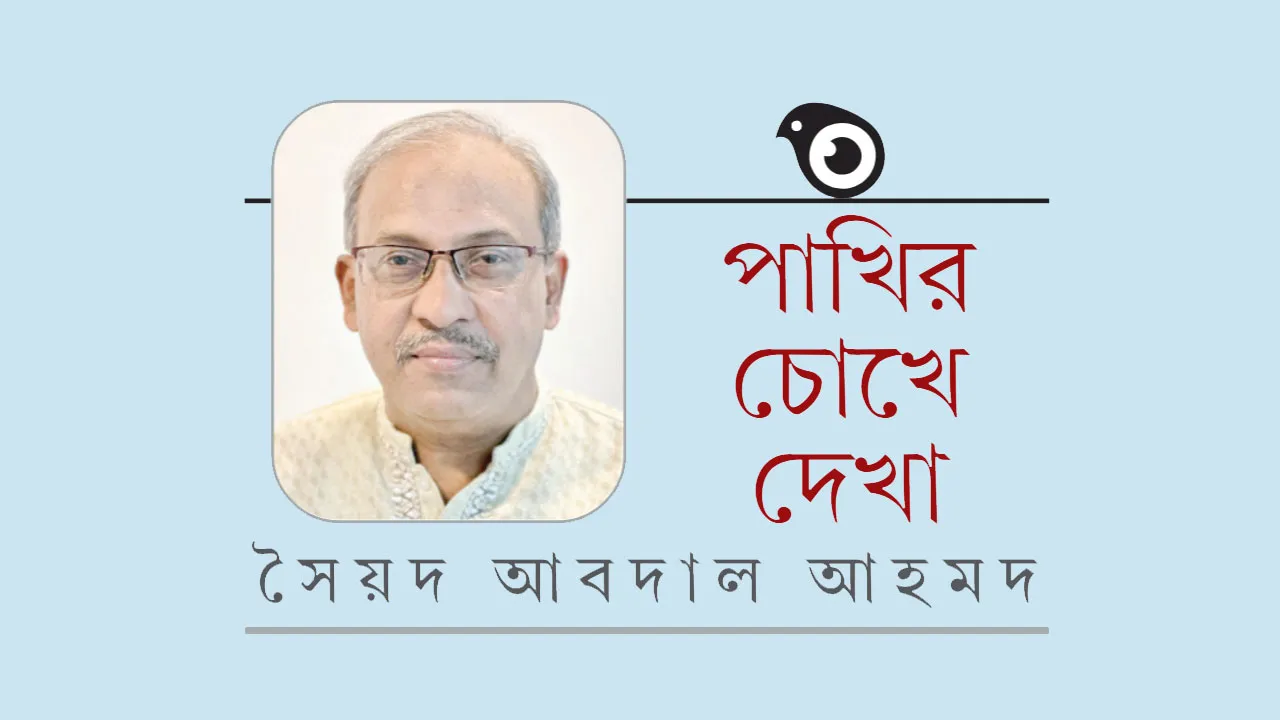 ডাকসু নির্বাচনে হোক গণতন্ত্রের সূচনা
ডাকসু নির্বাচনে হোক গণতন্ত্রের সূচনা