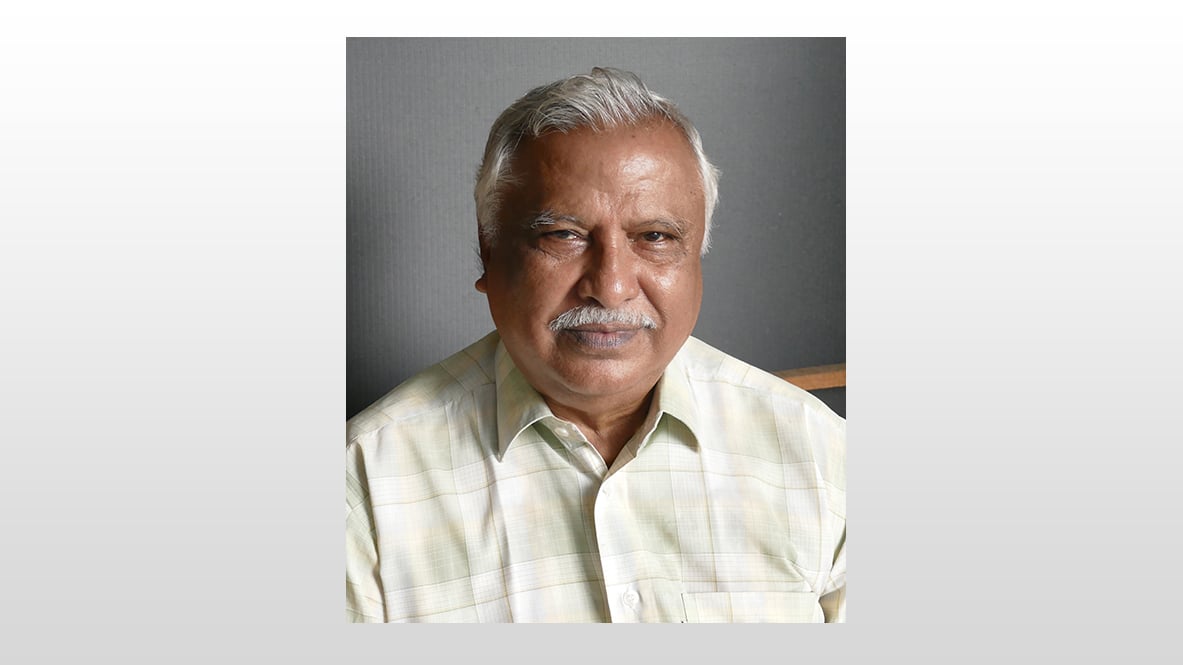২০১১ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গুরুশরণ কাউরসহ সর্বমোট ১৩৬ সফরসঙ্গীসহ ঢাকা সফরে আসেন। তার সঙ্গে আসেন প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা, আসামের তরুণ গগৈ, ত্রিপুরার মানিক সরকার ও মিজোরামের লাল খান হাওলা।
কথা ছিল এই সফরে তিস্তার নদীর পানিচুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। কিন্তু হয়নি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এতে আপত্তি করেন এবং সফরসঙ্গী হিসেবে মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে ঢাকা আসা থেকেও বিরত থাকেন।
মমতার আপত্তির কারণ হিসেবে যা জানা যায় তা হলো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মতি ছাড়াই নাকি এই চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। সফরের মাত্র কয়েক দিন আগে ক্যাবিনেটে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র সদস্য রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী বিষয়টি জানতে পেরে চুক্তির কপি সংগ্রহ করে দিল্লি থেকে ফ্যাক্সে মমতাকে পাঠান। চুক্তির কপি দেখেই ক্ষেপে যান মমতা। তিনি বলেন, শুকনো মৌসুমে তিনি কখনোই বাংলাদেশকে ৩৩ হাজার কিউসেক জল দিতে চান না। তাকে অন্ধকারে রেখে তিস্তা চুক্তি তৈরি করা হয়েছে। মমতা পরদিন মুখ্য সচিব সমর ঘোষকে দিয়ে দিল্লিকে জানিয়ে দেন, এ চুক্তি তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো জানান, তার পক্ষে মনমোহন সিংহের সঙ্গে ঢাকা যাওয়াও সম্ভব নয়। এর পরপরই ক্যাবিনেট মিনিস্টার প্রণব মুখার্জির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন ও জয়রাম রমেশ নামে আরেকজন টেলিফোনে মমতাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস আগে ২০১১ সালের মে মাসে বিপুল ভোটে ইতিহাস গড়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসা মমতা ব্যানার্জিকে টলানো সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে ঢাকা সফরের আগের দিন পররাষ্ট্র সচিব রঞ্জন মাথাই সাংবাদিকদের জানান, ‘জল আসলে অতি স্পর্শকাতর একটি বিষয়। আর ভারতের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমরা এমন কিছু করতে পারি না, যাতে রাজ্য সরকারের আপত্তি আছে।’
এর আগে ১৯৮৩ সালে যৌথ নদী কমিশনে একটি অ্যাডহক সমঝোতা হয়েছিল, তিস্তার পানিপ্রবাহের ৩৯ শতাংশ বাংলাদেশ ও ৩৬ শতাংশ ভারত ব্যবহার করতে পারবে। ভারতের জলসম্পদমন্ত্রী রামনিবাস মির্ধা এবং বাংলাদেশের পক্ষে এজেএম ওবায়দুল্লাহ সেই সমঝোতায় সই করেছিলেন এবং এটা টিকে ছিল মাত্র আড়াই বছর।
২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের সফরে যে চুক্তি সই হয়নি, সেই চুক্তি ছিল এরকম—শীতের মাসগুলোয় তিস্তার একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে যে পরিমাণ পানি থাকবে, তার ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ বাংলাদেশ ও ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভারত পাবে এবং অবশিষ্টাংশ তিস্তা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ছেড়ে দিতে হবে।
২০১১ সালের এই ঘটনার পর ১৩ বছর পার হয়েছে, কিন্তু অচল অবস্থার নিরসন হয়নি। পানি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কার্যকর কোনো বৈঠকও হয়নি। ন্যায্য প্রাপ্য পানি না পেলেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আদালতে যায়নি। অথচ ২০১৯ সালে ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একক সিদ্ধান্তে ফেনী নদী থেকে ১ দশমিক ৮২ কিউসেক (ঘনফুট প্রতি সেকেন্ডে) প্রত্যাহারের সুযোগ করে দেন। এ নিয়ে বুয়েটের ছাত্র আবরার ফেসবুকে পোস্ট দিলে তাকে ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের ছাত্র নামধারী একদল সন্ত্রাসী।
সভ্যতা বিকাশে নদীর পানি : মানবসভ্যতা বিকাশে নদীর পানি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পানি নিচের দিকে গড়ায়, রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ না মেনে ভাটিতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। পানি নিয়ে যেমন বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তেমনি মীমাংসার উদাহরণ আছে। আজ থেকে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ২৫০০ সালে সুমেরীয় শহর লাতাশ ও উম্মার মধ্যে টাইগ্রিস নদী নিয়ে বিরোধের মীমাংসা পানিচুক্তির মাধ্যমে করা হয়।
তিস্তা নদীর উৎস ও প্রবাহ : ২৪০ বছরের পুরোনো তিস্তা বাংলাদেশে চতুর্থ বৃহত্তম এবং আন্তর্জাতিক একটি নদী। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত সিকিমের ৭ হাজার ২০০ মিটার উচ্চতায় চিতামু হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশের নিলফামারী জেলার কালীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর গাইবান্ধা জেলার চিলমারীতে ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পদ্মা ও মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। ৪১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তা নদী সিকিমে ১৫৯ কিলোমিটার, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে ১৯, পশ্চিমবঙ্গে ১২৩ এবং অবশিষ্ট ১২১ কিলোমিটার বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। তিস্তা অববাহিকার আয়তন ১২ হাজার ৫৪০ বর্গকিলোমিটার।
বাংলাদেশে তিস্তার প্লাবনভূমি ২ হাজার ৭৫০ বর্গকিলোমিটার। এর সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার দুই কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। উজানে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গে বাস করে প্রায় এক কোটি মানুষ। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের কয়েক কোটি মানুষ কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, মাছ আহরণ ও দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজে তিস্তা নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল। শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি কমে যাওয়ায় প্রতি বছর প্রায় ১৫ লাখ টন বোরো ধান কম উৎপাদিত হয়, যা দেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯ শতাংশ (ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট রিপোর্ট)।
তিস্তা পানির ঘাটতির কারণে ভূর্গস্থ পানি ব্যবহার করে জমিতে সেচ দেওয়ার ফলে কৃষকের সেচের খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। উত্তরবঙ্গের খালবিল, পুকুর ও জলাশয়ও শুকিয়ে যাচ্ছে তিস্তা নদীর পানির অভাবে। এমন ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে পুরো উত্তরবঙ্গের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। আবার উজানে বর্ষায় অতি বৃষ্টির কারণে ভাটিতে প্রতি বছর বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় নদীর পাড় ভেঙে চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় প্রতি বছর। আবার নতুন বালিতে নদীর তলদেশে পলি জমে নদীর নাব্য হ্রাস পায় এবং পরের বছরের জন্য বন্যার কারণ হিসেবে দেখা দেয়।
তিস্তা নদীর উজানে বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র : গত ৫০ বছরেও তিস্তা নদীর পানি বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। এ অবস্থায় ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ৬০ কিলোমিটার উজানে জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবায় তিস্তা নদীতে হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম নির্মাণ করে ভারত। এভাবে তিস্তা নদীর পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ভারত। এ ছাড়া প্রকাশিত খবর অনুসারে, দার্জিলিংয়ে নির্মিত হচ্ছে আরো তিনটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র এবং উজানে পশ্চিমবঙ্গ আরো দুই সেচের জন্য খাল খনন করে তিস্তার পানি সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ভারত। এর ফলে শুকনা মৌসুমে তিস্তা নদী থেকে বাংলাদেশ কোনো পানি পাবে না বলা যায়।
তিস্তা মহাপরিকল্পনা : তিস্তা নদীর পানি চুক্তি না হওয়ায় উঠে আসে তিস্তা মহাপরিকল্পনা। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় দুই দেশের মধ্য ২৭টি সমঝোতা চুক্তি হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা। চীনের রাষ্ট্রদূতও তিস্তা নদী এলাকা পরিদর্শন করেছেন। চীন সরকার নিজ উদ্যোগে ও খরচে দুই বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে প্রকল্প নির্মাণ সম্ভব বলে জানিয়েছে এবং বাংলাদেশকে অর্থায়নসহ তিস্তা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছে।
একসময় চীনের হোয়াংহো নদী প্রতিবছর শত শত মাইল জনপদ ভাসিয়ে দিত। তখন হোয়াংহো নদীকে বলা হতো চীনের দুঃখ। চীন সর্বনাশা সেই নদী শাসন করায় চীনের মানুষের দুঃখ ঘুচেছে। চীনের জিয়াং প্রদেশের সুকিয়ান সিটির আদলে তিস্তার দুপাশে পরিকল্পিত স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে মহাপরিকল্পনায়। ১০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী ১০ মিটার গভীরতায় খনন করে নদীর দুপাড়ে ১৭৩ কিলোমিটার তীর রক্ষা বাঁধ, নদীর দুপাড়ে স্যাটেলাইট শহর নির্মাণ, বালু সরিয়ে কৃষিজমি উদ্ধার করে বছরে ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা এবং প্রতি বছর ২০ হাজার কোটি টাকার বাড়তি ফসল উৎপাদন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে চীনা পাওয়ার কোম্পানি প্রকল্প বাস্তবায়নে নকশা ও সম্ভাব্যতার কাজ শেষ করেছে। চীন তিস্তার পানি ব্যবস্থাপনাসহ নদীকে ঘিরে নানা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পরিকল্পনায় সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে আট হাজার কোটি টাকার বেশি। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তিস্তাপাড় হয়ে উঠবে পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশের সুকিয়ান সিটির মতো সুন্দর নগরী।
ভারতের উদ্বেগ ও আপত্তি : ভারতের সংবেদনশীল ‘চিকেন নেক’-এর কাছাকাছি হওয়ায় ভারত এই মহাপরিকল্পনায় উদ্বিগ্ন। পতনের আগে জুন মাসে ভারত ঘুরে এসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, ‘ভারত ও চীন দুই দেশই তিস্তা মহাপরিকল্পনায় আগ্রহী। আমরা দুই দেশের প্রস্তাব দেখে যেটা ভালো সেটাই গ্রহণ করব।’ কিন্তু কয়েক দিন পরে তিনি জানান, ‘ভারত ও চীন দুই দেশই প্রকল্পে আগ্রহী, তবে ভারতকে দেওয়াই ভালো হয়।’ ভারতের চাপে এবং ভারতকে খুশি করতে শেখ হাসিনা তিস্তা প্রকল্প থেকে চীনকে বাদ দেন। এর পরপরই চীন সফরে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা।
আমাদের আশু করণীয় : উত্তরবঙ্গের মাটি ও মানুষের সমস্যার নিরসনের জন্য অবিলম্বে তিস্তা মহাপরিকল্পনা শুরু করা প্রয়োজন। প্রধান উপদেষ্টা তার চীন সফরে তিস্তা প্রকল্পসহ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চীনকে ৫০ বছরের জন্য যে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন, তা খুবই আশাব্যঞ্জক একটি দিক।
আন্তর্জাতিক নদীর ন্যায্য পানি প্রাপ্তির চেষ্টা হিসেবে ১৯৯৬ সালে হেলসিংকি এবং ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত নীতি অনুসারে আমাদের তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা দাবি করতে হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে।
লেখক : সাবেক বিসিএস কর্মকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন