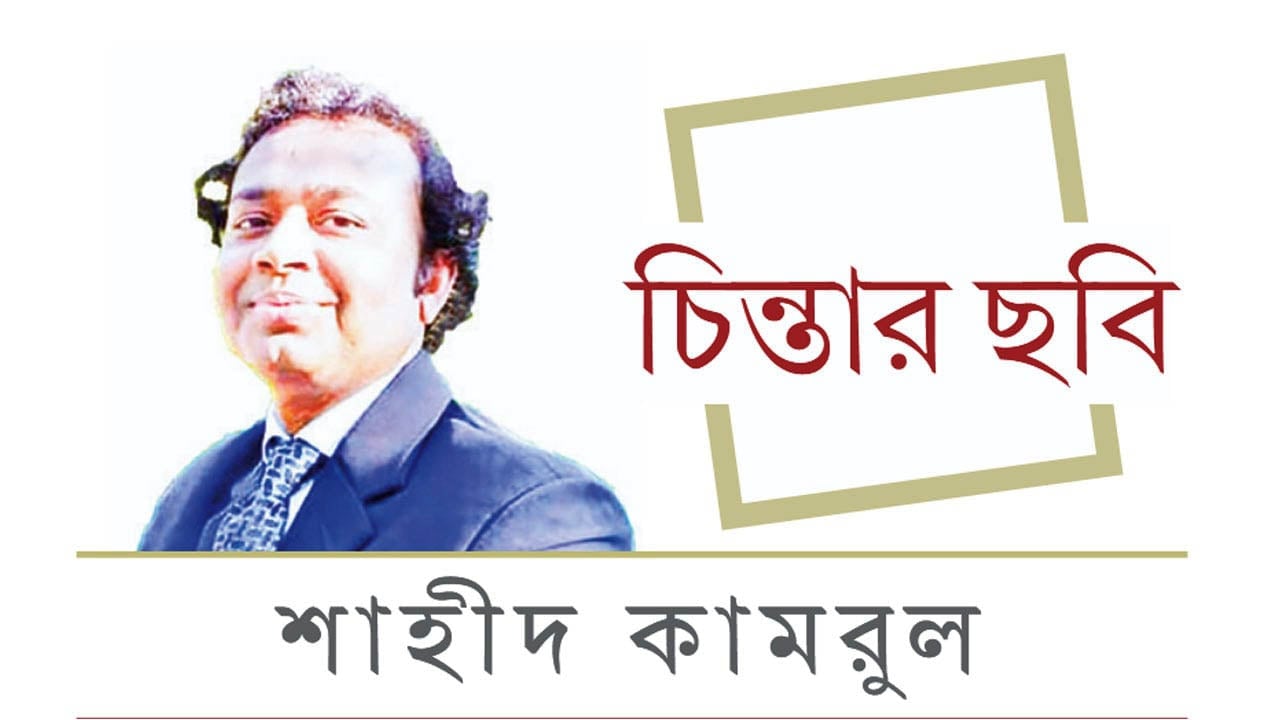ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের সাফল্য অনেকটা জগদ্বিখ্যাত গ্রিক কবি হোমারের মহাকাব্য ‘ওডিসি’র ওডিসিয়াস চরিত্রের মতো। ওডিসিয়াস তার দীর্ঘ যাত্রায় কেবল শক্তি বা প্রতিশোধের জন্য নয়, বরং বিচক্ষণতা, কৌশল ও নৈতিকতার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করেন। ঠিক তেমনই শিবির প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেনি, বরং তারা নিজেদের পরিকল্পনা ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোটারদের আস্থা অর্জন করেছে।
বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রজনন ক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। জাতীয় রাজনীতির প্রতিটি ধাপেই এখানকার ছাত্ররাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে—১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সবশেষে জুলাই ৩৬ বিপ্লব।
সুতরাং ডাকসু নির্বাচন কেবল একটি ছাত্র সংসদ নির্বাচন নয়, বরং জাতীয় রাজনীতির ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। সাম্প্রতিক ডাকসু নির্বাচনে দেখা গেল বিএনপিপন্থি ছাত্রদল, বাগছাস ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলো বড় ধরনের ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে, অথচ ইসলামী ছাত্রশিবির ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে।
এই ফলাফল কেবল একটি সাংগঠনিক বাস্তবতা নয়, বরং বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ভোটারদের মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মূল আলাপে আসার আগে বলি রাখি, আমি ব্যক্তিগতভাবে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির বিপক্ষে, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের ছাত্র ও যুবসমাজ নষ্ট হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে—ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা ক্ষমতা থেকে অন্যদের নামানোর ক্ষেত্রে।
ছাত্ররা করবে ছাত্ররাজনীতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন প্রভৃতি। এসবের মাধ্যমেই তারা সত্যিকারের সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠবে এবং নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের হাকিকত শিখবে। ছোটবেলা থেকেই লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি করলে একচোখা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এরা রাজনৈতিকভাবে অন্ধ হয়ে যায়, কখনোই পুরো আকাশ দেখতে পারে না। যে বয়সে সহপাঠীরা বন্ধু হওয়ার কথা, সে বয়সে রাজনীতির অপসংস্কৃতির ছোবলে আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে শত্রু হয়ে যায়; আর সেই শত্রুতার কারণে নৃশংসভাবে মেরে ফেলতেও কার্পণ্য করে না।
মোটাদাগে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল মূলত তিনটি বড় ভুল করেছে। প্রথমত, তারা ধরে নিয়েছিল যে, যেসব ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান বা বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা ছাত্রলীগকে সমর্থন করে না, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ছাত্রদলের ভোটার। অর্থাৎ তারা নতুন ভোটার সংগ্রহের কৌশল নেয়নি। রাজনীতিতে এটি মারাত্মক ভুল। রবার্ট মিশেলসের ‘Iron Law of Oligarchy’ তত্ত্ব দিয়ে বিষয়টি বোঝা যায়।
মিশেলস বলেছিলেন, রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় অভিজ্ঞ নেতার দখলে চলে যায় এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয় না। ছাত্রদলও সেই রোগে আক্রান্ত। নতুন প্রজন্মের জন্য কোনো প্রণোদনা তৈরি না হওয়ায় তাদের ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক উপস্থিতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে ভোটের সময় তারা মূলত পুরোনো সমর্থকদের ভরসায় থেকেছে।
দ্বিতীয়ত, ছাত্রদল তাদের ন্যারেটিভ নির্ধারণে বড় ধরনের ভুল করেছে। তারা ইসলামী ছাত্রশিবিরকে পাকিস্তানপন্থি বলে আক্রমণ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশি ভোটারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান মনোভাবকে রাজনৈতিক পরিচয়ের কেন্দ্রে রাখে। ফলে শিবির পাকিস্তানপন্থি বলে অভিযুক্ত হওয়াটা এই ভোটারদের চোখে উল্টো প্রশংসা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।
অর্থাৎ শিবিরই প্রকৃত অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান শক্তি—এই ধারণা আরো মজবুত হয়েছে। এই ব্যর্থতা গ্রামসির হেজেমনি তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায়। গ্রামসি বলেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা কেবল বলপ্রয়োগে টিকে থাকে না, বরং জনগণের সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেও টিকে থাকে। ছাত্রদল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেরাই প্রতিপক্ষের ন্যারেটিভকে শক্তিশালী করেছে।
তৃতীয়ত, ছাত্রদল নিজেদের বিকল্প কর্মসূচি উপস্থাপন করতে পারেনি। তারা কেবল প্রতিপক্ষকে নিন্দা করে সময় নষ্ট করেছে। অথচ রাজনীতির মূল চ্যালেঞ্জ হলো—নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরা। হান্না আরেন্ট বলেছিলেন, রাজনীতি মানে মানুষের সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা (power of collective action)। ছাত্রদল এই সম্মিলিত কর্মশক্তি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক প্রতিক্রিয়া, ইতিবাচক ভিশন নয়।
বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যর্থতা ভিন্ন ধরনের হলেও ফলাফল একই। তারা মূলত আদর্শিক রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থেকেছে। তাদের এজেন্ডা ছিল গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, প্রগতিশীলতা প্রভৃতি। কিন্তু ভোটারদের চোখে এই বিষয়গুলো তেমন প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। কারণ ডাকসুর ভোটাররা জাতীয় রাজনীতির অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান বনাম প্রো-ইন্ডিয়ান মেরূকরণ নিয়ে চিন্তা করেছিল বলে মনে করি। ফলে বামদের প্রগতিশীল স্লোগান ভোটে রূপান্তরিত হয়নি।
বামদের আরেকটি বড় ব্যর্থতা হলো বিভক্তি। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা একক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। এর ফলে তাদের প্রার্থী দাঁড় করালেও ভোট ছড়িয়ে গেছে। বোর্দিয়ুর ‘Capital’ ধারণা দিয়ে বিষয়টি বোঝা যায়। বোর্দিয়ু বলেছিলেন, সমাজে তিন ধরনের মূলধন থাকে—অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক।
বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে ছিল সাংস্কৃতিক ক্যাপিটাল (আদর্শ, বক্তৃতা, তত্ত্ব); কিন্তু তাদের কাছে ছিল না পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্যাপিটাল (ভোট টানার কৌশল, মাঠপর্যায়ের সংগঠন ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য)। ফলে তারা সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ হলেও নির্বাচনী বাস্তবতায় দুর্বল থেকে গেছে। এছাড়া বামরা ভোটারদের মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছে।
তারা ধরে নিয়েছিল যে ছাত্রসমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রগতিশীল। কিন্তু বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের ‘Imagined Communities’ ধারণা অনুযায়ী, জাতি বা রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি হয় কল্পিত কমিউনিটির মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভোটারদের একটি বড় অংশ নিজেদের পরিচয় নির্ধারণ করছে অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান আবেগের ভিত্তিতে। ফলে বামদের প্রগতিশীল আদর্শ ভোটারদের কল্পিত কমিউনিটির সঙ্গে মেলে না।
আর বাগছাশ নিজেই বিএনপি ও বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর মতো জামায়াত-শিবিরকে দোষারোপ করেছে; কিন্তু বাস্তবে তাদের কৌশল এবং প্রচার স্টাইল পুরোনো পাকিস্তানি ন্যারেটিভ অনুসরণ করেছে। তারা নিজেকে একটি ‘বিরোধী ছাত্র সংগঠন’ হিসেবে উপস্থাপন করার কোশেশ করেছে, কিন্তু ফলাফল দেখায় যে ভোটাররা এ ধরনের আউটডেটেড প্রোপাগান্ডা এবং জামায়াত-শিবিরের রাজনৈতিক ভাষাকে চিনতে পেরেছে।
অর্থাৎ, বাগছাশ জামায়াত-শিবিরকে দোষারোপ করলেও তারা নিজেরাই নির্দিষ্ট ভিশন বা কার্যকর কর্মসূচি ছাড়া পুরোনো রাজনীতির রুটিনে আটকে থেকে ভোটারদের কাছে প্রভাব ফেলতে পারেনি।
অন্যদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কামিয়াবির বেশ কিছু কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, তারা জানত, অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান ভোট তাদের হাতেই রয়েছে। তারা সেই ভোটকে ধরে রেখে নতুনভাবে সেক্যুলার মুসলমানদের টানার চেষ্টা করেছে। ফলে তারা দ্বৈত সুবিধা পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিবির ন্যারেটিভে জয়ী হয়েছে। ছাত্রদল যখন তাদের পাকিস্তানপন্থি বলে আক্রমণ করেছে, তখন অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান ভোটারদের চোখে সেটি উল্টো প্রশংসা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে শিবিরকে আলাদা করে নিজেদের অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান পরিচয় প্রমাণ করতে হয়নি।
তৃতীয়ত, শিবির কর্মসূচি উপস্থাপনে মনোযোগ দিয়েছে। তারা কেবল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেনি; বরং নিজেদের পরিকল্পনা ও ভিশন ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের কেবল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নয়, বরং প্রোঅ্যাকটিভ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। গ্রামসির ভাষায়, তারা আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক হেজেমনি তৈরি করতে পেরেছে। এছাড়া মিশেল ফুকোর ‘Power/Knowledge’ তত্ত্ব এখানে প্রাসঙ্গিক। ফুকো বলেছিলেন, ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। শিবির ক্যাম্পাসে নিজেদের ন্যারেটিভকে জ্ঞানের মতো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে—অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান অবস্থানই প্রকৃত দেশপ্রেম। এই জ্ঞান-আকারে ন্যারেটিভই তাদের ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করেছে।
অন্যদিকে লাক্লাউ ও মুফের ‘Discourse Theory’ দিয়ে বোঝা যায়, শিবির সফল হয়েছে, কারণ তারা ‘অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান’ নামক একটি ফ্লোটিং সাইনিফায়ার নিজেদের হাতে নিতে পেরেছে। ছাত্রদল বাগছাস ও বামরা যেখানে এই শব্দবন্ধকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করেছে, শিবির সেটিকে ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিচয়ে রূপান্তর করেছে। তাছাড়া শিবির বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ শিক্ষার্থীদের প্রার্থী করেছে, যারা সৎ, বিশ্বাসযোগ্য, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং আচরণে নম্র। গুজারা সাল থেকে শুরু করে এ বছর পর্যন্ত তারা দেশব্যাপী বৃহৎ শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেছে এবং আস্থা জাগিয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করে যে, শিক্ষার্থীরা এখন নৈতিক, শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
যাহোক, ডাকসু নির্বাচন কেবল একটি ছাত্রসংগঠনের প্রতিযোগিতা নয়, এটি জাতীয় রাজনীতির প্রতিচ্ছবি। শ্রীলঙ্কার উদাহরণ ও ডাকসু ফলাফল মিলিয়ে দেখা যায় যে, জাতীয় নির্বাচনে অনুরূপ পরিস্থিতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। শ্রীলঙ্কার জনগণ তৎকালীন সরকারের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে নতুন কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে ভোট দিয়েছে। বাংলাদেশে যদি জনগণ ক্ষমতাপ্রত্যাশী দলের দুর্বলতা, নেতৃত্বহীনতা ও জনমতের সঙ্গে সংযোগহীনতাকে অনুভব করে, তবে ডাকসু ফলাফলের মতো নতুন কোনো শক্তি জাতীয় নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে ক্ষমতায় আসতে পারে।
এটি নির্দেশ করে, কেবল রাজনৈতিক ঐতিহ্য বা ঐতিহ্যবাহী ভোটারসংখ্যা নয়, বরং নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ ও জনমতের সঙ্গে সংযোগই নির্বাচনের মূল নির্ধারক হবে। এছাড়া হ্যান্স মগেনসেনের সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব অনুযায়ী, জনমত ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। ডাকসুতে শিবিরের কার্যকর প্রচারণা এবং ছাত্রদল, বাগছাস ও বামদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে, জনগণ যখন একটি শক্তিশালী, সংগঠিত ও স্বচ্ছ ন্যারেটিভ দেখতে পায়, তখন তারা ওই দলকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত থাকে।
একইভাবে জাতীয় নির্বাচনে যদি বিএনপি বা অন্যান্য বিরোধী দল জনমতের ক্ষোভকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নতুন রাজনৈতিক শক্তি বা বিরোধী ন্যারেটিভ জাতীয় পর্যায়ে তাদের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
সর্বশেষে বলা যায়, ডাকসু নির্বাচন দেখিয়ে দিল, কেবল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে রাজনীতি করা যায় না। জনগণ সবসময় একটি ইতিবাচক ভিশন দেখতে চায়। রাজনীতির বড় শিক্ষা হলো ন্যারেটিভ ও সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া নির্বাচনি সাফল্য আসে না। যে দল জনগণের কল্পিত কমিউনিটির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারবে এবং ইতিবাচক কর্মসূচি উপস্থাপন করতে পারবে, তারাই ভবিষ্যতে ক্যাম্পাস ও জাতীয় রাজনীতিতে টিকে থাকবে।
ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল, শ্রীলঙ্কার উদাহরণ ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলো একত্রিতভাবে প্রমাণ করছে, বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী শক্তি এবং নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারে। জনগণের দুর্নীতি, অসন্তুষ্টি ও নেতৃত্বহীনতার প্রতি মনোভাব নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে।
শিবিরের বিজয় কেবল ক্যাম্পাসের ঘটনা নয়, এটি একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রাথমিক ইঙ্গিত, যা দেখাচ্ছে, যদি বিএনপি বা অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী দল জনগণের সঙ্গে যথাযথ সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ডাকসু ফলাফলের মতো জাতীয় নির্বাচনেও তাদের পিছিয়ে পড়া বা হারানো সম্ভব। ডাকসুর ফলাফলে আমি বিন্দুমাত্র অবাক হইনি, বরং এটা অনুমিত ছিল!
৫ আগস্টের পর তরুণ প্রজন্ম নতুন ভাবধারার রাজনৈতিক সূচনা চেয়েছিল, কিন্তু আমরা কি তা দেখেছি! ব্যক্তি ও দলের বদল হয়েছে, কিন্তু সেই পুরোনো ধারার স্লোগান আর ট্যাগিং প্রথা রয়ে গেছে, তথাকথিত সুশীলদের চুলকানি বন্ধ হয়নি। তারা আগের মতোই নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা আর ফায়দা লুটতে চেয়েছেন! ফলাফল একেবারে হাতেনাতে।
সময় থাকতে নিজেদের বদলান! না হয় ভবিতব্যের নিকষ কালো অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন।
লেখক : সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক, ফ্রাই ইউনিভার্সিটি বার্লিন, জার্মানি
গবেষণার ক্ষেত্র : উপনিবেশ, উপনিবেশ-উত্তর ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃতি, উপমহাদেশ ভাগ, পরিবেশ, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন