ইসরাইলের মোসাদ পরিচালিত ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’ গোয়েন্দা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অভিযান হিসেবে বিবেচিত। এটি আধুনিক যুদ্ধের এমন একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে কোনো গুলি ছোড়া হয় না, কোনো সেনা সীমান্ত অতিক্রম করে না—তবুও একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কাঠামো ভেতর থেকে ভেঙে ফেলা হয় প্রযুক্তি, প্রতারণা ও নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই মিশন গোয়েন্দা যুদ্ধের সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছে, যেখানে ট্যাংক ও সৈন্য নয়, বরং ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গভীর গোপন অপারেটিভ, সাইবার অনুপ্রবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক চাতুর্যই বড় হাতিয়ার।
বাংলাদেশের জন্য এটি কেবল একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা নয়, বরং এটি এক গভীর জাতীয় উদ্বেগের বিষয়। কারণ বাংলাদেশেরও রয়েছে একটি প্রভাবশালী ও উত্তপ্ত প্রতিবেশী—ভারত, যার সঙ্গে ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ সামরিক ও গোয়েন্দা সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্ক শুধু প্রতিরক্ষা ক্রয়-বিক্রয়েই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাইবার নিরাপত্তা, নজরদারি প্রযুক্তি ও আভিযানিক কৌশলেও দুই দেশের সমন্বয় বহু দূর এগিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিকভাবে এসব কার্যক্রম দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা হিসেবে উপস্থাপিত হলেও বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের জন্য এটি একটি সুপ্ত হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে।
ভারত অনেক আগেই প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে—স্যাটেলাইট নজরদারি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ড্রোন, ফেস রিকগনিশন, সাইবার স্পাইওয়্যার, চতুর্মাত্রিক গোয়েন্দা সমন্বয়সহ। এদের অনেক কিছুই ইসরাইল থেকে সংগ্রহ করা এবং সে অনুযায়ী উন্নয়নকৃত। দক্ষিণ এশিয়ার ক্রমবর্ধমান মেরূকরণ ও রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এসব কৌশল ভবিষ্যতে যদি বাংলাদেশকে লক্ষ করে ব্যবহার করা হয়, তবে সেটি হবে অত্যন্ত ভয়ানক এক চিত্র।
তেহরানে মোসাদের অভিযান দেখিয়েছে, কীভাবে সামাজিক অসন্তোষ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও ডিজিটাল নিরাপত্তার ফাঁকফোকর ব্যবহার করে একটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা যায়। বাংলাদেশ যদিও ডিজিটাল উন্নয়নের পথে অনেক এগিয়েছে, তবুও কিছু বাস্তব দুর্বলতা রয়ে গেছে, যেমন বেকার যুবসমাজ, রাজনৈতিক বিভাজন, এনজিও-নির্ভরতা, বিদেশি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও টেকনিক্যাল ঠিকাদারদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ এবং কৃত্রিম উপায়ে তৈরি জনমত—এসবই একসময় বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার প্রবেশপথ হয়ে উঠতে পারে।
এ কারণে ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’ আমাদের জন্য একটি সতর্ক সংকেত। এটি কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সতর্কতা নয়, বরং আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে একটি বাস্তব শিক্ষা। ভবিষ্যতের যুদ্ধ আর সীমান্ত দিয়ে আসবে না, তা আসবে আমাদের সার্ভার, নজরদারি ব্যবস্থার ফাঁকে, অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের ছায়ায় এবং তথ্য-প্রযুক্তির অদৃশ্য হাত ধরে। বাংলাদেশের উচিত এখনই ডিজিটাল দুর্বলতা খুঁজে বের করে তা মেরামত করা, বিদেশি প্রভাব পর্যবেক্ষণ জোরদার করা, গোয়েন্দা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি জনগণের ভেতরে এক গভীর দেশপ্রেম ও সচেতনতা তৈরি করা।
আমরা একটি এমন সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন রাষ্ট্রের ভেতর থেকেই তাকে অচল করে ফেলা যায়—সামরিক নয়, বেসামরিক ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরক্ষা শক্তিই হবে আমাদের টিকে থাকার ভিত্তি। নিরাপত্তা এখন শুধু সেনাবাহিনীর কাজ নয়; এটি একটি বহুমাত্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও নাগরিক অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অপারেশন একাধিকভাবে বিশ্লেষণযোগ্য এবং তার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
১. তথ্যনির্ভর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা : দুর্বলতার ছিদ্র কোথায়? বাংলাদেশ একটি সীমান্ত-সংকটপীড়িত ও ভূরাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর দেশ। চারদিকে ভারতের প্রভাব বিস্তার, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা চাপ, দক্ষিণ এশিয়ার জল-সংকট ও ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ চক্র—সব মিলিয়ে এটি একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ নিরাপত্তা পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রেক্ষাপটে যদি কোনো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশে মোসাদের মতো বহুস্তরীয় ও প্রযুক্তিনির্ভর মিশন চালাতে চায়, তবে তা কতটা প্রতিহত করা সম্ভব? আমাদের প্রশ্ন উঠবে, সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্ব কাদের হাতে? কটি সরকারি সংস্থা তথ্যপ্রযুক্তি নিরাপত্তায় সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত কাজ করছে? গোপন সরকারি ডেটা কতটা নিরাপদ, বিশেষ করে কনসালট্যান্ট, বিদেশি সংস্থা ও ঠিকাদারদের সঙ্গে ভাগাভাগির সময়? যদি উত্তরগুলো দুর্বল হয়, তাহলে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।
২. স্থানীয় অসন্তুষ্টি ও ‘সামাজিক হ্যাকিং’ : সবচেয়ে বিপজ্জনক চোরাগলি। মোসাদ তাদের অভিযান চালাতে ইরানের অভ্যন্তরে এমন কিছু মানুষকে রিক্রুট করেছিল যারা হয়তো প্রশাসনের ওপর অসন্তুষ্ট, বা প্রলোভনে পড়ে গিয়েছিল। এটাই ‘social hacking’—রাষ্ট্রের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সেই শূন্যস্থানগুলো খুঁজে বের করা, যেখান দিয়ে বাইরের শক্তি ঢুকে যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকার যুবসমাজ, এনজিও কাঠামোর অদৃশ্য দখল, সীমান্তবর্তী এলাকার অসন্তুষ্ট জনগণ—এগুলো কি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ‘সহজ প্রবেশদ্বার’ হয়ে উঠছে না? আমাদের সমাজের এসব দুর্বল জায়গা একদিন যদি প্রযুক্তির সমন্বয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় কোনো ‘Rising Lion’-এর সামনে, তাহলে সশস্ত্র বাহিনী, ডিজিটাল কাঠামো, এমনকি রাষ্ট্রীয় মনোবলও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।
৩. ফলস ফ্লাগ বা ভ্রান্ত প্রমাণ : বিভ্রান্তির কৌশল। মোসাদ পরিকল্পিতভাবে এমন সব প্রমাণ রেখে গিয়েছিল, যা ইরানকে বিভ্রান্ত করেছে। বাংলাদেশেও এমন ‘false narrative’ চালাতে পারার মতো প্রতিপক্ষ আছে, যারা মিডিয়া, এনজিও, ব্যবসায়িক সংস্থা, কিংবা সাইবার স্পেসে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশে অতীতে বহুবার দেখা গেছে, দায় স্বীকার করেছে ‘অজানা চক্র’, আর তদন্তে গিয়ে কাঠগড়ায় উঠে এসেছে অন্য কেউ। এ যেন আধুনিক বিভ্রান্তিকর যুদ্ধ, যেখানে সত্যকে আড়াল করা হয় সাজানো তথ্যের পর্দায়।
৪. কৌশলগত শিক্ষা : সীমান্ত নয়, নিরাপত্তা শুরু হয় মগজ থেকে। অপারেশন রাইজিং লায়ন বুঝিয়ে দিয়েছে, নিরাপত্তা এখন আর শুধু চেকপোস্ট, রাইফেল আর পাহারায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি শুরু হয় নাগরিকের মনে বিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে, সরকারের ভেতরে অনুপ্রবেশ রোধ করে, ডিজিটাল ডেটা সুরক্ষায় আধুনিক প্রতিরক্ষা গড়ে এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ মোকাবিলার মতো জনমত তৈরি করে। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা, আইসিটি ডিভিশন সেনাবাহিনীর সিগন্যাল ও ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট সবার জন্য এটা সময়োপযোগী বার্তা—প্রতিরক্ষা এখন ছদ্মবেশ, কোড, সিগন্যাল এবং মানুষের মন জয়ের লড়াই।
একটি ‘ডোমিনো’ যদি পড়ে, বাকিগুলোর পতনও সময়ের ব্যাপার মাত্র—এই সত্যটি শুধু তাত্ত্বিক নয়, বাস্তব জগতের বহু রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সীমান্তঘেরা বাস্তবতা এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের এমন এক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে প্রতিটি দুর্বলতা একটি সম্ভাব্য ফাটল, আর প্রতিটি ফাটল থেকেই শুরু হতে পারে একটি বিপজ্জনক অধ্যায়। আমাদের চারপাশে আছড়ে পড়ছে ক্ষমতার রাজনীতি, মহাশক্তির টানাপোড়েন ও আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত সীমান্ত ইস্যু, জলবণ্টন ও তিস্তা প্রশ্ন, ত্রিপুরা-মেঘালয় সীমান্তে বেড়ে ওঠা উত্তেজনা এবং বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও দিল্লির মধ্যকার কূটনৈতিক টানাপোড়েন—এসব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুবই সংবেদনশীল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মেরূকরণ, বিশ্বাসহীনতা, মিডিয়া ও সাইবার স্পেসে বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রবাহ এবং জাতীয় ঐক্যের অভাব।
এই প্রেক্ষাপটে যদি রাষ্ট্র তার জনগণের আস্থা হারায়, অর্থাৎ যদি নাগরিক মনে করে, সরকার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ, যদি গণতন্ত্র, মানবাধিকার বা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে শত্রুপক্ষ সেই দুর্বল মানসিকতা ও সামাজিক বিভ্রান্তিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। একবার যদি তথ্য ও প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়, যদি সাইবার সুরক্ষা ফাঁকফোকর দিয়ে হ্যাকার বা বিদেশি গোয়েন্দারা প্রবেশ করতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেতর থেকেই ভেঙে পড়তে পারে একটি দৃষ্টিনন্দন চেহারার পেছনে থাকা একটি ভঙ্গুর কাঠামোর মতো।
অপারেশন রাইজিং লায়ন আমাদের বাস্তবতার আয়নায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতের যুদ্ধ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তা শুরু হবে ভেতর থেকে। একজন অসন্তুষ্ট কর্মচারী, একটি হ্যাক্ড সার্ভার, একটি বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্ট—এসবই হতে পারে যুদ্ধের সূচনাবিন্দু। আধুনিক যুদ্ধ আর কেবল বারুদের নয়, এটি বিশ্বাসের, তথ্যের ও অন্তর্জালের যুদ্ধ। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজেকে পুনর্গঠন করা। তথ্য সুরক্ষা মানে কেবল ডিজিটাল ডেটা রক্ষা নয়, বরং জাতীয় ন্যারেটিভের নিয়ন্ত্রণ, জনমনে আস্থার পুনর্নির্মাণ এবং এমন এক সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলা, যা বিভাজন সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সামাজিক সংহতি এখন শুধু মানবিক মূল্যবোধ নয়, এটি একটি কৌশলগত সম্পদ। প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতা কেবল অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নয়, এটি নিরাপত্তার ঢাল। গোয়েন্দা দক্ষতা এখন আর কেবল সীমান্তে নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি সাইবার ডোমেইনে, নাগরিক সমাজে, এমনকি মিডিয়ার মনস্তাত্ত্বিক খেলায় অংশগ্রহণে প্রসারিত হয়েছে। যদি আমরা এখনই এই নতুন যুদ্ধ বাস্তবতা বুঝে নিজেদের প্রস্তুত না করি, তাহলে ভবিষ্যতের ইতিহাসে হয়তো লেখা থাকবে, ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’-এর মডেল অনুসরণ করে কোনো ‘নতুন অপারেশন’ হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ। সে অপারেশনের সময় রাষ্ট্র বুঝে ওঠার আগেই সবকিছু বদলে গিয়েছিল—ক্ষমতার ভারসাম্য, জাতীয় আত্মপরিচয়, এমনকি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বও।
এই সতর্কবার্তা শুধু আশঙ্কা নয়, এটি আত্মরক্ষার ডাক। এখনই সময় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভেতরে আত্মবিশ্বাস ও ঐক্য গড়ার এবং আধুনিক যুদ্ধের অদৃশ্য মঞ্চে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার। কারণ ভবিষ্যতের আক্রমণ হবে নিঃশব্দ, প্রযুক্তিনির্ভর ও আমাদেরই মাঝ থেকে চালানো, ঠিক যেভাবে রাইজিং লায়ন নিঃশব্দে তেহরানের বুকে নেমে এসেছিল।
‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’ বিশ্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে—আগামী দিনের যুদ্ধ শুরু হবে বাইরের সীমান্তে নয়, বরং দেশের ভেতরেই। এটি একটি সরাসরি হুঁশিয়ারি, বিশেষত বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের জন্য, যার ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যাগত ঘনত্ব ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের গতি তাকে এক অনিরাপদ ক্রসরোডে দাঁড় করিয়েছে।
আজকের বাস্তবতায়, যদি বাংলাদেশ এখনো জাতীয় নিরাপত্তাকে কেবল সামরিক শক্তি, সীমান্ত পাহারা ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভাবে, তাহলে সে এক বিপজ্জনক ভুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অপারেশন রাইজিং লায়ন দেখিয়ে দিয়েছে, প্রথম হামলা এখন আর সেনা ছাউনি কিংবা নৌঘাঁটির ওপর হয় না; হামলা শুরু হয় জনগণের মনোজগতে, সামাজিক নেটওয়ার্কে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে উসকে দিয়ে।
এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে এখনই চারটি মূল খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
প্রথমত, তথ্য নিরাপত্তা ও সাইবার সুরক্ষা খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন। এটি শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোও এর আওতায় আনতে হবে। বিদ্যুৎ গ্রিড, ব্যাংকিং সিস্টেম বা টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামোয় একটি বড় ধরনের সাইবার হামলা দেশের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দিতে পারে, যা একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে। আধুনিক হাইব্রিড যুদ্ধের একটি কৌশল হলো সমাজের ভেতরের বিভাজন—ধর্মীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিভেদকে উসকে দিয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাত সৃষ্টি করা। বাংলাদেশকে এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। বৈচিত্র্যকে দুর্বলতা নয়, শক্তি হিসেবে পরিণত করতে হবে।
তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন আজ জাতীয় নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিদেশি সফটওয়্যার, নজরদারি ব্যবস্থা বা প্রযুক্তিনির্ভরতার কারণে যে গোপন ঝুঁকি তৈরি হয়, তা এখন কেবল অর্থনৈতিক নয়, রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের জন্যও হুমকি। দেশীয় উদ্ভাবন, গবেষণা ও নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবস্থার বিকাশ একান্ত জরুরি।
চতুর্থত, গোয়েন্দা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও রূপান্তর অপরিহার্য। ঐতিহ্যগত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এখন যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশকে এমন একটি ইন্টিগ্রেটেড ও রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, যা মানসিক যুদ্ধ, বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত উগ্র গোষ্ঠী, ডিজিটাল নজরদারি এবং তথ্য ফাঁসের মতো সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক হুমকিগুলো শনাক্ত করতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে শুধু তথ্যদাতা নয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার রক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি হলো সেই হুমকি, যা সময়মতো রাষ্ট্র চিনতে পারে না। অপারেশন রাইজিং লায়ন দেখিয়ে দিয়েছে, ২১ শতকের প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি বিদেশি শক্তি কী পরিমাণ গভীর ক্ষতি সাধন করতে পারে—কোনো গুলিবর্ষণ ছাড়াই। বাংলাদেশ যদি সময়মতো সজাগ না হয়, প্রস্তুতি না নেয়, তবে পরবর্তী টার্গেট হয়ে উঠতে পারে এই দেশটিই।
তখন হয়তো ইতিহাসে লেখা হবে এক মর্মান্তিক বাক্য—‘অপারেশন রাইজিং লায়ন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরেকটি গোপন অপারেশন শুরু হয়েছিল—টার্গেট ছিল বাংলাদেশ। আর যখন তারা তা বুঝতে পেরেছিল, অনেক কিছুই ইতোমধ্যে বদলে গিয়েছিল।’
এই বাক্যটি যেন কখনো বাস্তবে পরিণত না হয়—এই হোক আমাদের সংকল্প। এখনই সময়, জাতীয় নিরাপত্তা আবার সংজ্ঞায়িত করার।
লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক, গবেষক ও লেখক
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


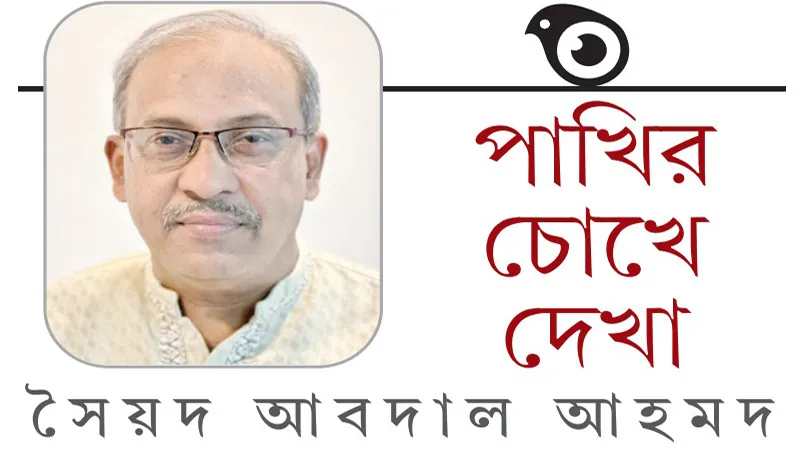 নিশিরাতের ভোট ও ডামি নির্বাচনের স্বীকারোক্তি
নিশিরাতের ভোট ও ডামি নির্বাচনের স্বীকারোক্তি