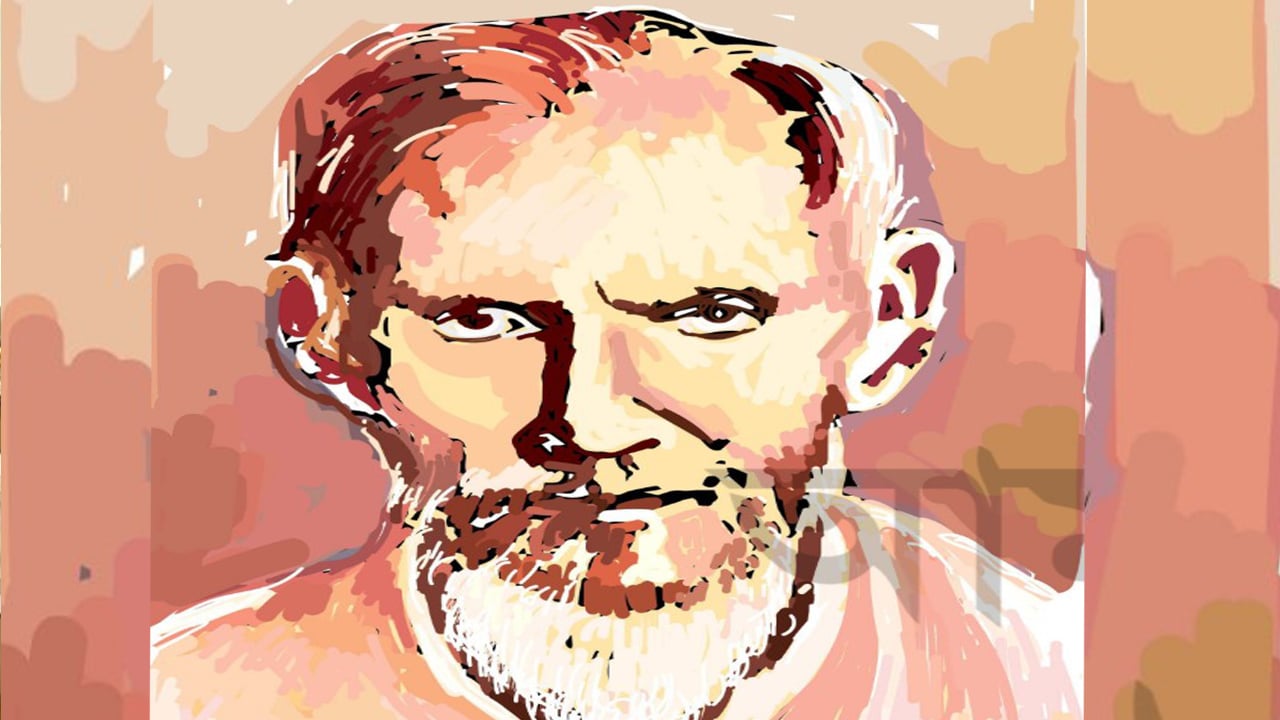প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মহাসন্ধান ও উদ্ধার শুরু হয় প্রধানত ব্রিটিশ উপনিবেশকালে, ব্রিটিশ শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রথম পর্বে ব্রিটিশ অনুদানে যারা বাংলা সাহিত্য সংগ্রহ শুরু করেন, তাদের সংগ্রহের একমাত্র বিষয় ছিল হিন্দু লেখকদের বই বা পুঁথি। ‘তারা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে পুঁথির সন্ধান করেছেন বটে, কিন্তু মুসলিম ঘরে উঁকি মেরে দেখার গরজ বোধ করেননি। অথচ পল্লিতে হিন্দু-মুসলিম প্রায় পাশাপাশি ঘরেই বাস করে—শহরে বাস করে ঘেঁষাঘেঁষি গৃহে।’ (ড. আহমদ শরীফ, সাহিত্যবিশারদ: কৃতি ও জীবনদৃষ্টি)।
সে সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, বিশ্বকোষ জার্নালের জন্য যারা ঢাকা ও কলকাতায় ‘নির্বাচিত সাহিত্য’ সংগ্রহ করছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, শিবরতন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বসু ও বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখ।
ব্রিটিশদের প্রবর্তনায় ‘হিন্দু-সাহিত্য’ সংগ্রহের যে মহাযোজন শুরু হলো, তার স্বাভাবিক ফল উনিশ শতকের হিন্দু রেনেসাঁ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) জানান, ‘ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ কি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর বাংলাদেশে যে বিস্ময়কর হিন্দু জাগরণ আসিয়াছিল, আমার যৌবনকালে তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয়াছি।’ (১৯৫২ সালের ২২ আগষ্ট পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)
সাহিত্যবিশারদই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির শিকার না হয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলা সাহিত্যের বিলুপ্তপ্রায় সম্পদ সংগ্রহ করেছেন, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। উপরে লেখা সংগ্রাহকদের সঙ্গে সাহিত্যবিশারদের পার্থক্য অসামান্য—
ক. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যবিশারদ সেই তুলনায় স্বল্প।
খ. তাদের ছিল প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ও পরিপোষণ, সাহিত্যবিশারদ ছিলেন সমর্থনহীন, সম্পূর্ণ একা।
গ. তারা শুধু হিন্দুলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেছেন, মুসলিমদের পুঁথি সংগ্রহ করেননি। সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ করেছেন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে।
তার ওপর তিনি মুসলমান হওয়ায় হিন্দুদের পুঁথি সংগ্রহে যে নিদারুণ লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, ১৯০১ সালের ৬ নভেম্বর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে এর সামান্য প্রকাশ পাওয়া যায়— ‘ইতিপূর্বেই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি ‘ম্লেচ্ছ’ মুসলমান। হিন্দুগণ ম্লেচ্ছকে পুঁথি দিতে চায় না বলিয়া আমার পক্ষে পুঁথি সংগ্রহ আরো কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে নাকি পাপ হয়। হায়!’ (মাঘ নিশীথের কোকিল, আজহার উদ্দীন খান)।
এই বৈরী সমাজে ভীষণ অপমানিত হয়েও সাহিত্য সংগ্রহকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইবাদতের আগ্রহে। এর করুণ বিবরণ পাওয়া যায় ড. আবদুল করিমের লেখায়— ‘হিন্দুর ঘরের পুঁথি সংগ্রহ করাও তার জন্য বিশেষ কষ্টকর ছিল, কারণ মুসলমানকে হিন্দুর ঘরে ঢুকতে দেওয়া হতো না, পুঁথি স্পর্শ করতে দেওয়া হতো না, পুঁথির মালিক ঘরের দেউড়ির বাইরে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখত এবং স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে দূর থেকে তাকে পুঁথি দেখাত। তিনি ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে পুঁথি দেখে নকল করে নিতেন। অশিক্ষিত লোকের কথা দূরে থাক্, অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকও পুঁথি অযত্নে ফেলে রাখত কিন্তু তাকে দেখতে দেয়নি, এইরূপ প্রমাণও আছে।’ (ড. আবদুল করিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু কথা)।
দুই
ষাট বছরের লম্বা সময়ে তার সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। একই পুঁথির একাধিক পাণ্ডুলিপি থাকায় শিরোনাম হিসেবে পুঁথির সংখ্যা ছিল ১০৮৭। প্রকাশিত হয়েছিল সামান্য কয়েকটি মাত্র। অপ্রকাশিত পুঁথির বিশাল সংগ্রহ জীবনের শেষ সময়ে উত্তরকালের গবেষকদের জন্য দান করে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া মুসলিম লেখকদের পুঁথির সংখ্যা ৫৯৭—৫৮৫টি বাংলা, ১০টি ফারসি ও দুটি উর্দু। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে দেওয়া হিন্দু লেখকদের পুঁথির সংখ্যা ৪৫০। তার মধ্যে ১৯৫৬ সালে মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির তালিকায় সাহিত্যবিশারদের ৩৩৮টি পুঁথির উল্লেখ দেখা যায়।
সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধের সংখ্যা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে সামান্য মতভিন্নতা আছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক জানান, ১১৪টি পত্রিকায় ছাপা হওয়া প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০০-এর বেশি। ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে নিবেদিত প্রবন্ধসংকলন’-এ ৪০৯টি প্রবন্ধপঞ্জি পাওয়া যায়। সাহিত্যবিশারদের ভাতিজা এবং একমাত্র পালক ছেলে ড. আহমদ শরীফ তার ‘পুঁথি পরিচিতি’তে ৪০৯টি প্রবন্ধের তালিকা প্রকাশ করেন।
সাহিত্যবিশারদের জীবনকালে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫। অবশ্য প্রকাশিত-অপ্রকাশিত মিলিয়ে বাংলা একাডেমির ‘প্রবন্ধসংকলন’ থেকে জানা যায় ১৬টি বইয়ের নাম—১. রাধিকার মানভঙ্গ, নরোত্তম ঠাকুর; ২. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা; ৩. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা; ৪. সত্যনারায়ণের পুঁথি, কবি বল্লভ; ৫. মৃগলুব্ধ, দ্বিজ রতিদেব; ৬. মৃগলুব্ধ সংবাদ, রামরাজা; ৭. গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজমাধব; ৮. জ্ঞানসাগর, আলীরাজা ওরফে কানু ফকির; ৯. শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ; ১০. সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন; ১১. গোরক্ষ বিজয়, শেখ ফয়জুল্লাহ; ১২. আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সহযোগে রচিত; ১৩. ইসলামাবাদ (চট্টগ্রামের ইতিহাস), সম্পাদনা, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৪. পদ্মাবতী, আলাওল (অপ্রকাশিত); ১৫. প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি বিবরণ (হিন্দু রচিত পুঁথি; অপ্রকাশিত); ১৬. পুঁথি পরিচিতি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত, সম্পাদনা, ডক্টর আহমদ শরীফ, প্রকাশক, মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, সংগ্রহ করা পুঁথির সংখ্যা এত বিপুল হলেও ছাপা হওয়া পুঁথির সংখ্যা এত নগণ্য কেন? এর প্রধান কারণ যে সেকালের বাঙালি মুসলমানের অচেতন অননুভব এবং বাঙালি হিন্দুর সচেতন অসহযোগ, সাহিত্যবিশারদের বিভিন্ন রচনায় এর প্রকাশ নজরে আসে। ‘মধ্যযুগের এই সাহিত্যের সন্ধান, উদ্ধার, পঠন ও গবেষণা কার্যে কৈশোর হইতে আজ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে জীবনের প্রতিদিন ব্যয় করিয়াছি। আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। তাই এক জীবনে যাহা সম্ভব ছিল, তাহা করিতে পারি নাই। সারা জীবন মুসলমান ভাইদিগকে এই পথে আকুল আহবান জানাইয়াছি কিন্তু কেহই সাড়া দিলেন না। সেই জন্য যে দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলাম, তাহা সহায়-সম্বল, সহযোগী সম্পদের অভাবে সফল হয় নাই।’ (১৯৫২ সালের ২২ আগস্ট পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)।
তবে এ বিষয়ে একটি বিশেষ ঘটনা বলে আরো পষ্ট করে প্রশ্নটি করেছেন ড. আবদুল করিম—‘আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণসহ সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত ১১ খানি বই ১৯০১ থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তার পরেও তিনি ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং অবিরত ও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তার লেখায় কোনো ভাটা পড়েনি। … আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসর তিনি বই সম্পাদনা করেন নি বা প্রকাশ করেন নি কেন? সম্পাদনা করার জন্য তার পুঁথির অভাব ছিল না। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে তিনি আর তার সম্পাদিত পুঁথি কলিকাতায় পাঠাতে সাহস পান নি। ঐ সালে কলিকাতায় কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সাহিত্যবিশারদের সম্পাদিত পুস্তক নিজেদের নামে ছাপিয়ে দেন।’ (ড. আবদুল করিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু কথা)
ঘটনার বিবরণ জানা যায় আজহার উদ্দীন খানের বরাতে—‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের হঠকারিতায় তিনি বিমূঢ় হয়ে যান এবং তারপর থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করেন। শিক্ষিতজনের প্রতি তার বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। কথা ছিল “গোপীচন্দ্রের গান” গ্রন্থ প্রকাশে তার নাম অন্যতম সম্পাদক হিসেবে থাকবে, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তাকে সুকৌশলে বাদ দিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ নিজেদের নামে প্রকাশ করেন (মে ১৯২৪)। শুধু মুখবন্ধে দীনেশ চন্দ্র সেন এবং ভূমিকায় বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য তার সম্পর্কে শুষ্ক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নিজেদের সাফাই গেয়েছেন।’ (মাঘ নিশীথের কোকিল, আজহার উদ্দীন খান)
এই ঘটনায় ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) মন্তব্য করেছিলেন— ‘সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহ ও গবেষণার কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে দীনেশচন্দ্র সেন নাম কিনেছেন। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি অঞ্চল থেকে সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক উদ্ধারিত পুঁথির উপর নির্ভর করে তিনি যেসব বই লিখেছেন—যেমন ‘প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান’ (১৯৪০)—তার মূল কৃতিত্ব আবদুল করিমের।’ (ঐ, আজহার উদ্দীন খান)
তিনি এই ঘটনাকে ‘মাৎসন্যায়ে’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত সুকুর মহম্মদ বিরচিত ‘গোপীচাঁদের সন্যাস’ গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই ঘটনা ‘সাহিত্যিক ডাকাতি’ হিসেবে বিশদভাবে বলেছেন।
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) লিখেছেন, ‘যাহারা তাহাকে সেদিন তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না। কারণ যে অসাধারণ পরিশ্রম এবং আগ্রহ সহকারে তিনি কেবল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহই নহে, তাহাদের শ্রমসাধ্য এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহা সকল যুগেই দুর্লভ।’ (মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও বাংলার নাথ সাহিত্য: আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ)
বিষয়টি সেকালের গবেষক মহলে যে দারুণ চাঞ্চল্য তৈয়ার করেছিল, ওপরের বিবরণে সেটা বোঝা যায়। এর নেতিভাব সাহিত্যবিশারদের জীবন ও গবেষণায় কত ব্যাপক ও গভীর ছিল, ড. আবদুল করিমের মন্তব্য থেকে তা জানতে পারি—‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবম্বিধ আচরণের পর সাহিত্যবিশারদ আর কোনো পুঁথি প্রকাশের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হন নি। সামর্থ্যে যেটুকু করা সম্ভব কিংবা অপরের কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাতে সফলকাম না হলেও আর নতুন করে প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকের শরণাপন্ন হন নি—তার তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাকে নিবৃত্ত করেছে।’ (ড. আবদুল করিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু কথা)
এ বিষয়ে সাহিত্যবিশারদ ব্যক্ত করেন তার বিষণ্ণ মনোভাব— ‘ডুবুরীর মতো অতল সমুদ্রে বসিয়া আমি রত্নাহরণ করিয়া দিয়াছি—আজ লোকে ডুবুরীকে ভুলিয়া যদি রত্ন লইয়া খেলিয়া নিজে আনন্দানুভব করে ও পরকে সেই আনন্দ বিলায়।’ (১৯৫২ সালের ২২ আগস্ট পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)।
তিন
সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত বাংলা সাহিত্য যে সেকালের বাঙালি মুসলমান সমাজের হীনম্মন্যতা ঘুচিয়েছে এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের কারণ হয়েছে, সাহিত্যবিশারদের দাবিতেই তার প্রকাশ নজরে আসে—‘ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম জাগরণের যে ক্ষীণ ধারা বেগবতী হিন্দু ধারার পাশাপাশি চলিতে আরম্ভ করে, তাহার সঙ্গে আমারও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। …যতটুকু সন্ধান দিয়াছি, তাহাতে মুসলমানদের হীনমন্যতা ঘুচিয়াছে।’ (১৯৫২ সালের ২২ আগস্ট পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)
কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্য, আবদুল করিমের সাহিত্য সংগ্রহে হিন্দু সমাজ দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বাঙালি মুসলমানের এই আত্মানুসন্ধান ও উদ্বোধনকে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ গ্রহণ করেছে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান হিসেবে। এ বিষয়ে সাহিত্যবিশারদ ১৯৩৯ সনের ৬-৭ মে কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মন্তব্য করেন—‘বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ বাস্তবিকই বিস্ময়ের সামগ্রী। এই বিস্ময় শুধু আমার একার নহে, ইহা আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। তাহারা নানা স্থানে—সাহিত্য-সম্মেলনে এবং কলিকাতার নানা কাগজে নানাভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানেরা এইবার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা টানিয়া আনিল বলিয়া নানা দিক হইতে নানা ভাবের হুঙ্কার কানে আসিতেছে। আমি রাজনীতিক নহি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালার মুসলমান কতখানি সাম্প্রদায়িক, সে-কথার বিচার বাঙ্গালী মুসলমান রাজনীতিকরা করিবেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানের জাগরণে সত্যই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে কি না, সে-কথা বলিবার অধিকার যত সামান্যই হউক—আমার আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।... সাহিত্যে জাতি-ধর্মের গণ্ডি আমি কখনও স্বীকার করি নাই, এখনও করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য স্বীকার করি। সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান যে জাতিরই হউক, ইহা সাহিত্য পদবাচ্য হইলেই সার্বজনীন হইয়া থাকে। ... মুসলমানের সাহিত্য সার্বজনীন সাহিত্যিক সৌন্দর্যের বিচিত্র ভঙ্গীর একদিক মাত্র। হিন্দুর সাহিত্যও তদ্রূপ আর একদিক। এই জন্যই আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যিক জাগরণকে আমি ভীতির চক্ষে দেখি না, বরং প্রীতির নয়নেই নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। কারণ অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সুগভীর এবং পরিচয় প্রাচীন।’
উপনিবেশ আমলে সাহিত্যবিশারদরা যে জাগরণের বীজ লাগিয়েছিলো, লম্বা এক শতাব্দীতে তা এখন কত বড় হলো?
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন