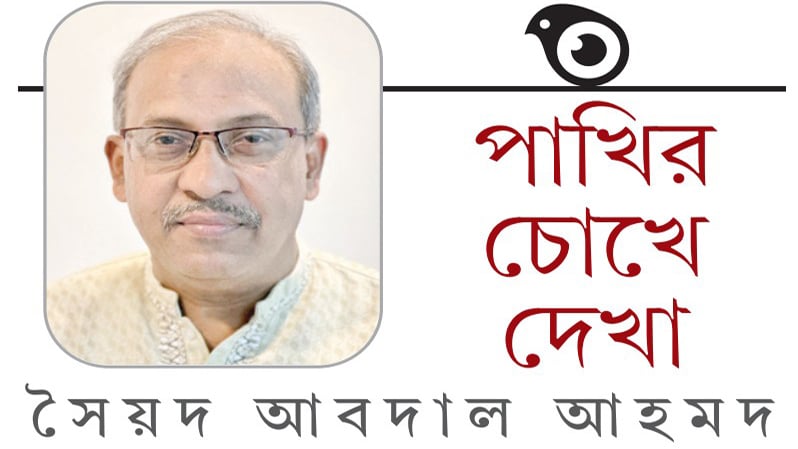গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গত শনিবার প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে কমিশন স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য সংবিধান ও আইন সংস্কারের পাশাপাশি নিবর্তনমূলক আইনগুলো বাতিল এবং বিভিন্ন ধারা সংশোধনের সুপারিশ করেছে।
কমিশনের সুপারিশে সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন করা, সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন বিসিএস নবম গ্রেডের সমান দেওয়া ও শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক করা, প্রেস কাউন্সিল অকার্যকর হয়ে যাওয়ায় প্রেস কাউন্সিল ও প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের পরিবর্তে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা, এক উদ্যোক্তার একটি গণমাধ্যম অর্থাৎ ‘ওয়ান হাউস, ওয়ান মিডিয়ার’ নীতি অনুসরণ করা, বিটিভি বেতার ও বাসসকে একীভূত করে একটি সংস্থার অধীনে আনার জন্য বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা বা জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা গঠন, বিজ্ঞাপন নীতিমালায় পরিবর্তন, বিজ্ঞাপনের সরকারি রেট বাড়ানোসহ বেশ কিছু বিষয় রয়েছে।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গত ১৮ নভেম্বর এই কমিশন গঠন করে। চার মাস অংশীজনদের সঙ্গে ৫৪টি বৈঠক করে এই প্রতিবেদন তৈরি করে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন। প্রধান উপদেষ্টা প্রতিবেদন গ্রহণ করে কমিশনকে আশু করণীয় বিষয়ে সরকারকে প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ জানান।
গণমাধ্যম কমিশন গণমাধ্যমের কাছে মানুষের প্রত্যাশা জানার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি জরিপও চালায়। এ জরিপে ৪৫ হাজার মানুষ অংশ নেন। এতে দেখা যায়, প্রতি ১০০ জনের ৬৮ জনই গণমাধ্যমকে স্বাধীন দেখতে চান। নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতহীন গণমাধ্যমের প্রত্যাশা ৬০ ভাগ মানুষের। দেশের গণমাধ্যম কেন স্বাধীন নয়Ñ এই প্রশ্নের উত্তরে ৭৯ ভাগ মানুষই বলেছেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা।
আর ৭২ ভাগ মানুষ বলেছেন, সরকারি হস্তক্ষেপ ও ৫০ ভাগ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপকেও কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জরিপের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের প্রচলিত ও বিকাশমান গণমাধ্যমের কাছে মানুষের এ প্রত্যাশা অমূলক নয়।
বাংলাদেশে স্বাধীন, বস্তুনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের বিকাশের পথে প্রধান বাধাগুলোকে তিন ভাগে দেখেছে কমিশন। তারা বলেছে, এ বাধাগুলো হচ্ছে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক। এ ছাড়া রয়েছে মালিকানার সংকট।
গণমাধ্যম কমিশন দেশের বর্তমান গণমাধ্যমের অবস্থা কী, তা অনুসন্ধান করে বলেছে, ১৯৮২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের সংখ্যা ছিল ডজনখানেক এবং সারাদেশে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাময়িকী মিলিয়ে সংখ্যাটি ছিল ৬০৪। বর্তমানে এ সংখ্যা ৩ হাজার ২৭০টি; যার মধ্যে ঢাকায় পত্রিকার সংখ্যা ১ হাজার ৩৭১টি। ডিএফপিতে মোট নিবন্ধিত দৈনিকের সংখ্যা ১ হাজার ৩৪০টি।
১৯৯৭ সালের আগে দেশে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন ও বেতার ছাড়া বেসরকারি কোনো টিভি চ্যানেল বা রেডিও ছিল না। বর্তমানে অনুমোদিত বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ৫৩টি, যার মধ্যে ৪০টি সম্প্রচারে আছে। এফএম রেডিওর অনুমোদন আছে ২৮টির। সম্প্রচারে আছে নিয়মিত ২০টি। অনলাইন পোর্টাল কী, তা সংবাদকর্মীদের কল্পনারও বাইরে ছিল।
এখন নিবন্ধিত পোর্টালের সংখ্যা ২২৮ এবং অনিবন্ধিত তিন হাজারের বেশি। পত্রিকা, টিভি, রেডিও অনলাইন মাধ্যমের যে সংখ্যাধিক্য, তা সত্ত্বেও পাঠক-দর্শক, শ্রোতা সাধারণভাবে গণমাধ্যমে নির্ভুল বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ এবং বহুমতের যথাযথ প্রতিফলন থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। নানাভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি, ক্ষমতাসীন স্বৈরতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীরা ভিন্নমত এবং সমালোচনাকে দমন আর তোষণকারীদের লালনের নিয়ম চালু করেছিল।
একদিকে ‘উই আর অল প্রাইম মিনিস্টার মেন’ ঘোষণা দেওয়া অনুগত সেবকদের স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গণমাধ্যমের দৃশ্যপটে নিয়ন্ত্রিতহীন নৈরাজ্য তৈরি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে গুম, খুন, গ্রেপ্তার ও বিচিত্র ধরনের হয়রানির মাধ্যমে সাহসী সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করেছেন, তাদের শত্রুজ্ঞান করেছেন। ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগকেই বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করে কমিশন বলেছে, ক্ষমতাধররা তা সে রাজনৈতিক ক্ষমতা কিংবা আর্থিক অথবা সামাজিক-অপপ্রয়োগে নানা ধরনের আইনের সুযোগ নেন এবং অপব্যবহার করেন। এসব আইন ও সরকার ঘোষিত নীতিমালা গত দেড় দশকে ভিন্নমত দমনে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি তোষণকারীদের লালন-পালনেও সহায়ক হয়েছে। নিপীড়ক ও দমনমূলক আইনগুলোর সংস্কার এবং সাংবাদিকতার পেশাগত অধিকার সুরক্ষায় বিশেষভাবে সরকারকে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।
পৌনে দুই কোটি লোক সংবাদপত্র পড়ে!
সংবাদপত্রের সংখ্যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কত লোক সংবাদপত্র পড়ে? গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন অনুসন্ধান করে যে তথ্য পেয়েছে, তা ভ্রু চমকে দেওয়ার মতো। সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ডিএফপির হিসাব অনুযায়ী তাদের মিডিয়া লিস্টের পত্রিকাগুলোর ঘোষিত প্রচার সংখ্যার যোগফল হচ্ছে পৌনে দুই কোটি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৫৭টি দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন এক লাখ বা তার বেশি কপি ছাপা হয়।
কিন্তু কমিশন ঢাকার দুটি হকার সমিতি এবং সারাদেশে বিতরণ করা পত্রিকা বিক্রির হিসাব এনে দেখেছে, এ সংখ্যা কোনোভাবেই ১০ লাখের বেশি নয়। তাহলে বাকি ১ কোটি ৭০ লাখ পত্রিকা কোথায় যায়? দৈনিক পত্রিকা সাধারণত শহরাঞ্চলে বিক্রি হয়। পৌনে দুই কোটি লোকই যদি পত্রিকার পাঠক হন, তাহলে দুধের শিশুকেও পাঠকের আওতায় আনতে হবে। কমিশন পুরোনো কাগজ কেনাবেচার ব্যবসাতেও খোঁজ করে দেখেছে এত বিপুল পরিমাণে অবিক্রীত কাগজ বিক্রির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মেলেনি। অর্থাৎ সবটাই ভুয়া। অলীক সার্কুলেশন দেখিয়ে শত শত আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে।
ডিএফপির তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট নিবন্ধিত দৈনিকের সংখ্যা ১ হাজার ৩৪০টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ৫৪৬টি এবং ঢাকার বাইরে থেকে ৭৯৪টি। এর মধ্যে কটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে গণমাধ্যম কমিশন খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে পাঠক ৫০টির মতো দৈনিক পত্রিকা পয়সা দিয়ে কেনেন। অন্য কোনো পত্রিকা হকারদের বিক্রির তালিকায় নেই। কিছু পত্রিকা আছে, যা ছাপা হয় নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তর এবং যাদের নিয়ে বিশেষ সংবাদ করা হয় তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এ পত্রিকাগুলো ‘দেয়াল পেস্টিং’ বা ‘আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা’ নামে পরিচিত।
বেসরকারি টেলিভিশনের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন। তবে এই চ্যানেলগুলোয় সরকারি বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি প্রায় নগণ্য। বেসরকারি বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো দর্শকসংখ্যা। এ ক্ষেত্রে বিবিধ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনদাতাদের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়। দর্শকদের প্রবণতাগুলো শনাক্ত করে বিশ্লেষণ ও সংকলনের পদ্ধতি হলো টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট বা টার্গেট রেটিং পয়েন্ট (টিআরপি)। যে টেলিভিশনের টিআরপি ভালো, তারা বেশি বিজ্ঞাপন পায়। আগে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা টিআরপি নির্ধারণ করত।
কিন্তু ২০২২ সাল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) টিআরপি নির্ধারণ করে। কিন্তু টিআরপি নির্ধারণে রয়েছে বড় ধরনের ঘাপলা। পুরো বিষয়টিই ত্রুটিপূর্ণ। সুযোগসন্ধানী টেলিভিশন প্রতারণা করে টিআরপিতে তাদের অবস্থান বাড়িয়ে নিচ্ছে।
অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের অনিয়ম করে গেছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। দলীয় নেতা এবং আওয়ামী ঘরানার লোকজনই এই নিবন্ধন পেয়েছে।
২০০৬ সালে বাংলাদেশে এফএম (ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন) রেডিওর যাত্রা শুরু। প্রথমদিকে জনপ্রিয়তা পেলেও এখন এর আকর্ষণ নেই। গণমাধ্যম জরিপে ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা রেডিও শোনেন না এবং তাদের ৫৪ শতাংশ বলেছেন, তারা রেডিও শোনার প্রয়োজন মনে করেন না। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ বেতারের এফএম ট্রান্সমিটারের সাহায্যে জনপ্রিয় বিদেশি গণমাধ্যম বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা এবং ডয়চে ভেলে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করত। তবে শ্রোতাদের চাহিদা ভাটা পড়ায় এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।
৫৪ বছরে গণমাধ্যমের হালচাল
গণমাধ্যম কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের দীর্ঘ ৫৪ বছরের পথচলার ঐতিহাসিক পরিক্রমা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পর্বটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। স্বাধীনতার পর তা বছর দু-একের মতো স্থায়ী হয়েছিল। আর দ্বিতীয় পর্বটি ছিল নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর।
আর এই দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়টি ছিল হতাশাজনক। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ এবং ১৯৮২-১৯৯০ সালের মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দারুণভাবে সংকুচিত হয় এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ধারাবাহিক চেষ্টা হয়েছে। তবে এর মধ্যে ১৯৭৫-৮২ সময়কালে গণমাধ্যম সীমিত আকারে স্বাধীন বা অধিকার চর্চার সুযোগ পেয়েছিল।
১৯৯০-পরবর্তী বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর আমরা একই ধরনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথমে ধীরে ধীরে উদারীকরণ এবং এরপর নতুন নতুন কৌশলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটে যে, দেড় দশক ধরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং তা এখন ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬৫তম স্থানে রয়েছে।
২০২১ সালে রিপোর্টার্স স্যঁ ফ্রুতিঁয়ে (আরএসএফ) রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন, চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী’ (প্রেস ফ্রিডম প্রিডেটরস) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল।
বিভিন্ন সময় সরকারগুলো গণমাধ্যমের আনুগত্য আদায়ের জন্য যেমন প্রলোভন দেখিয়েছে, তেমনই দমন-পীড়নের কৌশলও অবলম্বন করেছে। প্রকাশনা ও সম্প্রচার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা; মুদ্রণসামগ্রী ও সম্প্রচার সরঞ্জামের ওপর আমদানি শুল্ক নির্ধারণ; সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ; বিজ্ঞাপনের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব; সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার সীমিতকরণ; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের নামে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ; পরোক্ষ হুমকি ও হয়রানির উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
স্বাধীনতার পরপরই সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কৌশল হিসেবে সরকার রপ্তানির জন্য বিদেশে উচ্চ চাহিদার অজুহাত দেখিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্টের ওপর কোটা আরোপ করে। পরবর্তী বছরগুলোয় যখন সংবাদপত্রগুলো আমদানি করা নিউজপ্রিন্টের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন এই কোটাব্যবস্থা সম্পাদকীয় নীতিকে প্রভাবিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক মিত্রদের অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা খোলাবাজারে বিক্রির মতো অনৈতিক ব্যবসার সুযোগ তৈরি করে দেয়। আনুগত্যকে পুরস্কৃত করার একটি হাতিয়ার হিসেবে সরকারি বিজ্ঞাপনের ব্যবহার একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়।
লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, আমার দেশ
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন