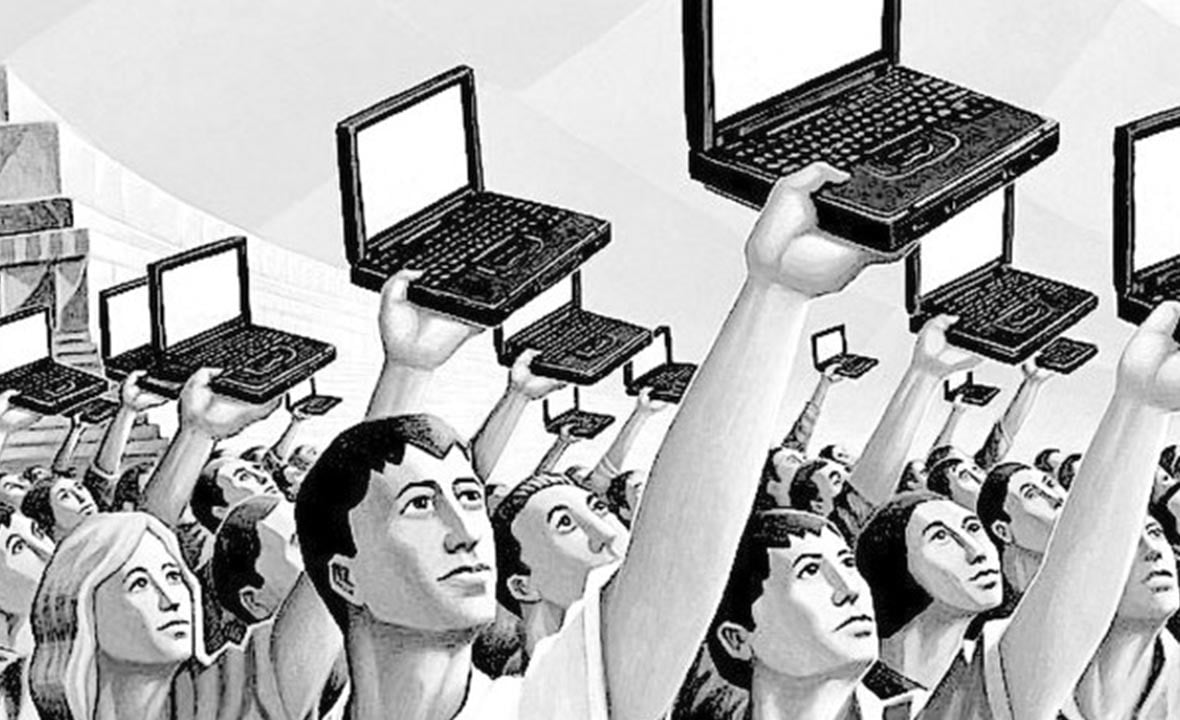‘রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারবিষয়ক সব মতামত ওয়েবসাইটে দিয়ে দেব, দেশের যেকোনো মানুষ সব দেখতে পাবে-সাবলীল ভাষায় এক বাক্যের এই ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রফেসর ইউনূস বাংলাদেশে ডিজিটাল ডেমোক্রেসির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। শেখ হাসিনা এবং তার ছেলের বদৌলতে ডিজিটাল শব্দটা বলতে যদিও আম জনতা সাধারণত হরির লুট বোঝে কিন্তু এই ডিজিটাল ডেমোক্রেসি হতে পারে বাংলাদেশ ২.০-এর রাজনৈতিক ভিত্তি, যার ওপর গড়ে উঠবে নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। কিন্তু কীভাবে আমরা ফ্যাসিবাদের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রকে এই ডিজিটাল ডেমোক্রেসিতে রূপান্তর করব, সব অংশীজনকে সঙ্গে নিয়ে সেটি এখন বড় প্রশ্ন।
আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটা খুবই জটিল এবং অজানা মনে হতে পারে; কিন্তু এক যুগ আগে তাইওয়ানের তরুণ সমাজ এর সমাধান বের করেছিল, যা এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই অনুকরণ করা হয়। ২০১৪ সালে তাইওয়ানের বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে পার্লামেন্টে রাজনীতিবিদের আলোচনা তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যার ফলে সানফ্লাওয়ার মুভমেন্ট নামে এক আন্দোলন তৈরি হয়। এই আন্দোলনের একপর্যায়ে তাইওয়ানের পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ এবং ভাঙচুর করা হয়। তাইওয়ান সরকার এরপর চীনের সঙ্গে ওই চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে তরুণদের গণ-আলোচনা করার একটা উপায় খুঁজে বের করতে বলে।
তাইওয়ানের একটি সামাজিক প্রযুক্তি সংগঠন, যারা সানফ্লাওয়ার মুভমেন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফরম যেমন ফেসবুকের আদলে ভি তাইওয়ান নামে একটা গণ-আলোচনা করার প্ল্যাটফরম তৈরি করে। আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে কর্মরত তরুণ স্বশিক্ষিত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার Audrey Tang এই প্ল্যাটফরম তৈরিতে নেতৃত্ব দেন এবং মূলত আমেরিকা সিয়াটল শহরের আরেক তরুণ Megill ও তার বন্ধু-বান্ধবের তৈরি করা ওপেন সোর্স প্ল্যাটফরম pol.is ব্যবহার করেন।
২০১১ সালের ওকুপাই ওয়াল স্ট্রিট এবং আরব বসন্তের প্রেক্ষাপটে তৈরি করা এই pol.is প্ল্যাটফরম, অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফরমের চেয়ে তিনটি কারণে ভিন্ন। প্রথমত. এটা সবার মতামতের সমতা তৈরি করে, দ্বিতীয়ত. এটা সহমত ভাই অথবা ট্রল প্রতিরোধ করে, তৃতীয়ত. সার্বক্ষণিক ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে সহায়তা করে ।
ধরুন যেকোনো একটি বিষয়ে সংসদে বা বর্তমানের সংস্কার বিষয়ে কোনো একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা এই প্ল্যাটফরম দেওয়া হলো গণ-আলোচনার জন্য । এই প্ল্যাটফরমে যে কেউ একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বিষয়টির বা সংস্কার প্রস্তাবটির ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত বা মন্তব্য পোস্ট করতে পারবেন। সেই সঙ্গে অন্য লোকের মন্তব্যকে আপ বা ডাউনভোট করতে পারবেন, Agree/Disagree/Unsure এই তিন অপশনের মাধ্যমে। কিন্তু কেউ অন্যের মতামত বা মন্তব্যের প্রতি-উত্তর (reply), শেয়ার দিতে পারবে না।
ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফরমগুলোর অ্যালগরিদম সাধারণত যে পোস্টে বেশি মন্তব্য হয়, শেয়ার হয়, যাদের অনুগামী বেশি এবং যারা ঘন ঘন জনপ্রিয় পোস্ট দেয়, তাদের প্রাধান্য দেয়। এর ভিত্তিতে ওপরের দিকে রাখে, যাতে বেশিরভাগ মানুষ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই পোস্ট দেখতে পান, পড়েন এবং তাদের প্ল্যাটফরমে বেশি সময় ব্যয় করেন।
প্রতি-উত্তর বা শেয়ার না করতে পারার কারণে সব মতামত বা মন্তব্যের মধ্যে যে শুধু সমতার সৃষ্টিই হয় তা নয়, সহমত বা ট্রলের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। পোস্ট দিলে কেউ দেখবে না, তাহলে কী লাভ? অথবা গুম, গালি খাওয়া বা ট্রল হওয়ার ক্ষতির কথা চিন্তা করে অনেকেই তাদের মূল্যবান মতামত পোস্ট করা থেকে বিরত থাকেন। pol.is শুধু এই লাভ ক্ষতির হিসাব থেকেই মন্তব্যকারীকে মুক্তি দেয় না, আপ বা ডাউনভোটের মাধ্যমে জনপরিসরে কোন মতামত কতটা মূল্যবান বা ফালতু, তা খুব দ্রুত নির্ধারণ করে দেয়।
এই ভোটাভুটি সপ্তাহ বা মাসব্যাপী হতে পারে, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সব মন্তব্য এবং আপ ও ডাউন ভোটের ভিত্তিতে একধরনের মানচিত্র তৈরি করে এবং সেটা চলমানভাবে আপডেট করে। স্বাভাবিকভাবেই এই ভোটিং ম্যাপে সমমনা এবং বিপীরতমনা গোষ্ঠীগুলো দ্রুত আবির্ভূত হয়, যেখানে দেখা যায় যে কোথায় বিভাজন আছে এবং কোথায় ঐকমত্য রয়েছে। আগের মন্তব্যকারীরা এবং নতুন মন্তব্যকারীরা পরে স্বাভাবিকভাবেই এমন মন্তব্য তৈরি করার চেষ্টা করে, যা বিভাজনের উভয় দিক থেকে ভোট জিতবে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে জনপরিসরের বিভাজনগুলো দূর হয়ে যায়। বেশি ভোটে জেতা শীর্ষ মতামত বা মন্তব্যগুলো নিয়ে তখন জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আমলারা গতানুগতিক বা লাইভে বিতর্ক বা আলোচনা করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ামাফিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।
উবার বিষয়ে সরকারি নীতিমালা কী হবে, তা নিয়ে তাইওয়ানে হাজার হাজার মতামত থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাতটি শীর্ষ মতামত উঠে আসে, যা থেকে নীতিনির্ধারকরা এক মাসের মধ্যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। মোটা দাগে দেখতে গেলে, এই সামাজিক টেকনোলজিনির্ভর প্রক্রিয়া শুধু স্বচ্ছ আর অন্তর্ভুক্তিমূলকই না, গতানুগতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে একটা দক্ষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে সৃষ্ট সামাজিক বিভাজন রেখাগুলো এই টেকনোলজির উভয় দিকের ভোটে জিতার এ amefication অ্যালগরিদমের মাধ্যমে ‘মধ্যপন্থি মতামত’গুলো শীর্ষস্থানে তুলে ধরে। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে আমজনতাকে সমতার ভিত্তিতে তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নীতিমালা তৈরিতে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের একটা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে, যা সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে ।
ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতনের পর নতুন যে বন্দোবস্তের কথা বলা হচ্ছে, সেটাতে সব অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং সব মত-পথের সংমিশ্রণ জরুরি। কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে মতৈক্যে পৌঁছানোর ঘটনা শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো উপমহাদেশেই বিরল। আমরা যদি সত্যি পুরোনো বন্দোবস্ত থেকে নতুন বন্দোবস্তে রূপান্তর চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। তাইওয়ানের তরুণরা এক যুগ আগে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেভাবে ডিজিটাল ডেমোক্রেসির প্রবর্তন করেছিল, বাংলাদেশের তরুণরাও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে এ দেশের সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল ডেমোক্রেসির গোড়াপত্তন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।
লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ডাটা সায়েন্স
কার্ডিফ মেট্রোপলিটান বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন