প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনের নানারকম বিভক্তি ও বিকেন্দ্রীকরণ থাকে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো সাধারণত ‘এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা’ বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা শাসিত হয়। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো বিশাল দেশ শাসনে অনিবার্যভাবেই ভৌগোলিক বিভক্তি ঘটে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একক ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং বহুধাবিভক্ত রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকার ব্যবস্থা বলে। উভয় ব্যবস্থাতেই স্থানীয় সরকার বা সর্বনিম্ন শাসন ইউনিটের বিভক্তি রয়েছে।
স্থানীয় শাসন সেই ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ছোট ছোট অংশ একরকম স্বাধীনভাবেই পরিচালিত হয়। এই স্বাধীনতা মানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, বরং রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন বিভক্তি থেকে একটু স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও হস্তক্ষেপপ্রবণতা রোধ করে নিজ গতিতে চলা। তবে জাতীয় সরকারের মতো জনপ্রতিনিধিত্বই স্থানীয় সরকারের প্রাণ। স্থানীয় সরকার যতটা দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ হবে, তৃণমূল মানুষের সুখ-সুবিধা ততই নিশ্চিত হবে।
তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করে কেন্দ্র ও স্থানীয় নেতৃত্বের সম্পর্কের ওপর। জাতীয় সরকারের চেয়ে স্থানীয় সরকার কোনো কোনো কারণে নাগরিক সাধারণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রথমত, স্থানীয় সরকারকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে বিবেচনা করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ের হওয়ার কারণে রাজনীতির হাতেখড়ি এখান থেকেই শুরু হয়। পরিবার যেমন শিক্ষা-দীক্ষা দেয়, সেটি প্রস্ফুটিত হয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের মতো স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার মাটি ও মানুষের কাছাকাছি হওয়ায় নাগরিক সেবা ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্রই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও ত্রাণ কার্যক্রমকে স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।
দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এর বিপরীতটি, অর্থাৎ উপরমুখী কেন্দ্রিকতা ঘটে। একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বদলির জন্য যদি তাকে ঢাকা আসতে হয়, তাহলে এর চেয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আর কী থাকতে পারে! বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রাথমিক প্রায়োগিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তপোক্ত হতে থাকে। তৃতীয়ত, বৈষয়িক ও ভৌতিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই অধিকতর কার্যকর। কারণ কোথায় রাস্তা হবে, আর কোথায় ব্রিজ হবে, এ সম্পর্কে স্থানীয় নেতৃত্বের চেয়ে অন্য কারও ভালো ধারণা থাকার কথা নয়।
অথচ এদেশে উন্নয়ন আরোপ করা হয়। অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকর অবকাঠামো অব্যবহৃত হওয়ার সচিত্র প্রতিবেদন পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বাজেট প্রণীত হলে এই অপচয় ও অন্যায় হতে পারবে না। চতুর্থত, স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা নিয়ে আরও বলা যায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পঞ্চমত, স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে নাগরিক সাধারণের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, যা রাজনৈতিক কর্মসূচি বা রাজধানী থেকে আদেশের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না।
পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারকেন্দ্রিক কমিউন ব্যবস্থাকে উত্তম মনে করা হয়। পৃথিবী গণতান্ত্রিকভাবে যতই এগুচ্ছে, ততই স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় স্থানীয় সরকারের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব ক্রমেই স্থানীয় সরকারের হাতে অর্পিত হচ্ছে। ষষ্ঠত, স্থানীয় সরকারের হাতে দায়িত্ব থাকলে স্থানীয় সম্পদ-সুবিধার যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব। এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিগত ও বেসরকারি তথা এনজিও সহযোগিতার দ্বারা স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। আর এভাবেই আধুনিক বিশ্বে স্থানীয় সরকার ‘অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত শৃঙ্খলা নিশ্চিত করছে (Jonathan Bradbury: 2001, 314)।’
উপনিবেশ-পরবর্তী এতদঞ্চল তথা বাংলাদেশে আর সব ভঙ্গুর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতো স্থানীয় সরকার পর্যায়ও কোনো নিশ্চিত প্রাতিষ্ঠানিকতা গড়ে ওঠেনি। তাই এখন ৫৩ বছর পর রাষ্ট্র সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার সংস্কারের কাজও এগিয়ে চলেছে। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘উন্নয়নশীল উন্নত দেশে উত্তরণের উপযোগী উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি-সহায়ক স্থানীয় শাসন কাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাপক আধুনিকায়ন প্রয়োজন।’ তারা এরই মধ্যে ছয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
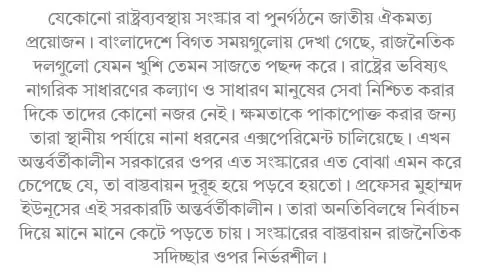
প্রথমত, প্রশাসনিক, আর্থিক এবং স্থানীয় শাসন ও সরকারের সঠিক সমন্বয় ও সংহত করার জন্য বহু স্তরীয় স্থানীয় সরকারের স্তর ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা হ্রাস করা। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকারের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি পৃথক আইন, পাঁচটি ভিন্ন ও পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর অবসান ঘটিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি একক আইন বা মাদার ল তৈরি করা। তৃতীয়ত, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে আরও কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার স্বার্থে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা।
কমিশন একে বলেছে, ‘রাষ্ট্রপতি আদলের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকার কাঠামো’। চতুর্থত, বর্তমান নারী মেম্বার নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে আবর্তন পদ্ধতি প্রবর্তন। আমার কাছে বিষয়টি একটু জটিল মনে হয়েছে। এ ব্যবস্থায় সারা এলাকায় নারীরা পর্যায়ক্রমে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবেন। কমিশনের বক্তব্য পুরুষ ও নারী একই ওয়ার্ডে যে সংঘাত এতদিন বিদ্যমান ছিল, তা আর থাকবে না।
পঞ্চমত, আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ এই কমিশন করেছে। আর তা হলো একক তফসিলে সব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন। এ ব্যবস্থাটি ব্যয়সাশ্রয়ী, সময়সাশ্রয়ী ও সহজতর হয়ে পড়বে। অনেকেই মনে করেন, এই সুপারিশটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি করা সম্ভব হলে অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন নিয়ে যে দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যবস্থায় তার অবসান ঘটবে। ষষ্ঠত, গ্রামীণ পৌরসভাগুলোর বিলুপ্তি। অতীতে শহর নয়, অথচ শহর বানানো হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে এগুলোর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।
যেকোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার বা পুনর্গঠনে জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিগত সময়গুলোয় দেখা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলো যেমন খুশি তেমন সাজতে পছন্দ করে। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক সাধারণের কল্যাণ ও সাধারণ মানুষের সেবা নিশ্চিত করার দিকে তাদের কোনো নজর নেই। ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা স্থানীয় পর্যায়ে নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে। এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর এত সংস্কারের এত বোঝা এমন করে চেপেছে যে, তা বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে পড়বে হয়তো।
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের এই সরকারটি অন্তর্বর্তীকালীন। তারা অনতিবিলম্বে নির্বাচন দিয়ে মানে মানে কেটে পড়তে চায়। সংস্কারের বাস্তবায়ন রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। সেটি এখনো এবং তখনো। রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য ব্যতীত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু করার সুবিধা ও অধিকার নেই। তোফায়েল আহমেদের মতো বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ যতই চমৎকার হোক না কেন, এর নির্ভরতা ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে আগামী নির্বাচিত সরকারের ওপরে। জনাব তোফায়েল চান যে তার সুপারিশগুলো এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়েই সম্পন্ন হোক। সে লক্ষ্যে তিনি জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হতে পারে কি না, সে বিষয়ে এক প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। আর এতেই বেধেছে গোল।
রাজনৈতিক ব্যক্তি, দল ও সিভিল সোসাইটি বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এটি ‘ডিম আগে নাকি মুরগি আগে’ এরকম জটিল ও কুটিল বিতর্ক নয়। যারা আগামী নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন চান তাদের অনেক যুক্তি; আবার জাতীয় নির্বাচনের পর স্থানীয় নির্বাচন চান যারা তাদেরও যুক্তি উপেক্ষা করার মতো নয়। সুতরাং বিষয়টি আন্দোলিত করছে রাজনৈতিক মহলকে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস যখন বললেন, জাতীয় নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার, তখন আলোচনাটি সরগরম হয়ে ওঠে।
এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি মতে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থানীয় নির্বাচন করতে চাইলে তা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই করতে হবে। এটি করতে গেলে নির্বাচিত সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার সুযোগ পাবে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এই যে, প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি পার্টিকে বলা হচ্ছে: ‘Government is waiting.’ পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় এটি একটি বাস্তবতা। খুব সংগতভাবেই বিএনপি চাইবে তাদের নেতৃত্বেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। তাতে সরকার গঠনের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক হবে।
বিএনপির রাজনৈতিক সমর্থন ও শক্তি আরও সংহত হবে। তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপির নেতৃত্বের মধ্যেও এই আশাবাদ যে, বিগত ১৭ বছরে তারা যে নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, স্থানীয় সরকার পর্যায়ের নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের হারানো গৌরব উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু এখনই অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের আগে যদি স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তারা সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—‘এরকম ক্রিটিকাল সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া অন্য নির্বাচন করার চিন্তাটা আসে কোত্থেকে?’ এ সময়ে জামায়াত-বিএনপি দ্বন্দ্ব-বিভেদের মৃদু বিতর্ক শোনা গেলেও আসলে তারা একমত। সেটির প্রমাণ মেলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে তাদের মতামতে। প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, জামায়াত সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানটি উত্তম মনে করছে। তাদের শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সে সরকার স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। এটা যদি না হয়, স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীদের পক্ষে-বিপক্ষে যে লড়াই শুরু হবে, সেটি অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।
সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে ৬৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ জনগণ চায় জাতীয় সরকারের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। আর এর বিপক্ষে ২৯ শতাংশ জাতীয় সরকারের পর স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী। এরই মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণ সংহতি আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন চরমোনাই এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পক্ষে জোরালো মতামত প্রকাশ করেছে।
এছাড়া গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, ‘সরকাররে কাজে গতি আনার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আহ্বান জানাচ্ছি।’ প্রকাশিত জরিপে সরকারের ইচ্ছার ইঙ্গিত রয়েছে, এমন কথাও বলা হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র এখন একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করছে। জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম-গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সময় হলে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে তাতে বড় কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় নির্বাচনের আগে বা পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মজবুত হবে। আমরা গণতন্ত্রের যুদ্ধে পরাজিত হতে চাই না।
এমবি
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

