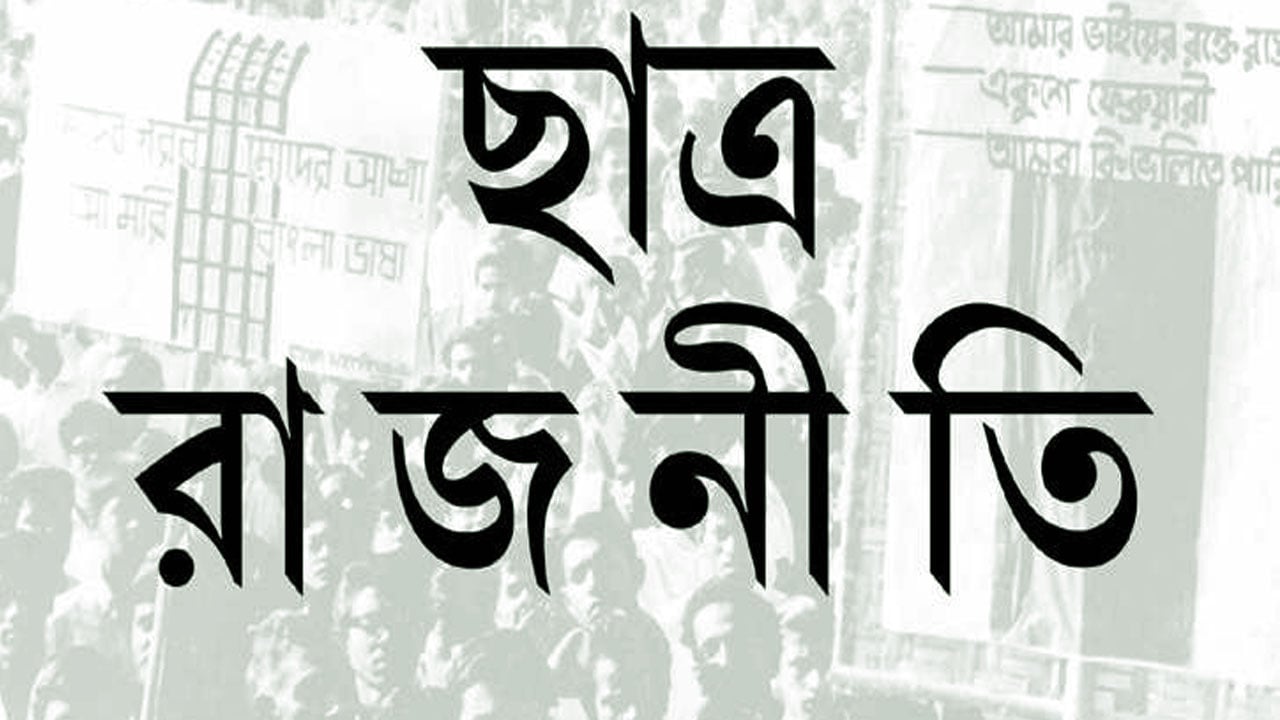দীর্ঘসময় ক্যাম্পাস দখলে রাখা ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে। অবসান ঘটেছে ক্যাম্পাসে তাদের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অত্যাচারেরও। এখন তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। সংগঠনটি আসলে ছাত্ররাজনীতি করত কি না সেটাই সব সময় আমাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন ছিল। ভাবতাম এটাকে ছাত্ররাজনীতি বলে কি না? পরে জাতীয় রাজনীতি দেখে মনে হয়েছে, তারা তাদের জায়গায় হয়তো ঠিকই আছে, কেননা সরকার তাদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। এর আগে যারা দেশ চালিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে ২০১৮ সালের কোটা আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান কোনোটিই কোনো দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে হয়নি। বরং ২০১৮ সালে যখন কোটাবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, তখন ছাত্রসংগঠন বিশেষ করে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের আচরণ আমরা দেখেছি। একটা ছাত্রসংগঠনের হেলমেট বাহিনীতে পরিণত হওয়া নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনা নয়। ২০২৪ সালে এসেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাদের সেই ভয়াবহ চেহারা।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোনো যৌক্তিক আন্দোলনে বড় ছাত্রসংগঠনগুলোর দেখা মেলে না। ছাত্রদের স্বার্থরক্ষায় তাদের কোনো অবস্থান বা সমর্থন নেই। যখন সেই স্বার্থটা তাদের মূল দলের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়, শুধু তখনই ছাত্রসংগঠনগুলো সেই আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেয়, যেমনটা আমরা বিরোধী দলের ছাত্রসংগঠনগুলোর দেখেছি। ছাত্রসংগঠন সেটা হোক সরকারি দলের কিংবা বিরোধী দলের, তাদের মূল কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা।
বলা বাহুল্য, ১৯৫২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত কোনো যৌক্তিক আন্দোলনই কোনো রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিক ছাত্রসংগঠন শুরু করেনি। ২০২৪ সালের ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ও কোনো রাজনৈতিক ব্যানারে হয়নি। বরং দলীয় সংগঠন এই ইস্যুতে কোনো কর্মসূচি দিলে তা সফল হতো না। এতে এটা প্রমাণিত হয়, লেজুড়বৃত্তিক ছাত্রসংগঠনের রাজনীতি ভালো কিছু বয়ে আনতে পারছে না। যখনই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আন্দোলন করার প্রয়োজন হয়েছে, তখনই সাধারণ ছাত্ররাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই আন্দোলনে। তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে নতুন নেতা। ১৯৫২ থেকে ৭১ এবং ১৯৯০ থেকে সর্বশেষ ২০২৪ সালের আন্দোলনে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবদান অসীম। অন্যদিকে দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্রসংগঠনগুলো শুধু তাদের রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্রসংগঠনগুলো কেন দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে, কিংবা মূল দলের কেন নিজস্ব ছাত্রবাহিনী লাগছে? নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টা বোঝা জটিল নয়। এখানে জটিল কোনো হিসাবনিকাশও নেই। কারণটি হচ্ছে মূলত ক্ষমতায় থাকা। কেউ যেন সরকারের সমালোচনা বা বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস না পায়, সেটা নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে আরো ছোটখাটো কিছু বিষয়ে (চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাণিজ্য, জমি দখল ইত্যাদি) তারা জড়িত তো আছেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর এদের কেন লাগছে? বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য দেশকে ভালোবাসা বা দেশের মানুষের জন্য কাজ করা এমনটা কখনো মনে হয়নি।
বর্তমানে ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা ও কালো টাকার মালিকরা টাকা দিয়ে নমিনেশন কেনেন এবং বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করেন নির্বাচনে জেতার জন্য। বর্তমান রাজনীতির এই বাস্তবতাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বড় দলগুলোতে এই প্রবণতা এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। যারা নমিনেশন কিনে আনেন, তারা দেশের সেবা করবেন কীভাবে? তারা তো নমিনেশন পাওয়ার পেছনে ব্যয় করা টাকা ওঠাতেই ব্যস্ত থাকেন।
আমার নিজের ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচনে দেখেছি, মেম্বার প্রার্থী কমপক্ষে ১০ লাখ এবং চেয়ারম্যান প্রার্থী কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বাজেট রাখেন নির্বাচনে জিততে। পাশের ইউনিয়নে এই অর্থের পরিমাণ আরো বেশি। হিসাব করলে দেখা যায়, নির্বাচিত হওয়ার পর একজন জনপ্রতিনিধিকে যে টাকা সম্মানী সরকারের পক্ষ থেকে দেখা হয়, তাতে খরচের ১০ ভাগের ১ ভাগও ওঠে আসে না। তাহলে তারা এত টাকা খরচ করেন কেন? মূল বিষয়টা এখানেই। রাজনীতিটা তাদের কাছে মূলত টাকা কামানো এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করার একটা মাধ্যম। এখন যাদের মূল উদ্দেশ্য টাকা কামানো এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করা, তাদের কাছ থেকে জনগণ কী সেবা প্রত্যাশা করতে পারেন?
ছাত্রনেতা থেকে বড় মাপের কোনো গবেষক, বিজ্ঞানী হয়েছেন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কষ্টকর। ক্যাম্পাসে দখলদারি, চাঁদাবাজি, নিয়োগ-বাণিজ্য, হল দখল, সিটবাণিজ্য, মারামারি, মাদক ব্যবসাসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া ছাত্রসংগঠনগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো কাজের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা থাকে না। ছাত্ররীতির একটা সুবিধা যেটা নিজের চোখে দেখেছি, ক্যাম্পাসের কয়েকজন নেতা কোটিপতি হয়েছেন রাজনীতি করে। অথচ একটা সময় তাদের তেমন কিছুই ছিল না। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে আছে বিনামূল্যে ক্যান্টিনে খাওয়া, সবার কাছ থেকে সালাম আদায় করা, সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় হাজার গুণ আরাম-আয়েশে থেকে হলে থাকা, পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন করে পাস করা, ভর্তিবাণিজ্য ইত্যাদি।
এসব করতে গিয়ে তাদের আসল কাজ অর্থাৎ লেখাপড়া পড়ে হুমকিতে। অনার্স-মাস্টার্স শেষ করতে লেগে যায় এক যুগেরও বেশি সময়। এ কারণে ৩৫-৪০ বছর বছর বয়সেও একজনকে ছাত্রসংগঠনের সভাপতি-সম্পাদক পদে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা পাস করেন। আমার ক্যাম্পাসে এক নেতাকে তার ফ্যাকাল্টি পরিবর্তন করে বিশেষ বিবেচনায় অন্য ফ্যাকাল্টিতে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এখন আবার দেখছি অন্যদের জন্যও বিশেষ বিবেচনার দ্বার খোলা হচ্ছে।
ক্যাম্পাসে তাদের রাজনীতি করার একটাই উদ্দেশ্য কোনো না কোনোভাবে টাকা কামানো। টাকা না কামানো গেলে এত লাখ লাখ টাকা দিয়ে তারা কমিটি আনত না। আমার ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগ নেতাকে অল্পদিনেই কোটিপতি হতে দেখেছি। হলপ করেই বলতে পারি, যারাই পরে ক্ষমতায় আসবে, তাদের ছাত্রসংগঠনের নেতারাও একই কাজ করবেন। হয়তো আগের মতো সমানমাত্রায় পারবেন না, তবে করবেন বলেই ধরে নিতে পারি। কিছুটা নমুনা ইতোমধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে ঢাকার বাইরের ক্যাম্পাসগুলোয়।
বড় দলগুলোর ছাত্রসংগঠন প্রকৃত অর্থে ছাত্রদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করে না। অনেকেই বলেন, ছাত্ররাজনীতি করা মানুষের মৌলিক অধিকার, যা সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। তবে রাজনীতি না করাও আমার মৌলিক অধিকার। তা যদি হয়, তবে আমাকে কেন মিছিলে যেতে বাধ্য করা হয়? কেন রাজনীতি না করলে হলে সিট পাওয়া যায় না? সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও আমার সিট পাওয়ার অধিকারের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে না।
বাস্তবতা হলো, গতানুগতিক রাজনীতি আর এখন চলবে না। এটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। উন্নত দেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ আছে, তবে নেই লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি। ফলে সেখানে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশে কেন হচ্ছে না, তা নিয়ে ভাবতে হবে।
লেখক : শিক্ষার্থী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন