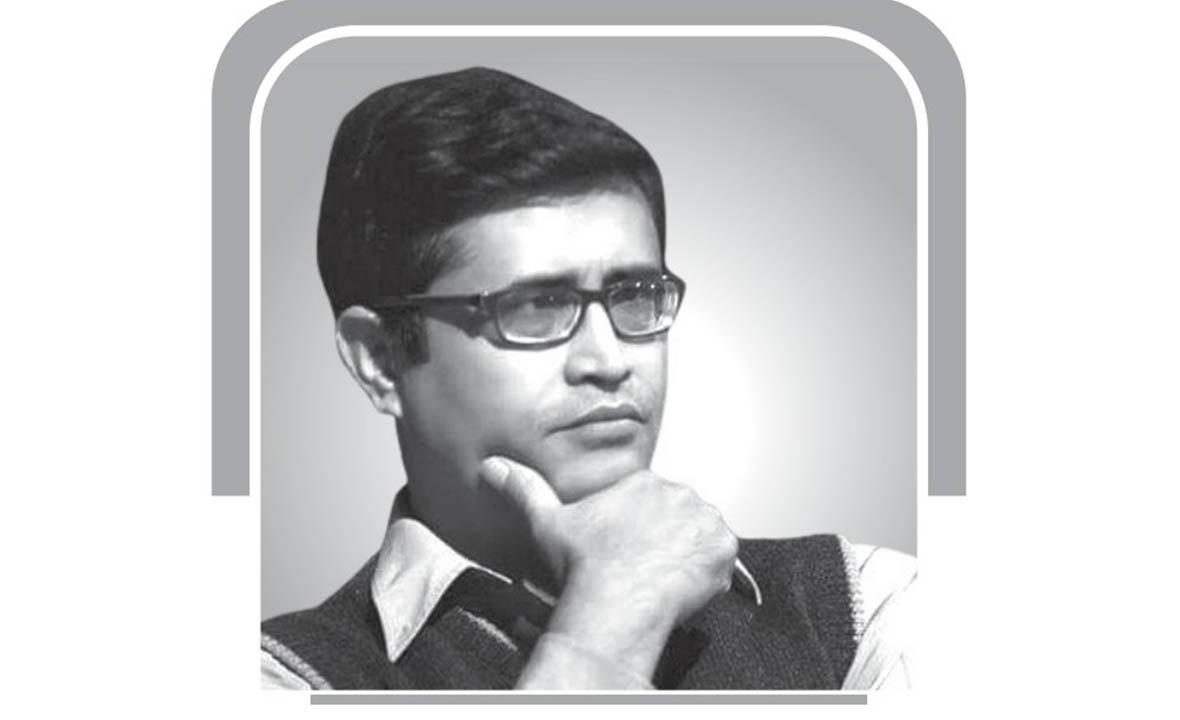খুব অস্থির হয়ে আছি। শুধু আমি নই। দেশে, সমাজে, একালে যারা বাস করছেন তারা সবাই অধীর। পরিস্থিতি অস্থির। সময় অধীর। কী হয়, কী হয় শঙ্কা চারদিকে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার এক ঝড়ো অভ্যুত্থানে হাসিনার ফ্যাসিস্ট রেজিম পড়ে যায়। কিন্তু সে অভ্যুত্থান ছিল এক অসমাপ্ত বিপ্লব। কায়েমি রাজনীতি ছিল হাসিনার বিদায়েই তুষ্ট। তারা দ্রুত নির্বাচনে ক্ষমতায় যেতে অধীর। কিন্তু ছাত্র-তরুণরা বিদ্যমান রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও ঘুণে ধরা রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলে ফেলার পক্ষে। এই দুপক্ষের ও দুই মতের মধ্যে আজতক কোনো সমঝোতা হয়নি। ফ্যাসিবাদ পতনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা ঐক্যসূত্র ছিন্ন করে সবাই ফিরে গিয়েছে যে-যার বৃন্তে। অস্থিরতার এ এক বড় কারণ।
মানুষের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জনমতও এখন আর স্পষ্ট নয়। কমবেশি অস্থির, বিভ্রান্ত, দিকভ্রান্ত যেন সবাই। প্রচার-অপপ্রচারের কুঞ্ঝটিকায় সত্যকে চিনে নেওয়া এখন ভারী কঠিন হয়ে পড়েছে। একজন যাকে হরিত বলছে, অপরজন তাকেই বলছে লাল। একের বয়ানে পরম দেশপ্রেমিক, অপরের গালাগালিতে হয়ে যাচ্ছে চরম দেশদ্রোহী। সকালের বিপ্লবী সন্ধ্যায় চিত্রিত হচ্ছে বেঈমান অভিধায়।
২০০৪ সালে একটা বই বেরিয়েছিল। আমেরিকান লেখক-সাংবাদিক র্যাল্ফ কীসের লেখা। বইয়ের নাম : ‘দ্য পোস্ট-ট্রুথ এরা’। এর বাংলা তরজমা কী হবে তা নিয়ে ভেবেছি অনেক। পরে একটা কঠিন অনুবাদ দাঁড় করিয়েছি মনে মনে। সেটা হলো ‘সত্যোত্তরকাল’ কিংবা ‘সত্য-পেরোনো সময়’।
এই পোস্ট-ট্রুথ এরা বলতে এমন একসময়কে বোঝায়, যেখানে জনমত গঠন ও রাজনৈতিক বিতর্কের ক্ষেত্রে আবেগ ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আবেদনের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের গুরুত্ব কম। ব্রেক্সিট ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি ২০১৬ সালে ‘পোস্ট-ট্রুথ এরা’ শব্দবন্ধকে বর্ষসেরা শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর তখন থেকেই এই কনসেপ্ট বা ধারণা প্রবল গুরুত্ব অর্জন করে।
এই সত্যোত্তরকালের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে : ১. তথ্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস। অনেক ক্ষেত্রে আবেগাক্রান্ত বয়ানের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যকে খারিজ করা কিংবা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২. মিসইনফরমেশন ও ফেক নিউজের বাড়বাড়ন্ত। অনলাইন ও মূলধারার মিডিয়ায় ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ছড়াছড়িতে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অনাস্থার এক পরিবেশ তৈরি হয়। ৩. মেরূকরণ বেড়ে যাওয়া। জনগণ তাদের চলমান বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে এমন তথ্যেই খুব বেশি প্রভাবিত হওয়ায় জনসমাজে দেখা দেয় মোটা দাগের বিভাজন। ৪. প্রাতিষ্ঠানিকতার ওপর আস্থায় ধস। ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া, এক্সপার্ট ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থার ঘাটতি পোস্ট-ট্রুথ আবহের দিকে ঠেলে দেয়। ৫. সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদম এবং প্ল্যাটফরমগুলো ভুল তথ্য এবং ইকো চেম্বারগুলোর আরো বিস্তার ঘটাতে পারে। এতে জনমত আরো বিকৃত হতে পারে।
পোস্ট-ট্রুথ এরার তিনটি বড় কুফল হচ্ছে : ক. গঠনমূলক সংলাপে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া। খ. মিসইনফরমেশনের বিস্তার ও পোলারাইজেশনের কারণে ব্যাপক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সামাজিক বিভাজন দেখা দেওয়া এবং গ. মিসইনফরমেশনের মাধ্যমে জনমত ম্যানিপুলেট করায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।
‘চব্বিশের জুলাই-আগস্টে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল, তা ছিল বহু বছরের অসন্তোষ, বঞ্চনা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই অভ্যুত্থান বিপ্লবে উন্নীত হতে পারেনি। ফলে বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে যায়। দেশ এক সামাজিক অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির আবর্তে প্রবেশ করে, যার সঙ্গে ভয়াবহভাবে মিশে যায় ‘পোস্ট-ট্রুথ সিন্ড্রোম’ নামক এক আধুনিক ব্যাধি।
‘চব্বিশের অভ্যুত্থান শুধু রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধেই ছিল না, বরং এটি ছিল একটি বৈষম্যমূলক, কেন্দ্রায়িত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। তরুণসমাজ, বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এটি রূপ নিয়েছিল এক গণ-জাগরণে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের, বিশেষ করে ডিপ স্টেটের অনীহা, নেতৃত্বহীনতা এবং উদ্দেশ্যবিচ্যুতি সেই বিপ্লবকে অসম্পূর্ণ রেখেছে। পরিবর্তনের আশা যেভাবে জেগেছিল, তা আকস্মিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়-সঙ্গে রেখে যায় এক গভীর হতাশা এবং বিশ্বাসহীনতা।
এই অস্থিরতার সময়েই এক নতুন সংকট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে পোস্ট-ট্রুথ সিন্ড্রোম। এ এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে সত্য নয়, বরং আবেগ এবং ব্যক্তি-চিন্তার বশবর্তী ‘বিকল্প বাস্তবতা’ প্রাধান্য পায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার এবং প্রোপাগান্ডা হয়ে ওঠে ক্ষমতার নতুন অস্ত্র। মানুষ এখন সত্য যাচাইয়ের চেয়ে তাদের মনে লালিত বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেয়। অনেক সময় সেই বিশ্বাস গঠিত হয় গুজব, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ও বিভ্রান্তির ওপর ভিত্তি করে।
একদিকে অসমাপ্ত বিপ্লবের হতাশা, অন্যদিকে পোস্ট-ট্রুথ সিন্ড্রোমের বিশৃঙ্খলা-এই দুইয়ে মিলে দেশে, সমাজে ও রাজনীতিতে একটি দ্বিমুখী সংকট সৃষ্টি করেছে। মানুষ হয়েছে দিকভ্রান্ত, নেতৃত্বহীন আর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। যার ফলে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়, রাজনৈতিক অনাস্থা এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস আরো গভীরতর হয়েছে।
একসময় আমাদের মধ্যে সত্য এবং মিথ্যা ছিল। এখন আমাদের কাছে সত্য-মিথ্যা ছাড়াও এমন ভার্শন আসে, যা সত্য নাও হতে পারে কিন্তু আমরা ওই মিথ্যা বলাটাকেই খুব স্মার্টনেস বলে মনে করি। এটি হলো সত্য-পরবর্তী যুগ। সত্য-পরবর্তী যুগে সত্য এবং মিথ্যা, সততা এবং অসততা, কল্পকাহিনি এবং অ-কল্পকাহিনির মধ্যকার সীমানা ঝাপসা হয়ে যায়। অন্যদের প্রতারণা করা একটি চ্যালেঞ্জ, একটি খেলা এবং শেষ পর্যন্ত একটি অভ্যাসে পরিণত হয়। কখনো কখনো সত্য-পরবর্তীকে একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়, যেখানে নাগরিক বা দর্শক এবং রাজনীতিবিদরা আর সত্যকে সম্মান করেন না বরং শুধু তারা যা বিশ্বাস করেন বা অনুভব করেন, তাকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন।
বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী রেজিম প্রতিষ্ঠার আগে শেখ হাসিনাই এই পোস্ট-ট্রুথ সিন্ড্রোম প্রবর্তন করেছিলেন। তবে সেটা ছিল একমুখী এবং এককেন্দ্রিক। শুধু হাসিনার সমর্থক ও অনুগতদের অধিকার ছিল অপতথ্য, মিথ্যা তথ্য ও বিকৃত তথ্য ছড়ানোর। তাদেরই শুধু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিকৃত জনমত গড়ে তোলার। বিভেদ, বিভাজন, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দেওয়া ছিল তাদের মোক্ষম অপকৌশল। বাকি সবাইকে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে ও সন্ত্রাসী কায়দায় অবদমিত করে রাখা হতো।
হাসিনা রেজিমের পতনের পর পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তি ছাড়া বাকি সবার জন্য বিধিনিষেধের অর্গল খুলে গেছে। এখন তারা প্রায় সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে অবাধে পোস্ট-ট্রুথ কনসেপ্ট প্রয়োগ করতে নেমে পড়েছে। যাদের ডেক্সটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবে ইন্টারনেট সংযোগ আছে, তারা তো বটেই, নিদেনপক্ষে যাদের হাতে একখানা স্মার্টফোন আছে, তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অপপ্রচার-যুদ্ধে। স্বাধীনতার এই অবাধ চর্চায় গড়ে উঠছে বিকৃত জনমত। বিভেদ-বিভাজন বাড়ছে। ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত হচ্ছে সবাই। দলবাজি এক ধরনের বিকারগ্রস্ততার রূপ নিয়েছে। সমালোচনার স্থান দখল করেছে কুৎসা, নিন্দা, মিথ্যা দোষারোপ, চরিত্রহনন ও নোংরা গালাগাল। অসহিষ্ণুতা, উত্তেজনা, ক্রোধ-সংঘাতে রূপ নিচ্ছে। সামাজিক স্থিতি, জাতীয় নিরাপত্তা, সংহতি এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পড়েছে প্রবল ঝুঁকির মুখে। স্বাভাবিক রাষ্ট্রপরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শান্তিপ্রিয় উৎকণ্ঠিত নাগরিকদের কেউ কেউ ইতোমধ্যে এর চেয়ে পতিত ফ্যাসিবাদীকেই ‘বেটার অপশন’ বলে ভাবতে শুরু করেছে। শুধু ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তির তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ কিংবা একটি নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই এই গুরুতর রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের নিরসন হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয় না।
সমাজে ও রাষ্ট্রে যে বিপ্লব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জনসমাজে তৈরি হয়েছে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তরুণসমাজের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে, তার সুরাহা করতে হবে সবাই মিলে। নতুবা অগ্নিগিরিকে ছাইচাপা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখার উদ্যোগ আরো অনেক বড় বিপর্যয় ঘটানোর মাধ্যমেই ব্যর্থ হবে।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক
ই-মেইল : mrfshl@gmail.com
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন