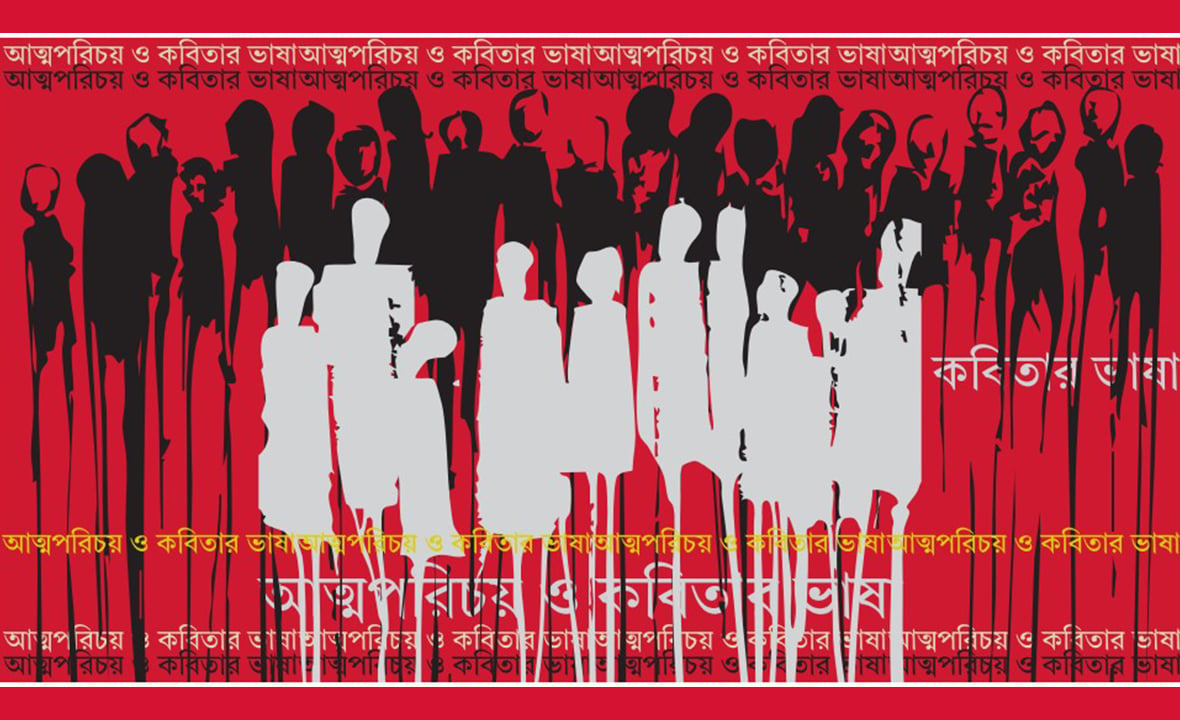আত্মপরিচয়হীন অনিকেত মানসিকতা আধুনিক কবিতার মূলমন্ত্র। আধুনিক কবিও তাই বোদলেয়ারের ‘প্যারিস সপ্লীন’-এ উল্লিখিত ‘অদ্ভুত অচেনা মানুষ’। বোদলেয়ার তাই ঘোষণাও করেছিলেন-“কবি কোনো ‘কাজে লাগেন’ না, যে বায়রনি বিদ্রোহের দিন গত হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ; প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার করে নিতে হয়, অতএব একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন।” বুদ্ধদেব বসুর ‘বোদলেয়ার ও তার কবিতা’র ভূমিকা থেকে আমরা এসব জানতে পারি। কিন্তু বিপ্লব কিংবা অভ্যুত্থানের সমর্থক হলে কবিকে এই আত্মরোমন্থনের বাইরে আসতে হয়। গণমুক্তি বা জনআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নেই বিপ্লব অনুপ্রাণিত। ফলে দ্রোহ যখন সফল হয়, তখনই তা বিপ্লব বা অভ্যুত্থান।
কবি যখন রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিপক্ষে দ্রোহী হয়ে ওঠেন, তখন এই গণসম্পৃক্ততা তার আত্মপরিচয়কে আরো বেশি মানবিক ও মহিমান্বিত করে তোলে। আধুনিকতার সেই ‘স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন’ অতিক্রম করে তিনি তার কবিতায় বিদ্রোহের দিনকেই বরং আগত সম্ভাবনা হিসেবে দেখেন। তখন তার বিবেচনায় থাকে মানুষ। আত্মপরিচয়ের জাতিগত অবস্থানকে তিনি নিশ্চিত করতে চান। যদিও সব জাতিবাদ ডিঙিয়ে বৃহত্তর মানবিকতায় পৌঁছতে চায় তার কাব্য। আধুনিকতার নন্দনতত্ত্ব তখন আর নিরঙ্কুশ সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না। কেননা এসব দ্রোহী কবিতা প্রমাণ করে কবিও কাজে লাগেন এবং কবিতারও একটা প্রায়োগিক মূল্য আছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং অভ্যুত্থানে সংযুক্ত হয় আপামর জনগণ। শিল্প-সাহিত্যেও সেই পরিবর্তনের গণঅভিপ্রায় নান্দনিক স্পর্ধা নিয়ে জারি থাকে।
মাহমুদ দারউইশ নিজের এক কবিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেনÑ আমি তুলে ধরি ‘সম্মিলিত স্মৃতিকে’। এই সম্মিলিত স্মৃতি আসলে ফিলিস্তিনের মাটি ও মানুষের পারম্পর্য। তিনি যে আরব রক্তের অংশীদার সেই জাতিসত্তার উজ্জীবনের মধ্য দিয়েই তিনি ফিলিস্তিনের মানুষ তথা গোটা মানব জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যাচাই করেছেন তার কবিতায়। ‘পরিচয়পত্র’ কবিতায় লিখেছেন-
‘লিখে রাখো
আমি এক আরব,
আমার পরিচয়পত্রের নম্বর পঞ্চাশ হাজার
আমি একজন আরব
শ্রমসঙ্গীদের সঙ্গে আমি পাথরখনিতে কাজ করি
আমার আটটি সন্তান
এই পাথরের শ্রম থেকেই আমি তাদের রুটিরুজি, বই-খাতা ও জামা-কাপড় দিই
তবু তোমাদের দরজায় ভিক্ষা চাই না
নতজানু হই না তোমাদের দোরগোড়ায়।’
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স আবার উত্থাপিত হচ্ছে। নতুন যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা শোনা যাচ্ছে, সেখানে হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠবার প্রয়াস পাবে বাঙালি মুসলমান। ইতিহাসের নিগূঢ় সত্য ঘেঁটে সেই প্রয়াস ও প্রচেষ্টাকে যৌথ পরিচয়ের মধ্যে নিষ্পন্ন করার দায়িত্ব কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের। সেই ডিসকোর্স বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্বকে আলাদা আইডেন্টিটিতে স্থাপন করবে না; বরং একাকার করে ভাববে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারÑ এই তিন মূলমন্ত্র বাহাত্তরের সংবিধানে রাখা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যে কালচারাল হেজিমনি চেপে বসেছিল আমাদের ওপর, চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সহুল আহমদ সম্পাদিত ‘অরাজ’ অনলাইন পত্রিকায় ১২ আগস্ট ২০২০ সংখ্যায় ‘সেক্যুলারিজম, উপনিবেশ ও রাষ্ট্র’ শিরোনামে জাহিদুল ইসলাম একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার আলোচনায় উঠে এসেছেÑ প্রখ্যাত তাত্ত্বিক তালাল আসাদ দেখিয়েছেন সেক্যুলারিজম শব্দটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে পশ্চিমা মুক্তচিন্তকরা ব্যবহার করেন। শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল, যেন তারা নাস্তিক উপাধি থেকে নিষ্কৃতি পান। খ্রিস্টান সমাজের সঙ্গে এক ধরনের স্থিতিশীল সম্পর্কের জন্য যা প্রয়োজন ছিলো। সেক্যুলার রাষ্ট্র ও সমাজ নিজস্ব ধর্ম থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়েছে। লকের প্রাকৃতিক আইনের ধারণাও ধর্মতত্ত্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। লকের মতে, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তিÑ এই তিনটি প্রাকৃতিক অধিকার মানুষের জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ প্রদত্ত এই অধিকার আদি পিতা আদমকে দেওয়া হয়। আমেরিকার সংবিধানে লকের ধারণাটি সম্পৃক্ত করা হয়। দার্শনিক জার্গেন হেবারমাস মনে করেন, ‘মানবাধিকার’, ‘ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ’ ও ‘গণতন্ত্রের’ মতো বিষয়গুলো সরাসরি ইহুদি ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ থেকে ধার করা। কাজেই ধর্মের সঙ্গে সেক্যুলারিজমের একদম বিপরীতধর্মী সম্পর্ক নেই। বরং সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপার। সেক্যুলারিজম যৌক্তিক, ধর্ম অযৌক্তক; সেক্যুলারিজম উদার, ধর্ম অনুদারÑ এভাবে দুটি বাইনারিতে ভাগ করা বিপজ্জনক। যে কাজটি তথাকথিত পশ্চিমা আলোকায়নের সময় হেগেল বা কান্টের মতো দার্শনিকরা করে গিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে।
বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে একই ধরনের বাইনারি অপজিশন কার্যকর রাখা হয়েছিল। হয় বাঙালি নতুবা মুসলমান। বাঙালি হতে গেলে মুসলিম কালচারাল হেরিটেজকে পরিহার করতে হবে। তালাল আসাদ তার ‘ফরমেশন অব দ্য সেক্যুলার’ গ্রন্থে দিখিয়েছেন, ইতালিতে কেউ ক্রস ব্যবহার করলে তা কালচারাল প্রতীক। কিন্তু হিজাব বা বোরকা হচ্ছে ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই সেক্যুলার রাষ্ট্রে হিজাব পরিধানের বিপক্ষে জনমত তৈরি করাটাও বৈধতা পায়। আমাদের দেশে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, প্যাঁচা ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতীক ব্যবহার করে পহেলা বৈশাখে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’য় অংশগ্রহণ আদর্শ বাঙালি কালচার হিসেবে দেখা হতো, স্বৈারাচার আমলে। অথচ দাড়ি-টুপির ব্যবহার, মিলাদ, মোনাজাত, রমজান এবং ঈদে মিলাদুন্নবীর মিছিল মুসলমান ধর্মীয় কালচারের অন্তর্ভুক্ত। বাঙালি মুসলমানকে বিশুদ্ধ বাঙালি হতে গেলে হিন্দুত্ববাদী কালচারাল ন্যারেটিভ মান্য করতে হবে, এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ কবি-লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে সক্রিয় আছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এটি একটি প্রকল্প হিসেবে জারি ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে পূর্ববঙ্গে যখন মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখা গেল, তখনই টনক নড়ে বঙ্কিম চন্দ্রের। বাঙালির ইতিহাস ও বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ক দুটি প্রবন্ধে তিনি দেখান মুসলমানরা আর্য রক্ত বহন করে না। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে। রাজশক্তি ব্যবহার করে মুসলমান শাসকরা ধর্মান্তরিত করেছেন বলে মনে করেন কেউ কেউ। ইংরেজি শিক্ষিত প্রায় প্রত্যেক হিন্দু স্কলার একই মত ব্যক্ত করেন। ইংরেজ স্কলারদের মতামত একটু ভিন্নরকম। তারা মনে করেন, ইসলামের সাম্যনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিষ্পেষিত নিম্নবর্গের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয় বলে মুসলমান আধিক্য দেখা দিয়েছে। যা-ই বলা হোক না কেন, মনস্তাত্ত্বিক হীনম্মন্যতা তৈরি হয় এই ঐতিহাসিক বয়ান থেকে যে, নিম্নবর্ণের রক্ত বহন করছে মুসলমানরা। অথচ ইতিহাসের এই সত্য প্রমাণিত নয়। পুরাণ, মহাকাব্য, কিসসা-কাহিনি ঘেঁটে যে বয়ান তৈরি করা হয়েছে, তা মূলত সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী এবং রমেশচন্দ্রও সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাদের কেউ কেউ মুসলমান শাসকদের ‘দুরাচার’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। লুটেরা ও চতুর ইংরেজরা তাদের কাছে ‘ত্রাণকর্তা’। কেউ আবার চলমান আর্য হিন্দু রাজত্বের প্রকল্পকে ইতিহাসের বয়ান হিসেবে জারি রাখতে চেষ্টা করেছেন। মুশকিল হলো, ঔপনিবেশিক কালপর্ব পার হয়ে এলেও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক কালের মুসলমান লেখক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইতিহাসের এই ভেজাল বয়ান গাঢ়তর প্রভাব রাখতে পেরেছে। তাই আহমদ ছফার ‘বাঙালি মুসলমানের মন’, গোলাম মুরশিদের ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ এবং আনিসুজ্জামানের ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’ বাঙালি মুসলমানকে যেভাবে চিত্রিত করেছে, তা এককথায় নেতিবাচকই। কাজেই সাংবিধানিক মূলনীতি হিসেবে ‘বাঙালিত্ব’ই যখন চেপে বসে, তখন বাংলাদেশের মুসলমান আত্মপরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগবে এবং দ্বিধান্বিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই আল মাহমুদের ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ পাঠ করতে গিয়ে সেক্যুলার ধর্মে দীক্ষিত কোনো কোনো বাঙালি কবির গা রি রি করে ওঠে। কেননা তিনি ‘জেহাদ জেহাদ বলে জেগে’ ওঠার প্রেরণায় লিখেছেনÑ ‘রক্তই সমাধান, বারুদই অন্তিম তৃপ্তি’। মায়ের গল্পের বয়ানে মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজিকে উদ্দেশ করে তিনি লিখেছেন-
‘আল্লার সেপাই তিনি, দুঃখীদের রাজা
যেখানে আজান দিতে ভয় পান মোমেনেরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিলজিদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি।
দ্যাখো, দ্যাখো, জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে। ’
বাঙালির সেক্যুলার ধর্ম এখানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই কবিতাকে মৌলবাদাক্রান্ত মনে করেন তারা। তাদের ভাষ্যমতে, মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি এক নিপীড়ক দখলদার। অথচ ইতিহাস গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ ভিন্ন ফলাফল দিচ্ছে। ১২০০ সাল পর্যন্ত গৌড়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই কালপর্বকে ‘হিন্দু রাজত্ব’ আখ্যা দেওয়া একটি ভুল বয়ান। প্রাচীন কাল থেকে বারো শতক পর্যন্ত পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ছিল বৌদ্ধ রাষ্ট্র। সেনদের আগে কোনো হিন্দু শাসক নিরঙ্কুশ শাসন কায়েম করতে পারেনি। সেনরা ৮০ বছর রাজত্ব করে। এর আগে পালরা শাসন করে সাড়ে ৩০০ বছর। বল্লাল সেনের অত্যাচারে কিছু বৌদ্ধ হিন্দু হয়ে যায়। লেখক, ধর্মগুরু, শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত অনেক বৌদ্ধ নেপালে পালিয়ে গিয়ে বাংলা সাহিত্য চর্চা করেন। তারানাথের ‘ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস’ গ্রন্থের বরাত দিয়ে কেউ কেউ বলেন, নির্যাতিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি দল মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজিকে বাংলা আক্রমণের উসকানি দেয়। তুর্কিরা ক্ষমতায় এলে নির্যাতিত বৌদ্ধরাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। কেননা ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হার ২৫%-৩০% হওয়ার কথা। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭%-৩৮%। বাকি সবাই প্রায় মুসলমান।
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন