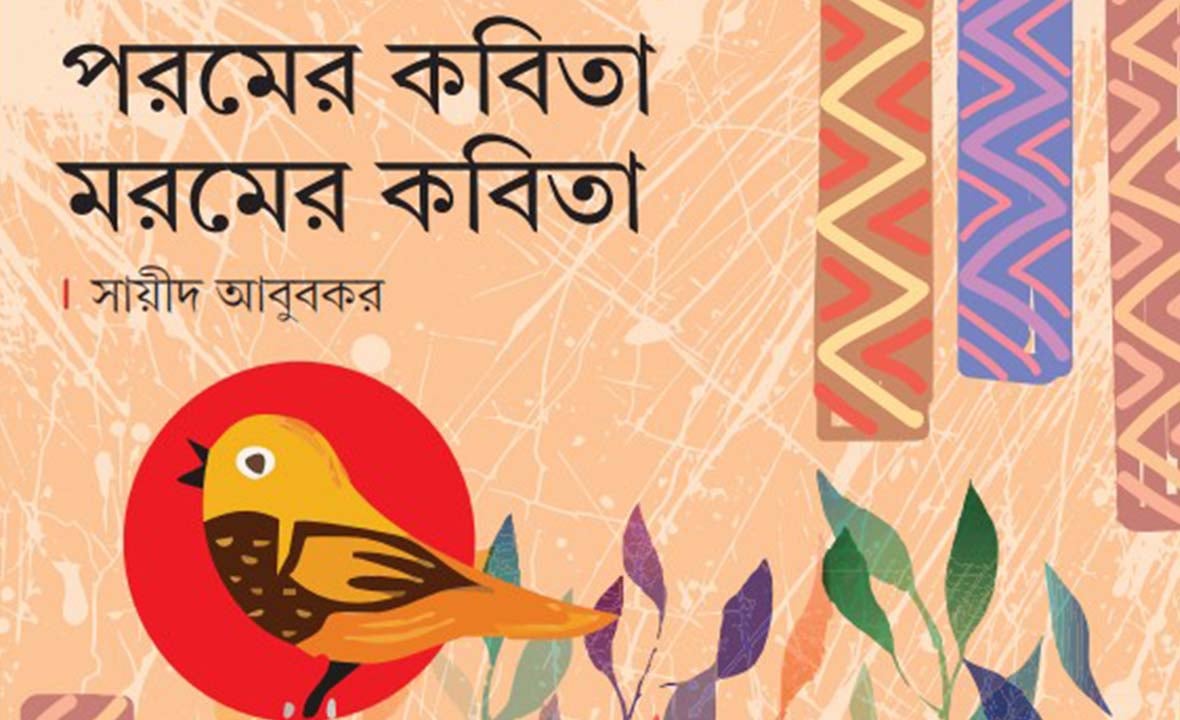সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন সাহিত্য। বহু রাজা ও রাজ্য হারিয়ে গেছে, কেবল টিকে আছে তার সাহিত্য। গ্রিক সভ্যতার শৌর্য-বীর্য বিলীন হয়ে গেছে অতীতের অন্ধকারে; কিন্তু তার অমর সাহিত্য সারা বিশ্বে আজও ছড়িয়ে যাচ্ছে তার দ্যুতি। হোমারের সময়কার রাজাবাদশাদের নাম-নিশানা মুছে গেছে; কিন্তু হোমার তার ইলিয়াড ও ওডিসি নিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছেন আজও সারা পৃথিবীতে। সাহিত্য এমনই, সে কেবল নিজে টেকে না, তার স্রষ্টাকেও সে অমর করে রাখে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়েই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।”
নানা বিষয় নিয়ে সাহিত্য হতে পারে। এককালে দেবস্তুতি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সাহিত্যের নিয়ামক ছিল। ধীরে ধীরে তা সাধারণ মানুষের জীবনস্তরে এসে থিতু হয়। কিন্তু মানুষ তো আধ্যাত্মিক জীব। তার জীবনাচারের সঙ্গে অধ্যাত্মবোধ অবিচ্ছিন্ন। সব দেশের সব সময়ের সাহিত্যে তাই আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল।
আধ্যাত্মিক কবিদের সম্রাট মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি। রুমি তার জগৎ-বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মসনবিতে নানা রূপকের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন ও বিরহের গান শুনিয়েছেন। মসনবি শুরু হয়েছে এভাবে: “বাঁশির কান্না শোনো, কীভাবে অভিযোগ করছে সে তার আবাসস্থান থেকে তাকে নির্বাসিত করার জন্যে—যেদিন আমাকে ছিঁড়ে ফেলা হলো বাঁশঝাড় থেকে, আমার কষ্টের সুর শুনে নারী ও পুরুষের চোখে পানি এসে গেল; আমি দীর্ঘশ্বাস থেকে বাঁচার জন্যে আঘাত করলাম বুকে, আমার আবাসস্থানের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা ব্যক্ত করার জন্যে; যে তার গৃহ থেকে দূরে অবস্থান করে, সে সবসময় অপেক্ষা করে সেই দিনের জন্যে, কবে সে বাড়ি ফিরবে; আমার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে সর্বত্র—কার সাধ্য পরিমাপ করে আমার হৃদয়ের রহস্যের গভীরতা! আত্মা থেকে শরীর বিচ্ছিন্ন নয়, আত্মাও বিচ্ছিন্ন নয় শরীর থেকে, যদিও কোনো মানুষ কখনো দেখেনি আত্মাকে।”
রুমির বাঁশির এ আর্তনাদ মূলত স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে মানবাত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আর্তনাদ। এ বিরহের যন্ত্রণা প্রতিটি মানুষের। তাই রুমির মসনবি হয়ে উঠেছে সমস্ত মানুষের হৃদয়ের সংগীত। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক বিক্রীত কবিতার বই মসনবি। রুমি পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি; জনপ্রিয় তার অধ্যাত্মবাদের কারণে। রুমির মতো রাবেয়া বসরি, শেখ সাদী, ফরিদউদ্দীন আত্তার প্রমুখ দরবেশ কবির আত্মার সংগীতও বিমোহিত করে রেখেছে সারা পৃথিবীকে।
মৃত্যুচেতনা, পুনরুত্থান, স্রষ্টার ধ্যানে বিভোরতা, প্রকৃতিমগ্নতা প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদের নানা উপাদান। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজেই একটা মতবাদ তৈরি করে বসেন, যার নাম প্যান্থেয়িজিম। তার মতে, প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে স্রষ্টা বিরাজমান। তার প্রায় সব কবিতায় প্রকৃতি ও স্রষ্টা একাকার হয়ে আছে। তার বিখ্যাত কবিতা ‘টিনটার্ন এবি’। এ কবিতায় কবি বলেন—
...Nature never did betray
The heart that loved her; 'tis her privilege,
Through all the years of this our life, to lead
From joy to joy.
কবি বলছেন, প্রকৃতি কখনো প্রতারণা করে না, এটা সৌন্দর্য ও নীরবতা দিয়ে, উচ্চতার চিন্তা দিয়ে আমাদের এক আনন্দ থেকে আরেক আনন্দের দিকে ধাবিত করে, এটাই মূলত ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঈশ্বর, যার ধ্যানে তিনি বিভোর।
এমিলি ডিকিন্সনকে বলা হয় ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। আমেরিকান এ কবি স্রষ্টার সঙ্গে মিলনের আকুতি ও মৃত্যুচেতনার কবিতা লিখে বিমোহিত করে রেখেছেন বিশ্বপাঠককে। তার বিখ্যাত একটি কবিতা ‘যেহেতু আমি মৃত্যুর জন্য থামতে পারিনি’। এ কবিতায় কবি মৃত্যুকে তুলনা করেছেন প্রিয়তম অর্থাৎ বরের সঙ্গে, আর তিনি প্রিয়তমা বা কনে; মৃত্যু এসেছে তাকে বাসরশয্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেটা মূলত কবর। কবি বলেন—
Because I could not stop for death —
He kindly stopped for me —
The carriage held but just ourselves —
And immortality.
রোমান্টিক কবিতার অগ্রদূত বলা হয় উইলিয়াম ব্লেককে। ব্লেকের ‘সংস অব ইনোসেন্স’ ও ‘সংস অব এক্সপেরিয়েন্স’ মূলত আধ্যাত্মিক কবিতার সংকলন। এ সংকলনের কবিতাগুলোয় কবি আত্মার জয়গান গেয়েছেন। সংস অব ইনোসেন্সের ভূমিকা নিয়ে কবিতায় কবি বলেন, ‘পাহাড়ের উপত্যকায় একদা বাঁশিতে তুলেছিলাম আনন্দের সুর। হঠাৎ আমি মেঘের ওপর দেখতে পেলাম একটি অলৌকিক শিশুকে। সে হাসতে হাসতে আমাকে বলল, ‘হে বংশীবাদক, এবার তুমি মেষকে নিয়ে গান গাও। আমি মেষকে নিয়ে বাঁশিতে তুললাম সুর। সেই সুর শুনে সে আনন্দে উঠল কেঁদে।’ এখানে কবি মেষ ও শিশু বলতে বুঝিয়েছেন যিশুখ্রিস্টকে। বাঁশির প্রথম গান ছিল পার্থিব গান; আর বাঁশির দ্বিতীয় গান ঐশ্বরিক গান। কবি বোঝাতে চেয়েছেন, গান যখন ঈশ্বরের নামে গাওয়া হয়, তখন সে গান আরো মধুর হয়। কবির কথায়—
Piping down the valleys wild
Piping songs of pleasant glee
On a cloud I saw a child.
And he laughing said to me.
Pipe a song about a Lamb;
So I piped with merry chear,
Piper pipe that song again—
So I piped, he wept to hear.
টিএস এলিয়টকে আধুনিক কাব্যজগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য করা হয়। তার জগৎ-বিখ্যাত কবিতা ‘দি ওয়েস্ট ল্যান্ড’। কবি ওয়েস্ট ল্যান্ড বলতে বুঝিয়েছেন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে। তিনি একে নিষ্ফলা জমিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ সভ্যতার কেবল শরীর আছে, কোনো আত্মা নেই; এ কারণে এ নিষ্ফলা। এ কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের হাহাকার বিরাজ করতে দেখা যায়। কবি সলিল সমাধি হওয়া ফ্লেবাসের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানবজাতিকে বিশ্বাসের জগতে ফিরে আসার আহ্বান জানান এভাবে—
Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.
বাংলা কবিতায় আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে মধ্যযুগে। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রমুখের কবিতায় পাই আধ্যাত্মিকতার মহাসমাবেশ। মুসলিম কবিদের মধ্যে শাহ মহম্মদ সগীর এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌদ্দ শ-পনেরো শ শতকের এ কবি ‘ইউসুফ জুলেখা’ প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করে অমর হন। তার এ কাব্যের পরতে পরতে ঘটেছে অধ্যাত্মচেতনার বহিঃপ্রকাশ। তার বিখ্যাত ‘বন্দনা’ কবিতা তিনি শুরু করেন এভাবে—
“প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভুর জীবদানে স্থাপিলা সংসার।।
দ্বিতীয়ে প্রণাম কঁরো মাও বাপ পাত্র।
যান দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধায়।।
পিঁপড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত।
কোল দিয়া বুক দিয়া জগতে বিদিত।।”
মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। আলাওলের কবিতায় কৃষ্ণ-বিরহগাথা ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। রাধার কণ্ঠে কবি শোনান কানাইয়ের জন্যে তার আবেগ ও আতঙ্কের কথা—
“মুই যদি জানিতাম বাটে, কানাইয়া যমুনার ঘাটে
ত কেনে ভরিতে আইলুম জল।
কৈয়াছিল গুরুজনে, সে কথা না ছিল মনে
পাইলাম তার প্রতিফল।”
আধ্যাত্মিকতার এই ধারা প্রচণ্ড গতি পায় রবীন্দ্রনাথে এসে। সোনার তরী, খেয়া, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদ প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায় নানা রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে। খেয়া কাব্যের একটি অসামান্য কবিতা ‘কৃপণ’। ‘কৃপণ’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, রাজাধিরাজের আশীর্বাদে কী করে ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ চাল সোনায় পরিণত হয়েছে। কবির ভাষায়—
“যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কী!
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে—
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে।”
রবীন্দ্রোত্তর কালে নজরুল, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবির কবিতায় মুসলিম অধ্যাত্মচেতনার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নজরুল তার এক ‘খেয়াপারের তরণী’ কবিতায় যে অধ্যাত্মবোধের ঢেউ তুলেছেন, তার দ্বিতীয়টি বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া ভার। কবির কী অভিনব উচ্চারণ—
“আবুবকর উস্মান উমর আলি হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান—লা-শরিক আল্লাহ!”
তিরিশের কবিরা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে আবির্ভূত হন বাংলা সাহিত্যে। তাদের প্রভাব প্রচণ্ডভাবে সংক্রামিত হয় চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কবিদের ওপর। ব্যতিক্রম চল্লিশের ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসান এবং পঞ্চাশের আল মাহমুদ। এঁরা আধ্যাত্মিক চেতনার কবিতা লিখে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা ভাষাকে।
আশির দশকে এসে বাংলা কবিতা বিশ্বাসের জগতে ফিরে আসে। নব্বইয়ের দশকে কতিপয় শক্তিশালী কবির হাতে বিশ্বাসের ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাত্মচেতনার কবিতা লিখে যারা প্রসিদ্ধ হন, তাদের মধ্যে খন্দকার আশরাফ হোসেন, মতিউর রহমান মল্লিক, সোলায়মান আহসান, তমিজ উদদীন লোদী, সায়ীদ আবুবকর, জাকির আবু জাফর, নয়ন আহমেদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আল মাহমুদ তার ‘স্মৃতির মেঘলাভোরে’ সনেটে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, তাই পূর্ণ হয়েছে, পবিত্র শুক্রবারেই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন তিনি।
“কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ।”