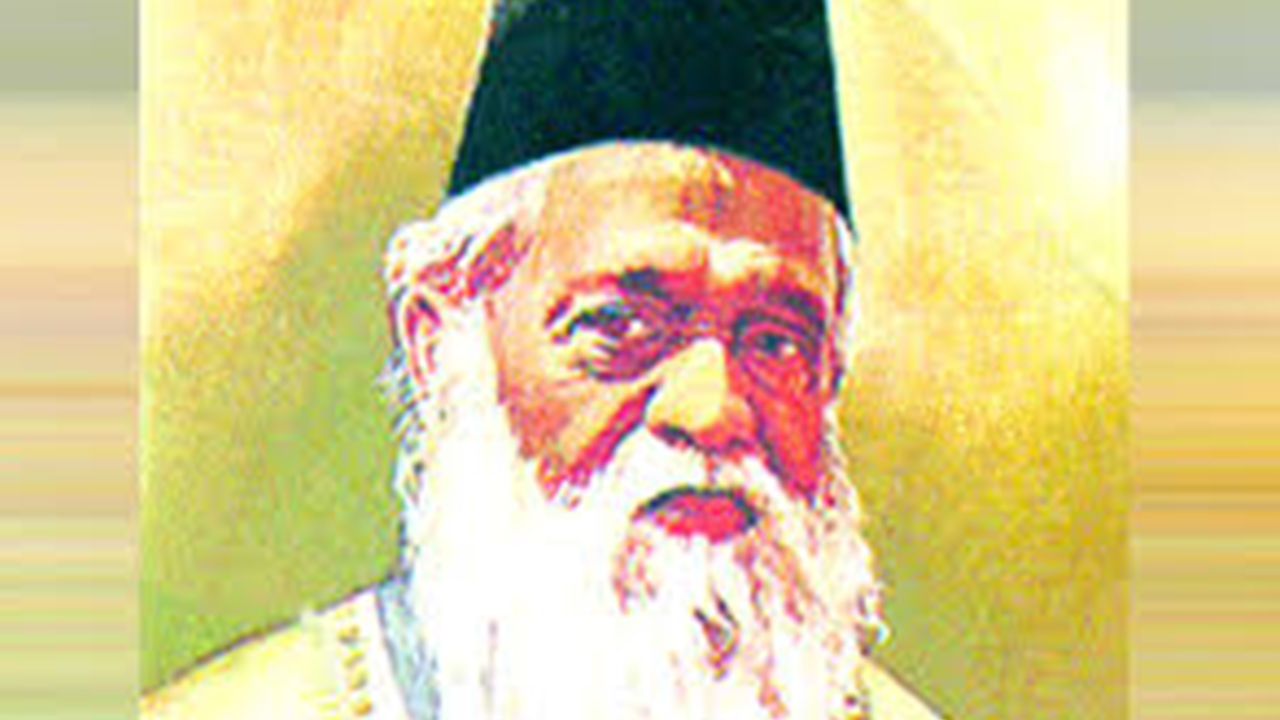জ্ঞান-তাপস ডক্টর শহীদুল্লাহ্র জ্ঞানের সীমানা বহু বিস্তৃত ছিল। তিনি মানববিদ্যার নানা শাখায় বিচরণ করেন; যেমন সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি। কোনো কোনো বিষয়ে তার সাফল্য অসামান্য। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করেন এবং সারা জীবন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তার মূল সাধনা ভাষা ও সাহিত্যের খাতে প্রবাহিত হয়। বহু ভাষাবিদরূপে তিনি খ্যাত; বিশেষ করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার পাণ্ডিত্য কিংবদন্তিতে পরিণত। প্রাচীন কাল থেকে সমকাল পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক জটিল গ্রন্থির উন্মোচন করেছেন এবং বিতর্কের সমাধান দিয়েছেন।
বাংলা সাহিত্যের অপর সাধক ডক্টর এনামুল হক ডক্টর শহীদুল্লাহকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন ‘চলমান বিশ্বকোষ’ বলে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।’ তার মতে, দীর্ঘদিন অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্যের যেকোনো সমস্যার সমাধান অতি সহজেই দিতে পারতেন।
বাংলাদেশের একটি উপেক্ষিত ধারা লোকবিদ্যার (folklore-এর) আলোচনায় তিনি সমান আগ্রহী ও দক্ষ ছিলেন, সেকথা আজ আমাদের অনেকের জানা নেই। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জাগে বিশ শতকের গোড়া থেকে। শুরুতে যে কয়জন বিদ্বান ব্যক্তির চেষ্টায় লোকবিদ্যা শিক্ষিত শ্রেণির দৃষ্টিগোচর হয় ও শ্রদ্ধা অর্জন করে, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাদের অন্যতম। যে তুলনামূলক পদ্ধতিতে তিনি লোকসাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন, তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি। বহু ভাষায় জ্ঞান ও বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য না থাকলে এই পদ্ধতিতে লোকসাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে আমাদের দেশে যে কয়জন ব্যক্তি লোকবিদ্যার চর্চা করেছেন, তারা কেউই ডক্টর শহীদুল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। আমরা মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে লোকবিদ্যার আলোচনা করে থাকি।
ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কখন কীভাবে লোকবিদ্যা চর্চায় মনোযোগী হন, সে সম্পর্কে বলার আগে লোকবিশারদ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের কিছু বক্তব্য স্মরণ করা যায়। ডক্টর ভট্টাচার্য এদেশের লোকবিদ্যার গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন; পরে সহকর্মী হন। গুরু-শিষ্য কিছুকাল একত্রে লোকচর্চা করেন। ডক্টর ভট্টাচার্য বলেন, “ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতো লোকসাহিত্য-প্রেমিক ব্যক্তি আমি অল্পত দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সনে মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে পূর্ব মৈমনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি ও আমি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। ঐ সম্মিলনীর সভাপতি রূপে লোকসাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তিনি যে একটি সুচিন্তিত মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সমসাময়িক প্রায় সকল পত্রিকাতেই আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইয়াছিল।
তাহার লোকসাহিত্য-প্রীতি কেবলমাত্র বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে একটি লোকসাহিত্য সংগ্রহ-সমিতি গঠন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতির এবং আমি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি।... কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ নিতান্ত অপ্রচুর ছিল বলিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের কার্য অগ্রসর হইতেছিল না।
অনন্যোপায় হইয়া ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব ও অর্থমন্ত্রী স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বিষয়ে বাংলা সরকারের নিকট তিনি অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহারা উভয়েই তাহার প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হন। ইতোমধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও তৎসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার জন্য কার্য স্বভাবতই আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান; কবি জসীমউদ্দীন সাহেবও কর্মান্তর গ্রহণ করিয়া ঢাকা পরিত্যাগ করেন। তারপর যে বৎসর ভারত-বিভাগ হয়, সেই বৎসর আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম পরিত্যাগ করি। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাটি সেখানেই অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে।”
লোকবিদ ডক্টর শহীদুল্লাহ্কে বোঝার জন্য আমরা এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম। তার কোনোরূপ পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে লোকচর্চায় অগ্রসর হন। লোকবিদ্যা চর্চার কয়েকটি স্তর আছে—বিশ্বস্ত সংগ্রহ-সংরক্ষণ, সনিষ্ঠ সম্পাদন-গবেষণা এবং প্রকাশনা। সবটাই যৌথকর্মের দ্বারা সম্ভব। তাই ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সমিতি গঠন করেন এবং সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যে চন্দ্রকুমার দে, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী, কবি জসীমউদ্দীন ও আশুতোষ ভট্টাচার্যকে একত্রিত ও অনুপ্রাণিত করেন; কিন্তু বিধি বাম। নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণেই একটি মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যে কাজটি চল্লিশ-দশকে সম্পন্ন হতে পারত, সে কাজটি ষষ্ঠ দশকে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ব্যক্তিগত প্রয়াস অব্যাহত রাখেন এবং সময় ও সুযোগমতো প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে তার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ দেন।
ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার পদে যোগদানের আগে দুই বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ‘গবেষণা-সহকারী’ হিসেবে কাজ করেন। ডক্টর সেন ওই সময় পূর্ববাংলার লোকগীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯২০ সালে তার রচিত ‘দ্য ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে তার সম্পাদনায় বিখ্যাত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ প্রকাশিত হয়। লোকসাহিত্য সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কৌতূহল এসময় জন্মে বলে আমাদের বিশ্বাস। দেখা যায়, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় তিনি ‘ময়নামতির গান’ নামক লোকসাহিত্যের একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ও নলিনী ভট্টশালী এটি সম্পাদনা করেন। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ ভাষা ও সাহিত্যে লোকসাহিত্য-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ ‘পল্লিসাহিত্য’ ও ‘আমার কাহিনি ফুরুলো’ সংকলিত হয়। ‘আমার কাহিনি ফুরুলো’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের মুসলিম ম্যাগাজিনে। সম্ভবত এ ধারার এটিই তার প্রথম রচনা। অতঃপর ১৩৪৫ সালে ‘পূর্ব মৈমনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনী’তে সভাপতির লিখিত ‘অভিভাষণ’ দেন, যা সমকালের পত্রপত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালে তিনি ‘Ancient Indian Folklore’ শিরোনামে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ওই সময় তার উদ্যোগে ঢাকায় ‘লোকসাহিত্য সংগ্রহ-সমিতি’ গঠিত হয়। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সিরাজুদ্দীন ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ‘কয়েকটি অপ্রকাশিত পালাগান ও বহু লোকগীতি’ সংগৃহীত হয়। ১৯৪৪ সালে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, “পল্লিগীতিকায় মুসলমানের দান অতি মহৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্যে পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে যে গাথাগুলো সংগৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া আরো বহু পল্লি-কবিতা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গের সরকার কি এদিকে মনোযোগ দেবেন?... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের অবশ্য কর্তব্য পূর্ব বাংলার সকল স্থান থেকে পুথি, পল্লিগীতি পল্লিকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ করে রক্ষা করা।”
অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমিতি নিষ্ক্রিয় হলেও ডক্টর শহীদুল্লাহ্ হাল ছেড়ে দেননি। তিনি ওই বছর সংখ্যাতিরিক্ত প্রফেসর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আবার যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণক্রমে তিনি ‘Traditional Culture in East Pakistan’ গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইকে সহযোগী হিসেবে নিয়ে তিনি ন্যূনাধিক এক বছরের মধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করেন। ১৯৫৮ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ট্রাডিশনাল কালচার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ওই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি একটি রিপোর্ট আকারে পেশ করেন। তিনি ওই সেমিনারে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক রিপোর্টটি ‘Traditional Culture in East Pakistan’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মোট আটটি অধ্যায়ের মধ্যে ছয়টি ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ও দুটি মুহম্মদ আবদুল হাই রচনা করেন। এটি নিঃসন্দেহে প্রবীণ শহীদুল্লাহ্র লোক-বিদ্যানুরাগের ফল।
এ সময়ের কিছু আগে ও পরে তিনি কয়েকটি মূল্যবান বাংলা প্রবন্ধ রচনা করেন। সেগুলো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অথবা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো— (১) ‘কাজলরেখা’, পাকিস্তানের লোককাহিনি, ঢাকা, ১৯৫৩; (২) ‘জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬১ বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা, ১৩৬১; (৩) ‘ভেলুয়া সুন্দরী’, পূর্ব বাংলার লোকগীতিকা, ঢাকা, ১৯৫৫; (৪) ‘মহুয়া’, পূর্ব বাংলার লোকগীতিকা, ঢাকা, ১৯৫৫; (৫) ‘গল্পের জন্মান্তর’, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫; (৬) ‘গল্পের রূপান্তর’, সমকাল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬; (৭) ‘লোক-সংস্কার’, সাহিত্যিকী, শরৎ সংখ্যা, ১৩৬৬; (৮) ‘লোক-কৃষ্টি সপ্তাহ’, পূর্ব পাকিস্তানের লোক-কৃষ্টি, ঢাকা ১৯৬৮।
১৯৬৩ সালে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ‘লোকসাহিত্য’-বিষয়ক একটি পৃথক আলোচনা আছে। ‘কাজলরেখা, শীত ও বসন্ত, আমার কাহিনি ফুরুলো, ব্রতকথা, ছড়া, ডাক ও খনার বচন, হিয়ালী-প্রবাদবাক্য’ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ২য় খণ্ডে মহুয়া, ভেলুয়া সুন্দরী, লোকসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের নারী, গীতিকারগণ, বারমাসী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।
ডক্টর শহীদুল্লাহ্র সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ‘পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’-এর সম্পাদনা। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই অভিধান উভয় বাংলায় এই প্রথম প্রণীত হয়। তিনি ওই গ্রন্থের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মনীষাদীপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক একটি ‘ভূমিকা’ প্রণয়ন করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমি অভিধানটি প্রকাশ করে।
অশীতিপর বয়স্ক ডক্টর শহীদুল্লাহ্র লোকচর্চার এটাই রূপরেখা। পরিমাণের দিক থেকে এ সংখ্যা অপ্রতুল। তিনি জ্ঞানসাধনার বিচিত্র ধারার মতো এ-ধারাতেও চিন্তার ব্যাপ্তি ও নিষ্ঠার সততা রক্ষা করেছেন। লোকসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা যেমন একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য বিষয়, আঞ্চলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, উৎস ও অর্থ-উদ্ধার তেমনি একটি দুরূহ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ উভয় কাজ সম্পন্ন করে আমাদের দেশে লোকচর্চাকে একটি সম্মানজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতির অতীত পরিচয়, সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার জন্য লোকভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার প্রয়োজন আছে—এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেন।
ইউনেস্কোর উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে রচিত ‘Traditional Culture in East Pakistan’ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় সাধন করা। এজন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ একটি উপক্রমণিকাসহ লোকনৃত্য, লোকবাদ্য, লোকচারুশিল্প, লোককারুশিল্প এবং সমাজজীবনে লোক-ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও তার সংরক্ষণ-পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে ছয়টি ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন। মুহম্মদ আবদুল হাই লেখেন, লোকসাহিত্য ও সংগীত এবং লৌকিক খেলাধুলা-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ। ডক্টর শহীদুল্লাহ্র শেষ প্রবন্ধটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব বাংলার লৌকিক উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, জাদুঘর, আর্ট কলেজ, আর্ট কাউন্সিল, বুলবুল একাডেমি, রেডিও প্রভৃতি সংগঠন কীভাবে পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দেন। এর সঙ্গে দেশের শিক্ষিত শ্রেণি এগুলোর মূল্যায়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে লোক-ঐতিহ্যের চর্চা অব্যাহত রাখেন, তারও পথনির্দেশ দেন। তার বিশ্বাস, দেশীয় ঐতিহ্যের ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা জাগবে এবং বিদেশি সংস্কৃতির দাসত্ব ঘুচবে। তিনি সরকারের উদ্যোগে একটি জাতীয় জাদুঘর স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেন। ১৯৫৮ সালে নভেম্বরে মাদ্রাজে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিভিন্ন প্রস্তাবে ‘জাদুঘর’ নির্মাণ করে লৌকিক উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১০ দেশজ উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি পরবর্তীকালেও উল্লেখ করেন। তার মৃত্যুর আগের বছর ১৯৬৮ সালে ঢাকার রেডিও ‘লোক-কৃষ্টি সপ্তাহ’ পালন করে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ওই নামের একটি প্রবন্ধে বলেন, “এই সকলের সংগ্রহ সংরক্ষণ তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতির জন্য পৃথিবীর অন্য সভ্য দেশগুলির ন্যায় আমাদের ঢাকাতেও একটি ‘লোক-কৃষ্টি সমিতি’ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক’।” স্বাধীনতা-উত্তর কালে ঢাকায় ‘বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ’ এবং সোনারগাঁয়ে জাতীয় পর্যায়ে ‘লৌকিক জাদুঘর’ (১৯৭৫) স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু উভয় প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠে ডক্টর শহীদুল্লাহ্র মতো বাংলার ঐতিহ্য-প্রেমিক আরো অনেকের সাধ ও স্বপ্নকে এখনো বাস্তব রূপ দিতে পারেনি।
পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, ডক্টর শহীদুল্লাহ্র লোকবিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলো একত্রে সংকলিত হওয়া উচিত। এ-ধারার গবেষক তাতে উপকৃত হবেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন অপেক্ষা ডক্টর শহীদুল্লাহ্র আলোচনার তাত্ত্বিক মূল্য অনেক বেশি। কেননা আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিকে তিনি লোকবিদ্যা বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন।
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন