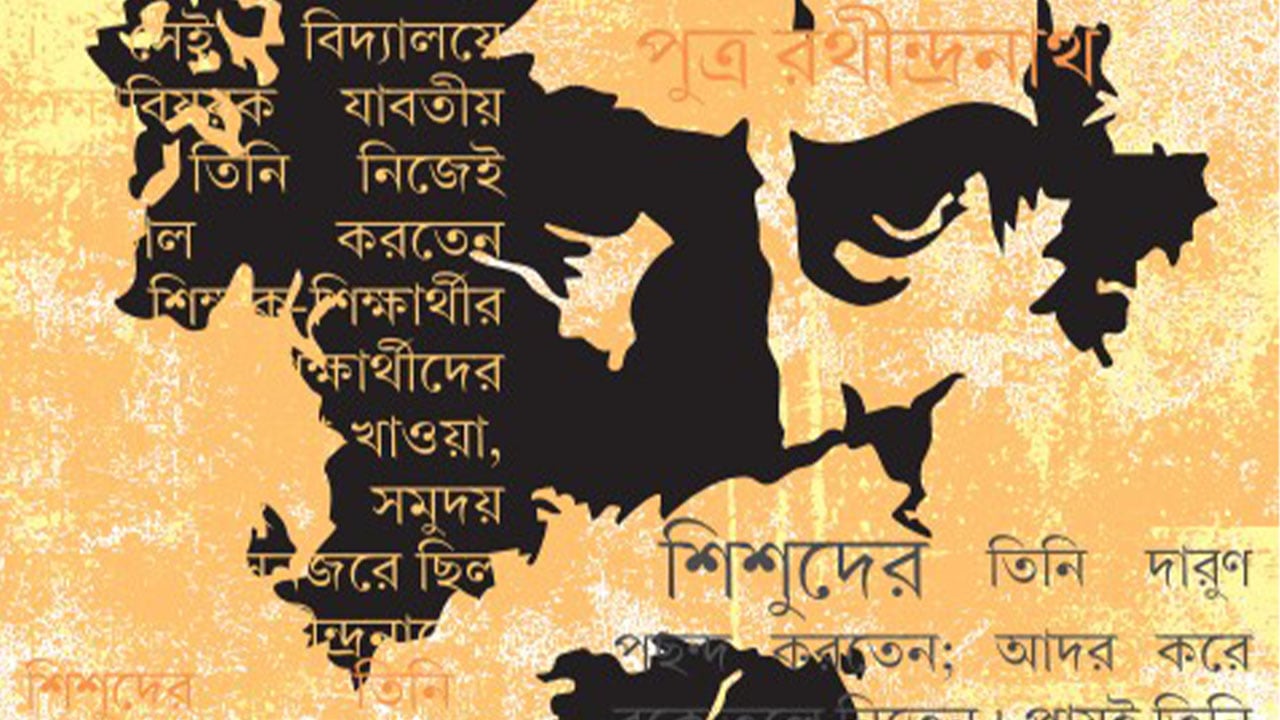রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) নিজে শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজ হাতে ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ (১৯০১) নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এমনকি তার দুই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় বিষয় তিনি নিজেই দেখভাল করতেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, শিক্ষার্থীদের বাসস্থান, থাকা-খাওয়া, আহারাদিসহ সমুদয় বিষয় তার সুনজরে ছিল। মূলত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি বিরাট শিশুমন ছিল। এমনকি বলা যায়, আজীবন তিনি শিশুই ছিলেন।
শিশুদের তিনি দারুণ পছন্দ করতেন; আদর করে বুকে তুলে নিতেন। প্রায়ই তিনি সবুজ-শ্যামল বৃক্ষের নিচে বসে ক্লাস (ব্রহ্ম বিদ্যালয়) নিতেন। প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির মতো উদার ও উন্মুক্ত মন নিয়ে শিশুর মতো করে তিনি শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশে যেতেন; তাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মীয় পুরাণ রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে গল্পসল্প করতেন। মূলত শিশুমন বোঝার এবং অনুধাবন করার চিন্তা ও চেষ্টা তিনি করতেন। শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর তিনি কিছু চাপিয়ে দিতে চাইতেন না, বরং তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকেই প্রবলভাবে প্রাধান্য দিতেন। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে এ ধরনের পাঠদান প্রক্রিয়াকে ‘প্যাডাগোজি’ বলা হয়।
আরো খোলাসা করে বললে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি। সেই প্রত্যয় ও পদ্ধতি তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রচার ও প্রচলন করেছিলেন। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের শিক্ষাজীবন থেকেই এই শিক্ষাপদ্ধতির (প্যাডাগোজি) উপযোগ ও অনুভবের কথা দারুণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শিশুবেলায় বিদ্যালয়ের প্রতি তার বিপুল আকর্ষণ ছিল। নাছোড়বান্দার মতো বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য তিনি প্রায়ই বায়না ধরতেন; এমনকি কান্নাকাটিও করতেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্তির পর বিদ্যালয়ের প্রতি তার বিকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল।
‘আমার ছেলেবেলা’, ‘পথের সঞ্চয়’, ‘আত্মপরিচয়’, কিংবা ‘জীবনস্মৃতি’র মতো স্মৃতিমূলক কোনো গ্রন্থেই কবিগুরুর শিক্ষাজীবনের কোনো সুখকর স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না। উল্টো বিয়োগ ও বিতৃষ্ণার কথাই লিখে গেছেন তিনি। কমবেশি প্রায় ছয় বছর কবিগুরু নর্মাল স্কুলে (মল্লিকদের বাড়ি) অধ্যয়ন করেছিলেন। বিদ্যালয় ছাড়াও কবিগৃহে কবিকে অনেক শিক্ষকই পড়াতে আসতেন। তার মধ্যে নীল কমল ঘোষাল, বিষ্ণু চক্রবর্তী, অঘোর বাবু অন্যতম। বিদ্যালয় থেকে তিনি খুব একটা কিছু শিখেছিলেন বলে মনে হয় না; উল্টো বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরুরা কবির শিশুমনে ‘বিভীষিকার সৃষ্টি করত’ অন্তত ‘বিশ্বভারতী’ প্রবন্ধগ্রন্থে কবি এমনটাই জানিয়েছেন। তবে শিক্ষক হিসেবে সীতনাথ দত্ত বোধহয় খানিকটা ব্যতিক্রম ছিলেন। কবির লেখায় এই শিক্ষকের কিঞ্চিৎ প্রশংসার কথা শোনা যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিখেছিলেন মূলত প্রকৃতির কাছ থেকে, জীবন ও জগতের কাছ থেকে। তার কাছে পুরো জগৎটাই ছিল পাঠশালা; সার্বক্ষণিকভাবেই শিক্ষা নিতেন তিনি। কবি নির্মল বসুর ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র/ নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র’Ñএই কাব্যচরণটি কবির সঙ্গে দারুণভাবে মিলে যায়। এই শিক্ষাই তাকে বিশ্বকবি বানিয়েছিল, বানিয়েছিল বিশ্বভুবনের বাসিন্দা। তাই কবিগুরু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের (আশ্রম) শিক্ষার্থীদেরও প্রকৃতির কাছে নিয়ে যেতেন; প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতেন।
তিনি চাইতেন, প্রকৃতির মতোই তার শিক্ষার্থীরা (স্বাভাবিকভাবে) বেড়ে উঠুক; বেড়ে উঠুক তাদের বিকাশ ও ব্যাপ্তি। আশ্রমে গাছ লাগানো, গাছের তলায় আগাছা নিড়ানো, পানি ঢালা ও রান্নাবান্নার মতো কাজকর্ম শিক্ষার্থীদের দিয়ে হাতে-কলমে করাতেন তিনি। পাখি কিংবা কাঠবিড়ালির মতো প্রাণীর পোষ মানানোয় তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পুরস্কারও ঘোষণা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রাণ, প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাণের বিকাশ ও বিস্তৃতি দেখতে চাইতেন; চাইতেন মনুষ্যত্বের উৎপত্তি ও উৎকর্ষ সাধন করতে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ও জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতেন; চেষ্টা করতেন জীবনটাকে আনন্দময় করে গড়ে তুলতে। কেবল সনদ কিংবা সার্টিফিকেটভিত্তিক শিক্ষা নয়, শিক্ষাকে তিনি জনজীবন ও জনপদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইতেন; মিলিয়ে নিতে চাইতেন। এই দেওয়া-নেওয়াতে তার যাপিত জীবন ও চিন্তাজগতের প্রচার ও প্রসারণ ঘটেছিল।
মূলত শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রমনে ব্যাপক চিন্তাভাবনা সক্রিয় ছিল। এই চিন্তাভাবনার প্রায়োগিক পদ্ধতির দিকেও এগিয়েছিলেন তিনি। হয়তোবা এ কারণেই তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন; উদ্যোগী হয়েছিলেন শিক্ষক নিয়োগের। তন্নতন্ন করে তিনি একজন ভালো মন ও মানের শিক্ষকের খোঁজ করতেন। একবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ে একজন নামকরা হেডমাস্টার নিয়োগ করেছিলেন। ওই মাস্টার শিশু শিক্ষার্থীদের গাছে চড়া, দৌড়ানো, লাফালাফি ইত্যাকার কর্মকাণ্ড দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন এবং এগুলোয় কবির সমর্থনও মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ওই মাস্টার বিদায় নেন, কবিও বিদায় দেন। এরপর আর হেডমাস্টার রাখেননি তিনি। হেডমাস্টারের বিদায় প্রসঙ্গে ‘বিশ্বভারতী’ প্রবন্ধে ঠাকুর লিখেছেন-তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার।’ রবীন্দ্রনাথ ধুরন্ধর পণ্ডিত চাননি; তিনি চেয়েছিলেন একজন মানবিক মানুষ, একজন মানবিক শিক্ষক; যে শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।
রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় সবাই অধ্যাপনার জন্য সমভাবে উপযুক্ত নয়। সবাইকে হরেদরে এই পেশায় আসা কিংবা নেওয়া সমুচিত নয়। ‘আশ্রমের শিক্ষা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেনÑ‘তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্যই তাঁদেরই স্বাভাবিক।’ ‘ছাত্র শাসনতন্ত্র’ নিবন্ধে শিক্ষকের গুণ ও গুণাবলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো লিখছেন-ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারিবে; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।’
সেইসঙ্গে কারা কারা গুরুপদে বরণের অযোগ্য, সেই মাপকাঠিও তার প্রবন্ধসাহিত্যে স্পষ্ট দেখা যায়। ‘ছাত্র শাসনতন্ত্র’ নিবন্ধে তাকে আরো লিখতে দেখি-যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য।’ এসব মাপকাঠির বিচার-বিবেচনায় আজকের বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজের কত শতাংশ শিক্ষক শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত-এই প্রশ্ন তো তোলাই যায়। এমনকি বিগত সরকারের শাসনামলে রাষ্ট্রই (সরকার) কি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সদাচার করেছিল? শিক্ষার্থীদের সামান্য দাবিদাওয়ার প্রতি ন্যূনতম সম্মান না দেখিয়ে উল্টো ‘রাজাকারের বাচ্চা’ বলে চূড়ান্ত অপমান করেছিল।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এহেন অপমান হজম করতে পারেনি। সেদিন সন্ধ্যায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছিল। শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ‘ছাত্র শাসনতন্ত্র’ নিবন্ধে কবিগুরু লিখছেন-এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিধিয়া থাকে।’ হয়তোবা তা-ই হয়েছিল। তাই সেদিন শিক্ষার্থীরা তাদের অমূল্য প্রাণটুকু হাতের মুঠোয় পুরে রাজপথে নেমে গিয়েছিল; ওই প্রাণের বিনিময়ে তারা উপহার দিয়েছিল নতুন বাংলাদেশ। নতুন বাংলাদেশে সম্ভবত শিক্ষক সমাজ সর্বোচ্চ সংকটের মুখোমুখি হয়। স্থানে স্থানে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে স্বয়ং শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। কোনো কোনো জায়গায় প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জোর করে টেনেহিঁচড়ে চেয়ার থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি সেনাবাহিনীর সদস্যের উপস্থিতিতেও ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে।
আদতে শিক্ষকের মানমর্যাদা আর্মি-পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী দিয়ে রক্ষা করা সম্ভব নয়। শিক্ষকের মর্যাদা শিক্ষককেই রক্ষা করতে হয়। হ্যাঁ, কিছু শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি করেছিল। কিন্তু সেই বাড়াবাড়িতে কোনো ধুরন্ধর পণ্ডিতের (শিক্ষক) যে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়া ছিল না, তা কি আমরা হলফ করে বলতে পারি? আবারও রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে আসি। ‘ছাত্র শাসনতন্ত্র’ নিবন্ধের আরেক জায়গায় তিনি লিখছেন-ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, তাহাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়।’ শিক্ষকতা মূলত সূক্ষ্ম সাধনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ সেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লেখালেখি, জমিদারি দেখাশোনা ইত্যাকার দরকারি কাজের পাশাপাশি শিক্ষকতাও তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শিক্ষকতাকেও রবীন্দ্রনাথ সাধনার মতোই গ্রহণ করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসেবে। তৎকালীন সময় ও সমাজে এমনটাই হতো। এমনকি রাজারাও তাদের রাজ্য ও রাজত্ব পরিত্যাগ করে শিক্ষকতায় আসতেন।
শীলভদ্র এমনই একজন মহান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তার রাজ্য ও রাজত্ব পরিত্যাগ করে নালন্দার (তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষাসংঘে যোগদান করেছিলেন। স্বয়ং হিউয়েন সাঙের মতো বিদেশি পর্যটক ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব এই শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ’ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনটাই জানিয়েছিলেন। শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষকতা কবিগুরুর অস্থিমজ্জার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গে জমিদারি দেখাশোনার জন্য কবিগুরু পদ্মার পথে নৌকাযোগে শিলাইদহে আসতেন। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ফাদার অ্যাজ আই নু হিম’ গ্রন্থমাধ্যমে জানা যায়, শিলাইদহে এসেও কবিগুরু ছেলেমেয়েদের বাংলা-ইংরেজি পড়াতেন। এই পড়া ও পড়ানোর কাজে শিক্ষকের আন্তরিকতা, সততা ও সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, শিক্ষকের মান ও মর্যাদা। এই সত্যটুকু স্মরণে রাখলেই আখেরে শিক্ষকেরই লাভ।
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন