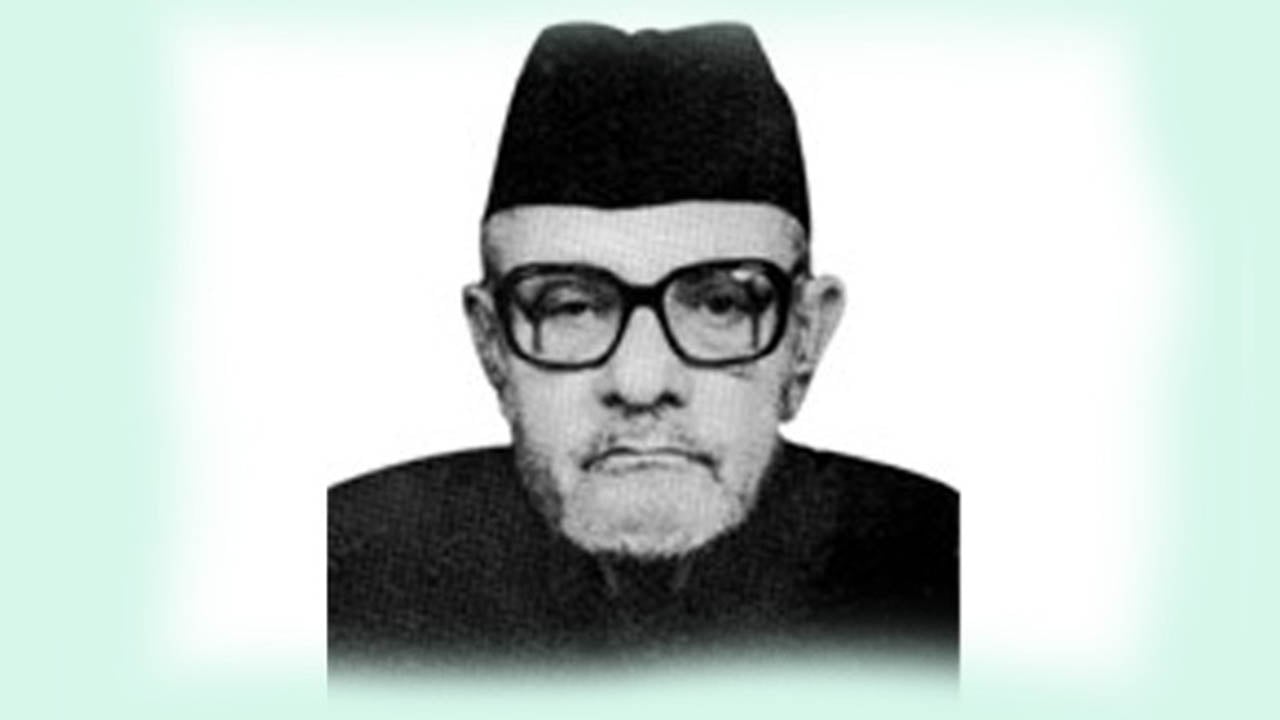এ দুনিয়ার সকল জীবেরই জীবন রক্ষার প্রয়োজনে কোনো না কোনো সংকেত ব্যবহার করতে হয়। একেবারে নিম্নশ্রেণির কীট-পতঙ্গের জীবনেও সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার প্রকাশরূপে নানাবিধ সংকেত প্রকাশ পায়। পাখিদের স্তরে যেসব প্রাণী রয়েছে, তাদের জীবনে বেশ পরিষ্কার কতকগুলো শিস উচ্চারিত হয়, যাতে তাদের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। বাঘ, ভালুক বা বানরজাতীয় জীবের পরিষ্কার ভাষা রয়েছে এবং প্রাণীতত্ত্ববিদগণ এ ভাষা বুঝতে সমর্থ হয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ করেন।
মানুষের জন্ম জীবজগতে হলেও মানুষের ভাষা ও পশুদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পশুরা তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে ভাষা আদিকাল থেকে ব্যবহার করে আসছে, সে ভাষাই চিরকাল ব্যবহার করবে, তাতে কোনো পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়।
মানুষের জীবনে নানা ভাব, নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির উদ্ভব ও লয়ের ফলে তার আদি ভাষাতে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলেও মানুষের ভাষায় নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। এজন্য মানুষেরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে এবং তাদের মানসিক বিকাশে তারতম্য দেখা দিলে এ দুনিয়ায় বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
যে ভাষাতে মানবজীবনের সকল ভাব যত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা যায়, সে ভাষাকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ সফল ভাষা বলা যায়।
মানবজাতি নানাবিধ কারণে দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাদের জীবনের নানাবিধ তাগিদে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ভাষার আশ্রয় নিয়েছে। এজন্য তাদের মধ্যে যেভাবে বিভাগ অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে, তেমনি তাদের ভাষায়ও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাই দেখা যায়, এ দুনিয়ায় নানাবিধ ভাষাভাষী লোকেরা বাস করছে। এ ভাষাগত পার্থক্যের ফলে তাদের জীবনে পরবর্তীকালে যেমন একতার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে হিংসা ও বৈরিতার বীজও বপন করা হয়েছে।
আমাদের এ উপমহাদেশে নানাবিধ ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় হাজার বছর পূর্বে এ অঞ্চলে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হলে পর তাতে একদল মানুষ তাদের মনপ্রাণের নানাবিধ ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম লাভ করে তাকে শ্রদ্ধা করে আসছে। এ ভাষার উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে এখনো তর্কের ইতি হয়নি। তবে এ ভাষা যে দেবভাষা থেকে সরাসরি উৎপন্ন হয়নি, সে সম্বন্ধে কোনো বাকবিতণ্ডা নেই। পালি, প্রাকৃত, সৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি স্তর মতান্তরে পূর্ব-মাগধী স্তর পার হয়ে এ ভাষা যে রূপ নিয়েছিল, সেখানেই তার গতির ইতি হয়নি। নানাজাতীয় লোকের এ অঞ্চলে আগমনের ফলে এবং সে সকল লোকের ভাষা এ ভাষায় গৃহীত ও একাত্মকরণের ফলে, এ ভাষা আরো প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। এ দেশে নানা ধর্মের উৎপত্তি হওয়ায় এবং বিদেশ থেকে আগত নানা লোকের ধর্মীয় মতবাদ এদেশে প্রচারিত হওয়ায়, ক্রমেই এ ভাষা সমৃদ্ধির পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার ফলে এবং সম্রাট অশোক কর্তৃক তা রাষ্ট্রধর্ম রূপে গৃহীত হওয়ার ফলে, যে সকল অঞ্চল অশোক কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, সে সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য দেখা দেয়। তবে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক অত্যন্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও জনগণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শশাঙ্কের পরবর্তী এক শত বছরের অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায়ের যুগ পার হলে, পাল রাজাদের রাজত্বকালে সারা বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবন দেখা দেয়। এ বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বকালেই খ্রিষ্টীয় ৭৫০-১১৩০ তৎকালীন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও বর্ধিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে সেন রাজগণ কর্তৃক এদেশ অধিকৃত হলে তারা পালদের অনুসারিত বৌদ্ধধর্ম ও তাদের সংস্কৃতিকে এদেশে থেকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার বিকাশে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। দেবভাষা থেকে পথভ্রষ্ট পূর্বী মাগধী বলে বর্তমানে পরিচিত বাংলা ভাষার উৎপত্তি হওয়ায় বাংলা ভাষাকে তাঁরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখেই দেখতেন। সে ভাষা গ্রহণ করার তো কোনো প্রশ্নই নেই, বরং তখনকার দিনে দেবভাষাতে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছিল, তাকে সংস্কৃত করার মানসে পণ্ডিতগণকে নিয়োগ করেন। তার ফলে তাঁদের রাজধানী গৌড়ে সংস্কৃত দেবভাষাতে এক নতুন রীতি দেখা দেয়। তা এখনো গৌড়ী রীতি বলে সুপরিচিত। তার নমুনাস্বরূপ সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব বিরচিত গীত গোবিন্দের নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিগুলো এখনো পণ্ডিত সমাজে জীবিত রয়েছে:
‘স্মরগরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম
দেহি পদপল্লব মুদারম’
—আমার মস্তকের ভূষণস্বরূপ কামরূপ চিত্তের খণ্ডনকারী উদার পদপল্লব আমাকে দাও।
এভাবে গৌড়ের বিদ্বান সমাজে কোনো আশ্রয় না পেয়ে বাংলা ভাষা সাধারণ বা তথাকথিত ইতর লোকের সমাজে স্থান লাভ করে। তবে সপ্তম শতাব্দী থেকে মুসলিম সুফিগণ ও সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশীয় বণিকগণ এদেশে আগমন করার কালে তাদের ভাষার কতকগুলো শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে মিলিত হয়ে এ ভাষার পুষ্টিসাধন করে। ১২০১ সালে (মতান্তরে ১২০৪ সালে) ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক এদেশ বিজিত হলে এ ভাষার পুষ্টির আরো সুযোগ দেখা দেয়। বিজেতা তুর্কিগণের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি, দরবারের ভাষা ছিল ফারসি এবং ঘরোয়া ভাষা ছিল তুর্কি। যদিও এদেশীয় অন্য বণিকদের ভাষাও অবলীলাক্রমে গৃহীত হয়ে ভাষার পুষ্টি সাধিত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে মুসলিম কবিগণ এ ভাষায় কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করার ফলে এ ভাষা আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কর্তৃক এদেশে বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ভাষা ক্রমেই নানা ভাষার শব্দসম্ভারের ফলে আরো গরীয়ান হয়ে দেখা দেয়। সে সময় এদেশের দরবারের ভাষা ছিল ফারসি, হিন্দু সমাজের পণ্ডিতজনের কালচারের ভাষা ছিল সংস্কৃত, মুসলিম সমাজের তথাকথিত অভিজাত সমাজের কালচারের ভাষা ছিল উর্দু এবং জনসাধারণের ভাষা ছিল মিশ্র বাংলা।
ইংরেজদের কোম্পানি সরকার নানাভাবে সদ্য বিজিত মুসলিমদের নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে প্রথমত ১৭৬৩ সালে নামেমাত্র সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে দেওয়ানি পদের সনদ গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম কর্মচারীদের বিতাড়িত করে, তাদের স্থলে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করে। তার পরে ১৭৯৩ সালে মুসলিমদের বঞ্চিত করে এদেশের ভূসম্পত্তি তাদের প্রতিবেশী এবং একদা অধীনস্থ হিন্দু সমাজের লোকদের নিকট বহুলভাবে বন্দোবস্ত দেয়। তারপরে ১৮০০ সালে তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কলকাতাতে সদানিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তখনকার দিনের খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামজয় তর্কালংকার, মদনমোহন তর্কালংকার প্রমুখদের নিযুক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নির্দেশ দেয় যেন তাতে ইসলাম বা মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু না থাকে। তার ফলে তারা এমন এক আদর্শিক ভাষা সৃষ্টি করেন, যাকে অবাধে অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জিত সংস্কৃত ভাষা বলা চলে। সে ভাষায় কেবল আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দাবলি বর্জিত হয়নি, প্রচলিত বাংলা শব্দাবলিও বর্জিত হয়েছে। সে ভাষার বিরুদ্ধেই প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বা ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ রচনা করেছিলেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও কষ্টেসৃষ্টে বাংলা সে ভাষার প্রচলনে প্রতিবাদ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ‘সীতার বনবাস’ বা ‘বেতাল পঞ্চবিংশতী’ যাঁরা পাঠ করেছেন, তারা বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রতিবাদের সমর্থন করবেন। তবে এ ভাষাই ইংরেজ সরকার কর্তৃক ইস্কুল-কলেজের ভাষা বলে গৃহীত হয়। তার ফলে মুসলিম সমাজের লোকেরা বাংলা ভাষার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে এবং সে সমাজের তথাকথিত অভিজাত সমাজের লোকেরা উর্দুকে তাদের সাংস্কৃতিক ভাষা বলে গ্রহণ করে।
এ উপমহাদেশে বাংলা ভাষার উৎপত্তি পরে দিল্লির সুলতান এমতাদউদ্দীন বুলবনের (মৃত্যু ১২৮৭ খ্রি.) রাজত্বকালে তুর্কি কবি আমির খসরুর দ্বারা উর্দু ভাষার সূত্রপাত। তখনকার দিল্লির সুলতানদের অধীনে আরব, পারস্য, তুর্কি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত নানাজাতীয় ও নানা লোকেরা এসে সৈনিক শ্রেণিতে ভর্তি হতো। তাদের পক্ষে একে অপরের ভাষা বোঝা কঠিন ছিল। অথচ তখনো ভারতের বুকে সাধারণ ভাষার উৎপত্তি হয়নি। এজন্য একটা সাধারণ ভাষার অভাব সকল মহলেই অনুভূত হতো। আমির খসরু দিল্লির চতুষ্পার্শ্বে প্রচলিত খড়িবুলির সঙ্গে ফারসি ভাষার যোগসাজশে এক অভিনব ভাষার সৃষ্টি করেন। কালে সেই ভাষাই বিবর্তনের ধারায় উর্দু বা শিবিরের ভাষাতে পরিণত হয়। তিনি একই কবিতায় ফারসি ও স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে এক অভিনব ভাষা গড়ে তোলেন:
‘হিন্দু বাচ্চেবা বনিগর-আজব হুসন ধরতো হ্যায়
দর আকতে সুমন গুফতন মুহফুল করতো হ্যায়
গুফতম বিয়াকে বর লবেতু বুসে বগীরম
গুফত আরে রাম ধরম নষ্ট করতো হ্যায়।’
অর্থাৎ, একটা হিন্দু ছেলেকে দেখো, কী আশ্চর্য সৌন্দর্যের সে অধিকারী। কথা বলার সময় তার মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ে। তাকে বললাম, কাছে এসো, তোমার ঠোঁটে চুমু খাব। সে বললে, আরে রাম, তাহলে আমার ধর্ম নষ্ট হবে। এ ভাষাই কালে বিবর্তনের ধারায় উর্দু ভাষায় পরিণত হয়। ইংরেজরা এদেশ অধিকার করার পূর্বে এ ভাষা মনে মনে বিকাশ লাভ করে। তার ফলে যুক্ত প্রদেশ, দিল্লি ও তার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের অভিজাত লোকদের সমাজে তা সাংস্কৃতিক ভাষার স্থান দখল করে।
কোম্পানি সরকার কর্তৃক কলকাতাতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে, সরকারি চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে নানা প্রদেশ থেকে অনেক মুসলমান কলকাতাতে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য উর্দুকে তাদের সাধারণ ভাষা বলে গ্রহণ করে। কালে এ ভাষাই তাদের মাতৃভাষায় পরিণত হয়। যেহেতু পণ্ডিতদের সৃষ্ট আদর্শিক বাংলা ভাষায় ইসলামি বা মুসলিমদের ঐতিহ্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি, এজন্য মুসলিমদের উচ্চকোটি মহলে বাংলা ভাষার প্রতি বিরাগের ভাব দেখা দেয় এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার সূচনাতে তারা উর্দুকে ভার্নাকুলার হিসেবে গ্রহণ করেন। মফস্বলের কোনো কোনো শহরে এবং কোনো কোনো উন্নত সংস্কৃতির গ্রামাঞ্চলেও উর্দু ভাষার চর্চা দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং তৎকালীন আসাম প্রদেশের অন্তর্গত সিলেট প্রভৃতি শহরে উর্দু ভাষার চর্চা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এতে বঙ্গদেশবাসী তথা ভারতীয় মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আবদুল লতীফেরও সমর্থন ছিল। তিনি বলতেন, ‘বঙ্গদেশের আশরাফদের মাতৃভাষা উর্দু তবে আতরাফদের মাতৃভাষা বাংলা।’
এদিকে কিন্তু আশরাফগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে বাংলা ভাষা গ্রামীণ সমাজে তার আপনার জীবনীশক্তির দ্বারাই বিকশিত ও বর্ধিত হয়েছিল। তবে তা বিদ্বজ্জন সমাজে ছিল তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয়বস্তু। সে ভাষায় লিখিত পুস্তকাদিকে বলা হতো, ‘কলিম পুঁথি’। সেগুলো খুব গরিব প্রেস থেকে ছাপা হতো বলে তার নাম ছিল বটতলার ছাপা। সে ভাষাই জনসাধারণের সাধারণ ভাষা হওয়ার প্রকৃত দাবিদার ছিল। অথচ সে ভাষাই রয়ে গেল অন্ত্যজ ভাষা হিসেবে। তবে ভাষা সর্বদাই জীবন্ত। জীবনের দাবি যেমন উপেক্ষা করা যায় না, ভাষার দাবিকেও তেমনি উপেক্ষা করা যায় না।
কালের গতিতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের লোকেরা আকৃষ্ট হয়। বাংলা ভাষাকে তাদের প্রকৃত ভাষা বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। এক্ষেত্রে নওয়াব আবদুল লতীফের উৎসাহ, মাওলানা কেরামত আলীর অনুমতি এবং মুনশী মেহেরউল্লার বাংলা ভাষার প্রচারণা ছিল কার্যকরী। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করে মুসলিম সমাজ যখন সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়, তখন নওয়াব আবদুল লতীফই মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তবে এতেও গোঁড়া সমাজের লোকেরা বাধা প্রদান করতেন। তাদের প্রচারণা ছিল ইংরেজদের অধিকৃত এদেশ দারুল হারব বা যুদ্ধের দেশ, ইংরেজের শিক্ষায় মুসলিমদের কাফির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এ শিক্ষা সর্বকালেই বর্জনীয়। এবংবিধ উক্তির প্রতিবাদে মাওলানা কেরামত আলী বলতেন, এদেশ দারুল হারব নয়, এদেশ দারুল আমান অর্থাৎ নিরাপত্তার দেশ।
ইংরেজি শিক্ষালাভ করলে মুসলিমদের পক্ষে কাফির হওয়ার কোনো সংগত কারণ নেই। মুনশী মেহেরউল্লার কাজ ছিল দরিদ্র মুসলিম সমাজের লোকদের নানাবিধ প্রলোভনে সম্মোহিত করে খ্রিষ্টান পাদ্রিগণ খ্রিষ্টান ধর্মে তাদের দীক্ষিত করার ফলে মুসলিম সমাজে যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে তাকে রোধ করা। তিনি ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে ইসলাম ধর্মের সার জনসমাজে প্রচার করতে আরম্ভ করলে, দেখা গেল, পাদ্রিদের প্রলোভনে বিপথগামী মুসলিমেরা আবার স্বধর্মে ফিরে এসেছে। যেহেতু এ সকল পুস্তিকা বাংলা ভাষায় রচিত ছিল, এজন্য জনসমাজের উপর বাংলা ভাষার প্রভাব প্রমাণিত হয়েছিল বলে, বাঙালি মুসলিম সমাজের লোকেরা পুনরায় বাংলা ভাষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং বাংলা ভাষাকে তাদের মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করে। মুসলিম জনসাধারণের উপর বাংলা ভাষার প্রভাব লক্ষ করেই মুনশী সাহেবের সমসাময়িক মুসলিম সমাজের লেখকদের মনে বাংলা ভাষার চর্চার প্রতি সমধিক উৎসাহ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে কায়কোবাদের মতো কবি, মাওলানা আকরম খাঁ-এর মতো জীবনীলেখক, নজিবুর রহমানের মতো কথাশিল্পী, গোলাম মোস্তফার মতো কবির অভ্যুত্থানে প্রেরণা দান করেছে। তবে তা সত্ত্বেও তৎকালীন মুসলিম অভিজাত সমাজের মানসে এক ভীষণ দ্বন্দ্ব ছিল কার্যকরী। তারা তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাদের কাছে বাংলা ছিল বিমাতার ভাষা। এরাই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাংলা ভাষার মূলে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে প্রস্তুত ছিলেন। মুনশী মেহেরউল্লার ধারায় অগ্রসর হয়ে নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন। তখন থেকেই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে যে দ্বন্দ্বের কণা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তা উবে যায়। সকলেই বাংলা ভাষাকে মুসলিম সমাজের সত্যিকার মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করে সাদরে বরণ করেন। নজরুল একদিকে তাঁর বীররসপ্রসূত উপলমুখর ভাষা প্রয়োগের দ্বারা, অপরদিকে বাংলা ভাষাতে নানা ভাষার শব্দ সম্পদ আমদানি করে এবং সে ভাষাতে যত প্রকার বন্ধন রয়েছে তার গিটগুলো খুলে দিয়ে তার অবাধ গতির পথ প্রশস্ত করেছেন। তার ফলে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে ভাষা বন্দি হয়েছিল, তা সহসা যেন ঝর্ণার তালে তালে নৃত্য করে দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষার মহাসমুদ্রের পানে অগ্রসর হতে থাকে। সে ভাষাতে যে দুর্বার গতি প্রকাশ পায়, তা এ ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব:
‘চড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
মুসলিমে সারা দুনিয়াটার
জুলফেকার খুলবে তার
দুধারীধার শেরে খোদার,
রক্তে পূত বদন
খুনে আজকে রুধবো মন।’
বাংলা কাব্যের কোনো এক বা দুই পঙ্ক্তিতে উর্দু ভাষার প্রয়োগ করে তাকে আরো গতিমান করে তোলেন:
‘নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া!’
আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়ার পরিবর্তে যদি বিশুদ্ধ বাংলা ‘মাতঃ তব মানিককে করেছে হত্যা কোনো ঘাতক’ ব্যবহার করা হতো তা হলে—তাতে সে হাস্যাস্পদ আড়ষ্টতা দেখা দিত, তা ভাববিচারের ক্ষেত্রে অমার্জনীয়। তাই অবাধ ছন্দ ও আধার ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে কবি অপূর্ব ভাবের একটা অনুপম কাব্য সংযোজন করেছেন।
একথা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে কবি বিদ্যাপতি কর্তৃক ব্যবহৃত ব্রজবুলি ভাষার প্রচলন ছিল। বিদ্যাপতির ‘সখি হামার দুঃখের নাহি ওর/ এ ভরা বাদর মাহ বাদর শূন্য মন্দির মোর।’ এখনো নানা আসরে গীত হয়। এ ভাষা এখন লুপ্তপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসাধনার সূত্রপাতের সময় ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করে তাকে আবার সুধী সমাবেশে জীবন্ত করার চেষ্টা করেছিলেন—
মরণ যে তুই মম শ্যাম সমান
এ মধুর ভাষা এখন রবীন্দ্রকাব্য সাধনার এক পর্যায়ের চিহ্নস্বরূপ বর্তমান। তারপরে শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ বলে ঢাকার এক উদীয়মান কবির কাব্যে তাকে ধরে রাখার প্রয়াস পাওয়া যায়। তার কোনো এক কাব্যে ছিল:
‘তুহু ছাড়া প্রিয়তম দাদুরী কি গাবে গান
অনাদরে মুই কি গো ফুটিবে?
তুহু না আসিলে আর কে আর সোহাগ ভরে
মাধুবী মদিরাতার লুঠিবে?’
এ কবি তার এ কবিতায় তুহ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা তাকে ব্রজবুলির ছাঁচে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি দীর্ঘকাল কাব্যচর্চায় মগ্ন থাকেননি বলে তা আর আমাদের ভাষায় স্থায়ী আসন পায়নি। নজরুল ইসলাম তার সুস্থ জীবনকালে নানা কবিতায় এ ধারাটি বজায় রেখে বাংলা ভাষা সবল ও সাবলীল রাখার চেষ্টা করেছেন: ‘শ্যামল মুখ স্মরি সখিয়া বুক গোরি
উঠিছে ব্যথা ভরি আঁখিয়া ভর।’
এ স্থলে সখির স্থলে সখিয়া এবং আঁখির স্থলে আঁখিয়ার প্রয়োগে ভাষাতে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও গতি দেখা দিয়েছে। কেবল পদ্যে নয় তাঁর গদ্যরচনার মধ্যেও এরূপ ব্রজবুলি প্রভাবান্বিত শব্দ ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এজন্য তাঁকে বাংলা ভাষার মুক্তিদাতা বলা যায়।
বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজি শব্দ বর্জন করে তার স্থলে কষ্ট করে যেসব শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট করা হচ্ছে, নজরুল ইসলাম সুস্থ অবস্থায় জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করতেন। আজকে বাংলা ভাষাকে সংকুচিত করার এ সংকটে নজরুল ইসলামের এ অবদান বাস্তবিকই বিশেষভাবে স্মরণীয়।
আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন